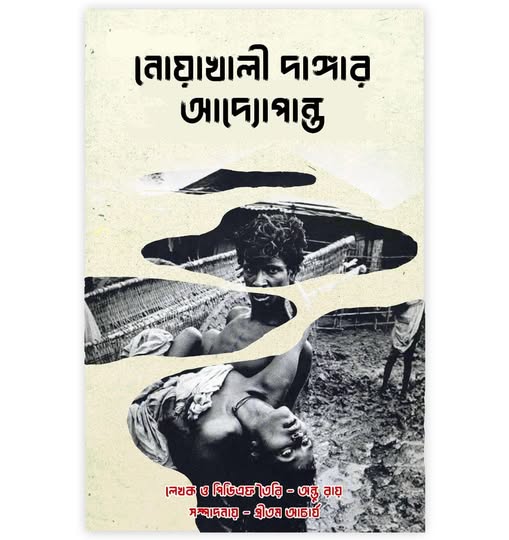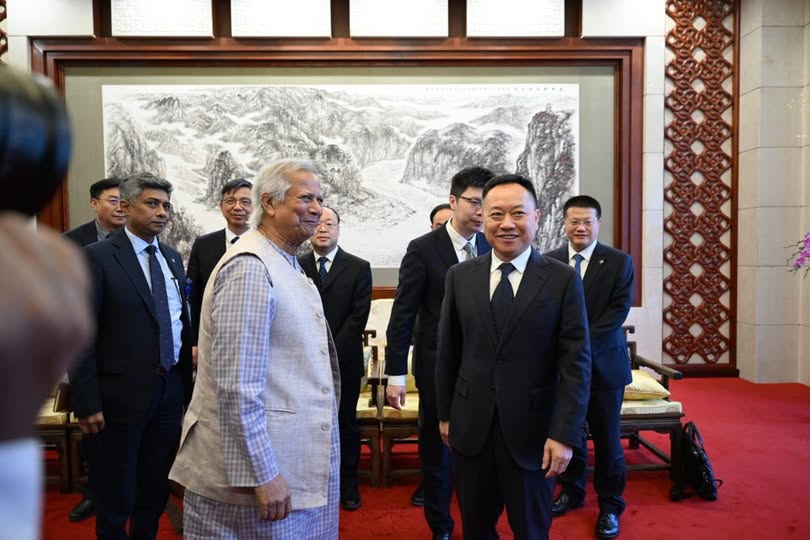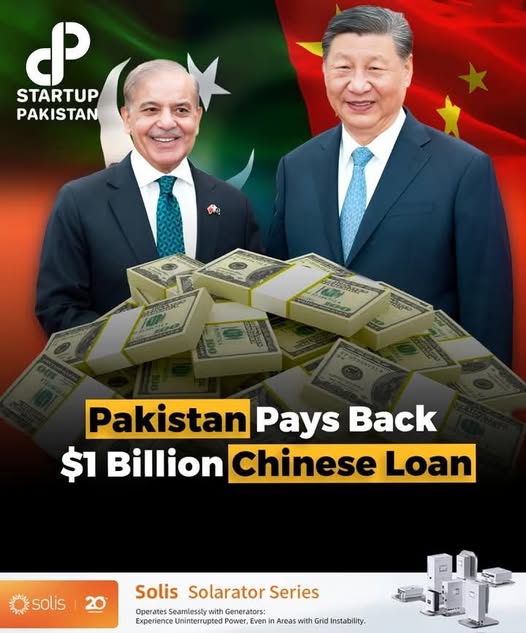ফাটকা পুজিবাদের জন্ম একচেটিয়া পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে মূলত ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে কতগুলো যুগান্তকারি ঘটনা ঘটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৪ সালে যে ব্রেটনউডস চুক্তি হয় তাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে আসে। পশ্চীম ইউরপীয় ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্থনীতির দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে ও উদীয়মান কমিউনস্ট শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই তারা মার্কিন সাম্রাজ্যের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৮ সালে মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। বিশ্ব জিডিপির ৪৫% ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জিডিপি ছিল সোভিয়েত ও ব্রিটেন এবং তা যথাক্রমে ছিল বিশ্ব জিডিপির ১১% ও ৯%। তাই বোঝাই যাচ্ছে মার্কিন অর্থনীতি বিশ্বে কতটা শক্তিশালী ছিল। এছাড়াও তার ছিল বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। পশ্চীম ইউরোপের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিশেষ করে ব্রিটেনের ছিল বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ব্রিটেন-এর জিডিপি মার্কিন জিডিপি-এর মাত্র এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব ভূ-রাজনীতির দিক থেকে এক নম্বর শক্তি ছিল ব্রিটেন। ফলে ব্রিটেনের পাউণ্ড বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বাধিক ব্যাবহার হওয়া মুদ্রা ছিল। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার উপনিবেশগুলোকে ও ডাচ সাম্রাজ্যকে বাধ্য করত পাউণ্ড ব্যাবহার করতে। যে কোন মুদ্রার শক্তি নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপরঃ সেই দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও ভূ-রাজনৈতিক শক্তি। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে একটি দেশের মুদ্রা বিশ্ব বাজারে কতটা চলবে তা নির্ভর সেই দেশ থেকে কত পণ্য ও সম্পদ কেনে বাকি বিশ্ব তার ওপর। তাই কোন দেশের মোট অর্থনীতি যদি বাকি বিশ্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় হয় আর বিশ্ববাজারে যদি তার পণ্যের ও সম্পদের বিপুল চাহিদা থাকে তবেই সেই দেশের মুদ্রার ব্যাবহার করবে বাকি বিশ্ব। সেই দিক থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যের ডলার-এরই বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বাধিক ব্যবহ্রিত মুদ্রা হওয়ার কথা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। কিন্তু তা হয়নি কারণ ব্রিটেন তার ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তার প্রভাবে থাকা দেশগুলোর সরকারকে বাধ্য করত পাউণ্ড-কে মুদ্রা ভাণ্ডারে বেশী জায়গা দিতে। ফলে সেই সব দেশের ব্যবসায়ীরাও পাউণ্ড ব্যবহার করতে বাধ্য হত। এইভাবেই পাউণ্ড ব্যাবহার করতে বাকি বিশ্বকে বাধ্য করত ব্রিটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পাউণ্ড-এর প্রভাব কমতে থাকে বটে কিন্তু ১৯৪৪ পর্যন্ত তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল। এর ফলে ব্রিটেনের মুদ্রা তার উৎপাদন ভিত্তির তুলনায় বেশী দামী ছিল। আর মার্কিন মুদ্রা তার উৎপাদন ভিত্তির তুলনায় কম দামী ছিল। তাই মার্কিন উৎপাদন ছিল বিশ্ব বাজারে সস্তা ও তার রপ্তানী ছিল বেশী। তার ছিল বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ব্রিটেনের তুলনায়। বিশ্ব বাজারে ভারসাম্য আনতে তাই ডলার এর ব্যাবহার বাড়াতে হয়। এবং এই দায়িত্বটাই পালন করে ব্রেটনউডস চুক্তি। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চীম ইউরোপীয় ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি মার্কিন হাতে সমর্পণ করা হয়।
এর ফলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার ডলারকে তাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে সবচেয়ে বেশী জায়গা দেয় (প্রায় ৮০%) এবং ফলে বিশ্ব বাজারে ডলারের ব্যাবহার বিপুলভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে মার্কিন উৎপাদন পশ্চীম ইউরোপের তুলনায় ক্রমেই দামী হয়ে যায় বিশ্ব বাজারে। ফলে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রে রপ্তানী করে পশ্চীম ইউরোপ ও জাপান বিপুল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটায় ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে। এমনকি ৬০ এর দশকের শেষে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য এই সময়ে মার্কিন অর্থনীতি পশ্চীম ইউরোপ ও জাপানের বাজার হয়ে উঠে পুঁজিবাদের অতি উৎপাদন সমস্যা দূর করতে পারে সাময়িক ভাবে। এর ফলে সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির লাভ হয় বটে কিন্তু ১৯৭০-এ মার্কিন জিডিপি বিশ্ব জিডিপির শতাংশ হিসেবে কমে হয়ে দাঁড়ায় ২৮%। অর্থনৈতিক নিয়ম মানলে ডলারের মুল্য ও ব্যাবহার কমে যাওয়া উচিত মার্কিন উৎপাদন ভিত্তির গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে। আবার অন্যদিকে মার্কিন জিডিপি পশ্চীম ইউরোপ ও জাপানের তুলনায় অনেক ছোট হোয়ে যাওয়ায় মার্কিন জিডিপির পক্ষে সমগ্র পশ্চীম ইউরোপ ও জাপানের বাজার হয়ে ওঠাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি আবার অতি উৎপাদনের সঙ্কটে পড়ে ১৯৭০ দশকের গোঁড়াতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্থানের মুখে দেশেহারা হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হেনরি কিসিঞ্জার-এর নেত্রিত্বে কতগুলো সিদ্ধান্ত নেয়। এক, ১৯৭১-এ ব্রেটনউডস চুক্তিতে ডলার ও সোনা যে নির্দিষ্ট মূল্যে বাঁধা ছিল তা ভেঙ্গে যায় এবং বাজারের চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী ডলারের মূল্য স্থির করা শুরু হয়। দুই, ১৯৭২-এ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। তিন, ১৯৭৩-এ ইসরাইল-আরব যুদ্ধের সময় যখন সৌদি আরব-এর নেত্রিত্বে “ওপেক” কারটেল খনিজ তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় তখন মার্কিন সরকার তা মেনে নেয় এই শর্তে যে সৌদি তেল বিক্রি করবে শুধুমাত্র ডলারে যা সমগ্র “ওপেক” মেনে চলবে এবং তেলের প্রয়োজন অনিবার্য বলে সমগ্র বিশ্ব তেল কিনতে গিয়ে ডলার ব্যাবহার করতে বাধ্য হবে।
১৯৭০-এর দশকে পুঁজিবাদী বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে কমে যায়। মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে বিশ্ব পুজিবাককে বাজার দেওয়া অসম্ভব হচ্ছিল। আবার বিশ্ব বাজারেও চাহিদা ছিলনা মার্কিন পণ্য বা পরিষেবার। তখন চাহিদা তৈরির এক অভিনব প্রক্রিয়া শুরু করে মার্কিন পুঁজিবাদ। সে সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবসার মধ্য দিয়ে মুনাফাজনক বিনিয়োগের সূত্র খুঁজে বার করে। কিন্তু তার জন্য সম্পত্তির মূল্য ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা দরকার। সম্পত্তির দাম বাঁড়াতে চাই বিপুল ঋণের যোগান। ব্রেটনউডস চুক্তির পরম্পরা থাকায় ও তেলের সঙ্গে ডলার বাঁধা থাকায় ডলারের একটা নির্দিষ্ট চাহিদা বজায় ছিলই। সেই চাহিদার জন্য সমগ্র বিশ্ব আন্তর্জাতিক আয় ডলারে সঞ্চয় করত। ফলে মার্কিন অর্থনীতি গোটা বিশ্বের সঞ্চয় তার সম্পত্তির বাজারে টেনে আনতে সক্ষম হয়। এই সঞ্চয় মার্কিন সম্পত্তির বাজারকে দিতে সক্ষম হয় সস্তা ঋণের যোগান আর এর ফলে মার্কিন ফাটকা বাজার হয়ে ওঠে লাভজনক। এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ফাটকা পুজিবাদ স্তরের সূচনা হয় যা সাম্রাজ্যবাদী স্তরকে অতিক্রম করে গড়ে ওঠে।
লাভজনক সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবসাকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন অর্থনীতি অতি উৎপাদন সঙ্কট থেকে আবারও সাময়িক মুক্তি পায় এবং বিশ্ব পুজিবাদকে বাজার দেওয়া শুরু করে। ১৯৮০-এর দশকে পশ্চীম ইউরোপ ও জাপান অর্থনৈতিকভাবে স্থবির রয়ে গেলেও মার্কিন অর্থনীতি গতিশীল থাকে সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাবসার জোড়ে। আর মার্কিন অর্থনীতিতে রপ্তানী করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়াতে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে চীন এই সুযোগ নেয় সবচেয়ে বেশী। সামন্ততন্ত্র বিলোপ করে শিক্ষা-সাস্থ্য-পরিকাঠামো-প্রতিরক্ষায় বিনিয়োগে বাকিদের থেকে এগিয়ে থাকায়, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রিয় উদ্যোগ-এর ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ায় ও মোট জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় চীন সবচেয়ে বেশী সফল দেশ হয় এই ফাটকা পুঁজিবাদী স্তরে। চীন ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উত্থান বোঝাতে একটা সংখ্যাতত্ত্বই যথেষ্ট। ১৯৮০ সালে মোট বিশ্ব জিডিপি-এর ৩০% ছিল তৃতীয় বিশ্বের উদীয়মান দেশসমূহ (Emerging Market Economies) আর ২০১৭ তে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬০%। একই সময়ে চীনের বৃদ্ধি হয় ২% থেকে ১৯%। ১৯৮০ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে এবং মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি মোট বিশ্ব জিডিপি-এর শতাংশ হিসেবে হ্রাস পায় যথাক্রমে ২৪% ও ২৮% থেকে ১৫% ও ১৬%।
এইভাবে ফাটকা পুঁজিবাদী স্তরে অনুতপাদনকারী খাতে বিনিয়োগ করে ও সস্তা শ্রমের দেশে উৎপাদনকারী শিল্প পাঠিয়ে দিয়ে মার্কিন অর্থনীতির একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সেই অবস্থা হয় ঠিক যেই অবস্থা ব্রিটিশদের হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ডলারের উত্থান যেমন পাউণ্ড-এর পতন ঘটানো শুরু করে তেমনই চীনের মুদ্রা উয়ানের উত্থানের সম্ভাবনা ডলারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ১৯৪৪ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে মার্কিন জিডিপি-এর গুরুত্ব বিশ্ব জিডিপি-এর তুলনায় ৪৫% থেকে ১৫%-এ কমে গেলেও ডলারের আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে গুরুত্ব কমেছে ৮০% থেকে কমেছে মাত্র ৬২%। ফলে মার্কিন উৎপাদন ভিত্তির তুলনায় ডলারের মূল্য বেশী রয়ে গেছে। ফলে মার্কিন উৎপাদন বিশ্ব বাজারে বেশী দামী হওয়ায় বাজার পাচ্ছেনা। আবার চীনের জিডিপি এত বেড়ে গেছে মার্কিন জিডিপি-এর তুলনায় যে মার্কিন ফাটকা বাজার চীনের অর্থনীতিকে পর্যাপ্ত বাজার দিতেও অক্ষম হচ্ছে। তাই বিশ্ব বাজারে ডলারের অতিরিক্ত ব্যবহার বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির পক্ষে কোন কাজ করছেনা। তাই চীনের মুদ্রা উয়ানকে বিশ্ব বাজারে জায়গা দেওয়া না হলে চীনের পক্ষে বিশ্ব অর্থনীতির বাজার হওয়া সম্ভব নয়। চীন যেহেতু ২০৩০ পর্যন্ত ৫%-এর ওপর বৃদ্ধির হার বজায় রাখবে বলে আশা করা যায়, তাই তখন চীনের জিডিপি বিশ্ব জিডিপির ২৫% হবে আর মার্কিন জিডিপি হবে স্রেফ ১২%। তাই ধীরে ধীরে চীনের মুদ্রা উয়ানকে বিশ্ব বাজারে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতেই হবে বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখতে। কিন্তু মজার ব্যাপার উয়ান কেবলমাত্র ২০১৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে জায়গা পেতে শুরু করে এবং ২০১৬ সালে শতাংশের হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে জায়গা পায় ১.০৮%, ২০১৭ সালে ১.২৩% ও ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১.৮৩% শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৫ সালের মধ্যে উয়ানকে যদি ১০% জায়গা দেওয়া না যায়, বিশ্ব বাজারের অসঙ্গতি কাটবেনা। কিন্তু এই জায়গা তৈরি করার একটা প্রাথমিক শর্ত হল চীনের ভূ-রাজনৈতিক গুরত্ব বৃদ্ধি মেনে নেওয়া। কিন্তু তা মানতে রাজি নয় মার্কিন সামরিক ও শ্বেতাঙ্গবাদী উগ্র জাতিয়তাবাদী নেতারা। তারা চীনের উত্থান ঠেকাতে বিশ্বায়ণের বিরুদ্ধে গিয়ে বাণিজ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর ফলে মার্কিন বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।
এদিকে মার্কিন ফাটকা পুঁজিবাদ জাত মার্কিন বাজারের ওপর ভরসা রাখতে না পেরে চীন বাধ্য হয়েছে তার সরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিনিয়োগ বাড়িয়ে বাজার তৈরি করতে। এই প্রক্রিয়া বিশ্ব জুড়ে কায়েম করতে চীন চালু করেছে “বেল্ট রোড ইনিসিয়েটিভ”। ফলে মার্কিন ফাটকা বাজার কেন্ত্রিক বিশ্বায়ণ ভেঙ্গে সরকারি সংস্থা কেন্দ্রিক বিনিয়োগকে ভিত্তি করে নতুন চীন করকার কেন্দ্রিক বিশ্বায়ণ গড়ে তুলতে চাইছে চীন। এই জন্য মার্কিন ফাটকা পুঁজির প্রাণকেন্দ্র ওয়াল স্ট্রিট বুঝতে পারছে চীনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় না এলে ক্রমেই চীন একটা স্বাধীন চীন ভিত্তিক বিশ্বায়ণ করে তুলবে। হেনরি কিসিঞ্জার যিনি এই ফাটকা পুঁজিবাদের জনক তিনি ৯৫ বছর বয়সে ছুটে গেছেন বেইজিং-এ চীন ও মার্কিন রফাসূত্র বের করতে। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৮-এর নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে গড়ে তোলা হয়েছে “নয়া অর্থনীতি সঙ্ঘ” যা কিনা চীনের উত্থান স্বীকার করে বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কে নীতি প্রস্তাবনা করবে।
রফা সূত্র বের করা কতটা দরকারী তা বুঝতে বিশ্বজুড়ে বিদেশী বিনিয়োগ বা আন্তর্জাতিক পুঁজির চলাচল কিভাবে কমছে তার একটা সংখ্যা দেওয়া হল।
বিদেশী বিনিয়োগের সংখ্যাতত্ত্ব (১৯৭০-২০১৭, বিলিয়ন ডলার)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Nations Conference on Trade and Development and official national sources ১৯৭০ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজির চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তা কমে গেছে ভয়ানকভাবে। ৩.১ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে কমে হয়েছে ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১৮ সালে ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য তা কমে দাঁড়াবে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু চীন ও মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুজির চলাচল প্রায় স্থির আছে। এর অর্থ বাকি বিশ্বে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ কমেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ইউরোপ, তুর্কি, ভেনেজুয়েলা, পাকিস্তানের মতো দেশে কমেছে ভয়াবহভাবে। যদি এই প্রবণতা বজায় থাকে ক্রমে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ দেউলিয়া হবে এবং এর ফলে আবারও নানারকম বিদ্রোহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কিসিঞ্জার তাই বলেছেন, “চীন ও মার্কিন বৈরিতা বাড়লে ক্রমেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে”। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুগে যে শ্রমিক সুবিধাবাদ গড়ে উঠেছিল, ফাটকা পুঁজিবাদের যুগে তার ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমিকের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এই পুঁজি রপ্তানীর ও তৃতীয় বিশ্ব থেকে সস্তা পণ্য ও সস্তা অভিবাসী শ্রমিক আনার বিরুদ্ধে বিশ্বায়ণ-বিরোধী রাজনীতি তৈরি করেছে। এই রাজনীতি ক্রমেই উগ্র দক্ষিণপন্থার জন্ম দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প, ব্রিটেনে ফ্যারাজ, ইতালিতে সালভিনি, হাঙ্গেরিতে ওরবানের রাজনৈতিক উত্থান এই ভয়ঙ্কর দিক উন্মোচিত করছে। এই রাজনীতি সমাজে এই ধারণার জন্ম দিচ্ছে যে বিশ্ব পুঁজি এবং শ্রমিক ও পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচল হল সমস্যা আর একটি জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে পুঁজিবাদ ভালো। তাদের চোখে জাতি রাষ্ট্র অতিক্রম করে পুঁজির চলাচল ও বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতা আসলে ইহুদী বা বিশ্বায়ণবাদী বিশেষ পুঁজির ষড়যন্ত্র মাত্র। তারা এই সহজ কথা বুঝতে অক্ষম যে পুঁজি মুনাফা বাড়াতে পুঁজির নিয়মেই বিশ্বায়িত হয়েছে আর এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে পুঁজিবাদের সাথে ও পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার উদ্যেশ্যেই লড়াই করতে হবে। তাই মার্কিন ও চীন দ্বন্দ্ব আসলে এই উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ফল আর এই শক্তিকে আটকাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওয়াল স্ট্রিট। চীন-মার্কিন রফা কিরকম হতে পারে তা বুঝতে হলে জানতে হবে মার্কিন দাবী কি? মার্কিন সরকার চীনের কাছ থেকে চাইছে এমন মেধাজাত সম্পদ আইন যা চীনে করা উচ্চপ্রযুক্তির মার্কিন বিনিয়োগ থেকে পাওয়া মুনাফা বাড়াবে, চীন যেন আরও বেশী আমদানী করে এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমিয়ে আনে ও চীন যেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো দ্বারা বিনিয়োগ নির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে এসে ব্যাক্তিমালিকানা ভিত্তিক ফাটকা বাজার নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলে। চীন শেষ প্রস্তাবটি ছাড়া বাকি দুটো প্রস্তাবই মেনে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রথম দুটি প্রস্তাবের অর্থ দাঁড়ায় মার্কিন উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবসায়ীরা চীনের সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করতে ও মুনাফা করতে পারবে। আর চীনের বাজারকে নির্ভর করে রপ্তানী বাড়াতে পারবে। কিন্তু চীনের বাজার বাড়াতে গেলে উয়ানের মূল্য বাড়াতে হবে। অতএব উয়ানের গুরুত্ব বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে বাড়াতে হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চীনের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়াতে হবে। এর ফলে মার্কিন ব্যাবসায়ীদের মুনাফা বাড়বে কিন্তু মার্কিন সামরিক শক্তি অর্থাৎ পেন্টাগণের শক্তি খর্ব করতে হবে। পেন্টাগণ যদি এর বিরোধিতা করে তবে সে হতে চলেছে মুনাফালাভে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা। পেন্টাগণ পশ্চীম ও মার্কিন সমাজের বিশ্বায়ণ বিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুঁজির মুনাফালাভে বাঁধা তৈরি করতেই পারে। মজার বিষয় যেই পেন্টাগণ সবচেয়ে অনুগত খোঁজা হিসেবে বিশ্ব পুঁজিবাদের হারেমের পাহাড়া দিয়েছে আজ সেই পেন্টাগণের শক্তি খর্ব করতে চাইবে বিশ্ব পুঁজি। ইতিহাস রসিক পুরুষ। আর সেই ভয়ঙ্কর রসিকতা এবার হয়তো পেন্টাগণের সাথেই হতে চলেছে। |
Author: Saikat Bhattacharya
International geopolitics General 07-November-2021 by east is rising