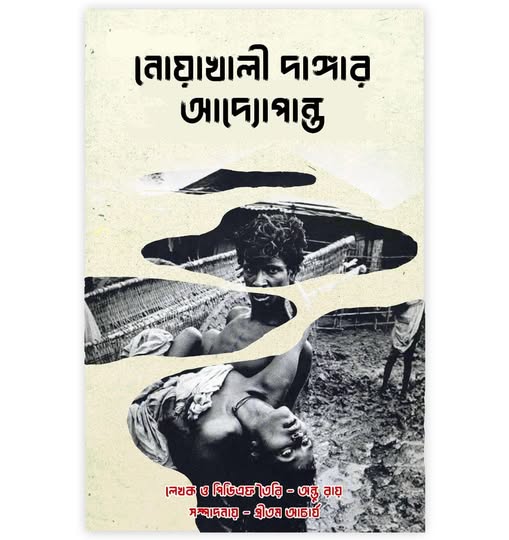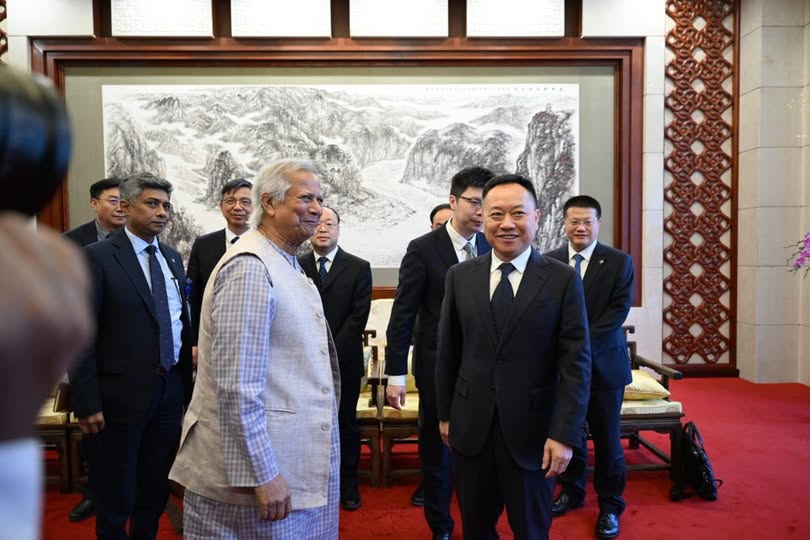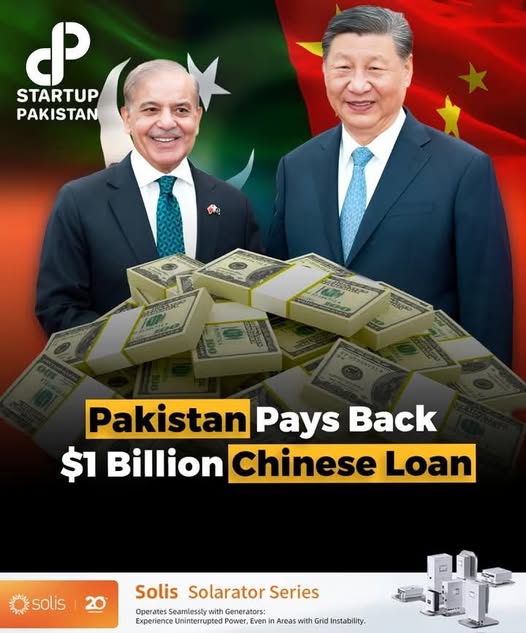পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার সদর পুরুলিয়া শহর থেকে 47 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে রথুনাথপুর মহকুমার অন্তর্গত জলে নিমজ্জিত প্রত্নস্থল তেলকুপি। পাঞ্চেতে দামোদার নদীর উপর 1959 সালে বাঁধ তৈরীর সময় এই পুরাকেন্দ্রটি দামোদারের জলে নিমজ্জিত হয় এবং তার সাথে সলিলসমাধি ঘটে বাঙালীর ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের।
তেলকুপীর প্রাচীন নাম ছিল 'তৈলকম্পী'। তৈল অর্থাৎ কর ও কম্পন অর্থাৎ পরগণার সংযোগে এর নামকরণ যার অর্থ করদ প্রদেশ। এই তৈলকম্পী ছিল পঞ্চকোট রাজ্যের শিখরবংশীয় রাজাদের একটি প্রাচীন রাজধানী। আনুমানিক নবম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মত। এই বংশেরই একাদশ-দ্বাদশ শতকের এক রাজা রুদ্রশিখর তার বিভিন্ন সামন্তের সহযোগীতায় পালসম্রাট রামপালকে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন। তাদের এই গৌরবগাথা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' এ বর্ণনা করা আছে:
''শিখর ইতি সমর পরিসর বিসর দরিরাজ
রাজিগত্ত গধ্বগহন দহন দাবানল:
তৈলকম্পীয় কল্পতরু রুদ্রশিখর''
(যুদ্ধে যার প্রভাব, নদী-পর্বত ও উপান্তভূমি জুড়ে বিস্তৃত, পর্বত কন্দরের রাজবর্গের যিনি দর্প দহনকারী দাবানলের মতো সেই তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশিখর।)
পঞ্চকোটের রাজবংশমালা অনুযায়ী রুদ্রশিখরের আবির্ভাব ঘটে 1098 সালে আবার ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন গুপ্তর মতে রামপালের শাসনকাল 1070-1120 খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং বাংলার ইতিহাসের একটা হারানো অধ্যায় এখানে পাওয়া যাবে।
রাজধানী হবার সাথে সাথে এটি ছিল তৎকালীন এক গুরত্বপূর্ণ বন্দরনগরী। এর কাছেই অবস্থিত ছিল দুটি তামার খনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাঢ়বাংলা যুগ যুগ ধরেই তামা, কাঁসা, পিতলের দ্রব্য উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। এই থেকে ঐতিহাসিকদের মত যে এই বন্দরনগরী দামোদার নদীপথের বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এবং এই বাণিজ্যপথে বণিকরা তাম্রলিপ্ত বন্দরে বাণিজ্যসামগ্রী নিয়ে যেত যার মধ্যে তামা, কাঁসা, পিতল, পাথর, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য সামগ্রী থাকত। বণিকরা মূলত জৈনধর্মাবলম্বী ছিল বলে ঐতিহাসিকদের মত। এর কারণ হল রাঢ়বাংলাতে জৈনধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এবং বণিকদের মাঝে জৈনধর্ম ছিল জনপ্রিয়। তাছাড়া তেলকুপির মন্দিরগুলির অনেকগুলিই হল জৈনমন্দির ও হিন্দুমন্দিরগুলিতেই জৈনপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মূলত বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই মন্দিরগুলি গড়ে বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে জৈনধর্ম হ্রাস পাওয়াতে অনেক জৈন মন্দির হিন্দু মন্দিরে রূপান্তিরত হয় ও অনেক জৈন বিশ্বাস, আচার, ধর্মীয় চরিত্র হিন্দুদের মাঝে প্রবেশ করে। যেমন স্থানীয় অধীবাসীদের এক উপাস্য দেবতা হল বিরূপনাথ বা ভৈরবনাথ। এই ভৈরবনাথ আদতে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব। পরবর্তীকালে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে শিবের এক রূপ হিসাবে উপাস্যে পরিণত হন। কিছু কিছু স্থাপত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও দেখা যায়।
এই মন্দিরসমূহ নিয়ে ঐতিহাসিক বিবরণগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলঃ
1. ১৮৭৮ এ প্রকাশিত জে. ডি বেগলারের “Report of A Tour through the Bengal Provinces (Vol VIII)”।
2. ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হান্টারের "Statistical Account of Bengal (volume=XVII)"।
3. ১৮৯৬ সালে অবিভক্ত বাংলার পূর্ত বিভাগের দ্বারা সংকলিত বাংলার প্রাচীন সৌধের একটি তালিকা যা ৩১শে আগস্ট ১৮৯৫ পর্যন্ত সংযোজিত করা ছিল।
4. 1903 সালে বেঙ্গল সার্কেলের আর্কিওলজিকাল সার্ভেয়ার টি. ব্লচের বিবরণ।
5. নির্মলকুমার বসুর বিবরণ।
6. দেবলা মিত্রের বিবরণ।
7. এছাড়া ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ও সুভাষ রায়ের বিবরণ।
এর মধ্যে বেগলারের বিবরণীতেই পুঙ্খানুপুঙ্গভাবে মন্দিরসমূহের বিবরণী আছে। বেগলারের মতে সেসময় ছোটনাগপুর সার্কেলের ভিতর তেলকুপী ব্যতীত এত স্বল্প পরিসরে এতগুলি উৎকৃষ্ট মানের মন্দির দেখা যায়নি। মন্দিরগুলি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের মন্দিরগুলি গ্রামের উত্তর দিকে নদীর কাছে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় ভাগের মন্দিরগুলির অবস্থান ছিল গ্রামের কাছে; কিছুটা পশ্চিম দিকে। তৃতীয় মন্দির সমষ্টিগুলি ছিল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে– গ্রামের শেষ প্রান্তে। প্রথম সমষ্টিতে তেরোটি মন্দির ছিল। দ্বিতীয় মন্দিরসমূহতে বেগলার ছটি মন্দির ও অনেক মূর্তি দেখেছিলেন, যার মধ্যে উনি চারটি মন্দিরকে উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলেন। তৃতীয় মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে বেগলার তিনটি মন্দির ও একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন। এই শেষাক্ত মন্দিরশ্রেণীর আশেপাশে উনি অনেক পাথরের ও ইঁটের স্তুপ দেখতে পেয়েছিলেন। নিম্নে তার লিঙ্কটি দেওয়া হল বিস্তারিত জানার জন্যঃ
https://en.m.wikisource.org/wiki/Report_of_a_Tour_through_the_Bengal_Provinces/Telkupi
মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতি স্বকীয়তা ও নৈপুণ্যের পরিচয়বাহক। বড় পাথরকেটে উপযুক্ত আকার করে তারপর তা দিয়ে মন্দিরগুলি নির্মিত হত। কোন পেষণীযন্ত্রের প্রযোগ হতনা। তারপর পাথরের উপর ভাস্কর্য নির্মাণ হত। ছোট ফাঁকগুলি পাথর ও বড় ফাঁকগুলি করবেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভরাট করা হত। মন্দিরগুলিতে একটিমাত্র খিলানযুক্ত প্রবেশপথ থাকত যাকে দেউল বলা হত।
বর্তমানে এই প্রত্নস্থলের পুরোটাই জলে নিমজ্জিত। 1959 সালে জলরাশির অতল গভীরে তলিয়ে গেল বাঙালীর ইতিহাসের এক অধ্যায়। কয়েকটি মন্দিরই টিকে আছে যার মধ্যে কিছু ভগ্নপ্রায় ও কিছু অক্ষত। গ্রীষ্কালের দাবদাহে জল শুকোলে কিছু মন্দিরের চুড়া দেখা যায়। একটি মন্দির অর্ধনিমজ্জিত ও তা নৌকার সাহায্যে গিয়ে দেখতে হয়। এছাড়া ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু অবশিষ্ট দেউল, কিছু বিগ্রহ, ইঁটের ভগ্নস্তুপ ইত্যাদি।
এই তেলকুপি কী অন্য কিছুরও সংকেত দেয়? বাঙালীর ইতিহাস নিমজ্জিত হয়ে অতল গভীরে হারিয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনীর সাক্ষী হয়ে আছে আজকের তেলকুপী। তবে জলের মধ্যে থেকেও চুড়ো তুলে থাকা কিছুটা আশার উদ্রেক করে।
Read MoreAuthor: Sayak Bhattacharya
Historical General 14-July-2022 by east is risingশুশুনিয়া পাহাড় পর্যটনপ্রিয় মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ। মূলত শীতকালে এখানে পর্যটকদের ঢল নেমে পড়ে। camping, rock climbing, trekking ছাড়াও মনোরম প্রকৃতির আস্বাদন করতে পর্যটকেরা এখানে আসেন।
তবে এই পাহাড়ের মূল গুরুত্ব পর্যটনের জন্য নয়, এটি মূলত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তিক অঞ্চল হিসাবে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই অঞ্চল বাংলার সর্বপ্রাচীন অঞ্চলদের মধ্যে অন্যতম।
পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা শহরের কাছে এই পাহাড় অবস্থিত। ভূতাত্বিকভাবে বাংলার সবচেয়ে পুরনো ভূমি হল পশ্চিম রাঢ়, তারই অন্তর্গত এই শুশুনিয়া পাহাড়। শুশুকের আকৃতির জন্যে এই নামকরণ।
এই অঞ্চলে হায়না, জিরাফ, এশিয়াটিক সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর জীবাষ্ম মিলেছে। এর মধ্যে এশিয়াটিক সিংহের গুরত্ব আলাদাই কারণ বাংলার রাজকীয় পশু যুগ যুগ ধরে ছিল এই এশিয়াটিক সিংহ।
প্রাণীর জীবাষ্ম ছাড়াও এখানে মিলেছে প্রস্তরযুগে ব্যাবহৃত যন্ত্রাদি ও অস্ত্র। প্রস্তরযুগের নানান সময়কালের(time period) অস্ত্রই এখানে মিলেছে। নুড়িপাথর, স্ফটিক, ফেল্সপার,জ্যাসপার, ব্যাসল্ট, ডোলোরাইট প্রভৃতি পাথরের তৈরী অস্ত্র, যন্ত্রাদি মিলেছে এখানে। কুঠার, ছুরি, তীরের ফলা, খননযন্ত্র, চাঁছনি, ওভেট, খননযন্ত্র, ছেদক ইত্যাদি যন্ত্রাদি পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল সম্পূর্ণ বনজঙ্গলে আবৃত ছিল এবং নানান ধরণের তৃণভোজী, মাংসাসী প্রাণীর বিচরণ ছিল এখানে। আবার কাছেপিঠে নদী ও ঝর্ণা উভয়ের জলই প্রাপ্য ছিল। ফলে প্রস্তরযুগে বসবাসের জন্যে পর্যাপ্ত রসদ ছিল তাই সমগ্র প্রস্তরযুগ ধরেই মানুষের বসবাস ছিল। মূলত পশুর মাংস ও বুনোফল ছিল তাদের খাদ্য। শুশুনিয়ার পাদদেশের কাছাকাছি ত্রিশটি মত পুরাতাত্বিক কেন্দ্র অবস্থিত।
তবে শুধু প্রাগৈতাহিক যুগেই নয়, বাংলার ইতিহাসেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শুশুনিয়া পাহাড়েই মিলেছে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি- রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি। এই পাহাড়েই চন্দ্রবর্মার দূর্গের অবস্থান ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। এর নিকটেই ছিল রাজধানী পুষ্করণা নগর। মালবদেশের দশপুর-মন্দসৌর লিপি যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন তা অনুসারে জয়বর্মার পুত্র সিংহবর্মা ও সিংহবর্মার দুই পুত্র- বড় চন্দ্রবর্মা ও ছোট নরবর্মা। এই বংশের আদি পরিচয়, নিবাস নিয়ে জল্পনা রয়েছে। কোনমতে তারা রাজস্থানের, কোনমতে আবার তাদের আদিনিবাস সিংহল। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকরি হরিসেন রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' তে যে চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে তা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে এই পুষ্করণারাজ চন্দ্রবর্মাই।
ধর্মে তারা ছিলেন বৈষ্ণব এবং বিষ্ণুকে নৃসিংহরূপেই উপাসনা করতেন। রাজার প্রভাবে এই অঞ্চলে মানুষদের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম প্রসার ঘটে। শুশুনিয়া পাহাড়ে ওঠার ধাপের আগেই পাদদেশে একটি নৃসিংহ মূর্তি ও উপাসনাস্থল রয়েছে। আবার এর সামনেই রয়েছে একটি পাহাড়ি ঝর্ণা যেটি টাইলসে বাঁধানো ও জলের উৎসমূখে সিংহের মূখ বসানো রয়েছে। এই জলে ঔষধিগুণ আছে বলেও জনমানসে বিশ্বাস। এছাড়াও নরসিংহ নিয়ে বহু কিংবদন্তী স্থানীয় লোককথাতে প্রচলিত।
সেই চন্দ্রবর্মার আমলেই শুশুনিয়া পাহাড়ে খচিত হয় বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি। এই লিপির দুটি অংশ- উপরের অংশে দুটি সমান্তরাল বৃত্ত অবস্থান করছে। একটি বৃত্ত থেকে কতগুলি রেখা নির্গত হয়ে এসেছে, এই রেখাগুলি আবার আরেকটি বড় বৃত্ত দ্বারা আবৃত। অপর বৃত্তটি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকগুলি অগ্নিশিখা। প্রতিটি অগ্নিশিখার পরেই আবার দুটি করে অর্ধবৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এটি মূলত ভাবলিপি। এই ভাগটিকে বিষ্ণুচক্র বলে ধারণা করা হয়েছে।
নীচের অংশে ব্রাহ্মীলিপিতে নিম্নোক্ত কথা খোদিত আছে যা বন্ধনীতে বাংলা করে দেওয়া হল:
''পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য/ মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ কৃতিঃ/ চক্রস্বামিন দাসাগ্রেণাতি সৃষ্টঃ’'
(পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মার কীর্তি। চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর অগ্রদাসের দ্বারা সৃষ্ট।)
হয় রাজ্যবিজয় নয় ভূদান বা কোন গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির স্মারক হিসাবেই এই লিপি খোদিত।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটি ‘দ্য ওল্ডেস্ট ব্রাহ্মি ইনস্ক্রিপশন ইন বেঙ্গল' এবং প, ম, হ, র প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষর প্রায় আধুনিক বাংলা অক্ষরের মতো’।
এই অঞ্চলের কাছেই নেতকমলা ও বিকনা গ্রামদুটি ডোকরা শিল্পের জন্যে বিখ্যাত। এই ডোকরা শিল্প হল এক প্রাচীন শিল্প যার নিদর্শন সিন্ধ্যুসভ্যতা থেকে চীন, ভিয়েতনাম সর্বত্র পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন এই শিল্প পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্র হল উপরোক্ত দুটি গ্রাম। এছাড়াও বর্ধমান, বাঁকুড়ার আরো কিছু স্থানে এই শিল্পের প্রচলন আছে। পাহাড়ের পাদদেশে যে হাট বসে তাতে এই শিল্পসামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়াও গ্রামে ডোকরামেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই শিল্পের অবস্থা বর্তমানে সঙ্গীন। এই ডোকরা শিল্প নিয়ে পারলে পরে লিখব।
অতীতের সেই পুষ্করণা নগরী বর্তমানে পখন্না বা পোখরনা নামে একটি সাধারণ গ্রাম মাত্র।
এই অঞ্চলের ভূমি আদিম ও ঐতিহ্যবাহী। সঠিক উদ্যোগে ঐতিহাসিক, পুরাতাত্বিক গবেষণাকার্য হলে বাঙালীর ইতিহাসের আরো অনেক অধ্যায় বেরিয়ে আসবে তা সন্দেহাতীত। সুতরাং বাংলার ইতিহাস, পুরাতত্ব ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এই অঞ্চল বাংলার এক অমূল্য সম্পদ।
Read MoreAuthor: Sayak Bhattacharya
Historical General 14-July-2022 by east is risingইতিহাস ও নৈসর্গের এক মনোরম সহাবস্থান হল গড় পঞ্চকোট। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে জীবন্ত ইতিহাসেরও সাক্ষী এই স্থানটি। পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলার পাঞ্চেত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই স্থান। বরাকর বা আদ্রা থেকে সড়কপথে যাওয়া যায় এখানে।
জনস্রুতি অনুসারে দামোদার শিখর আনুমানিক নব্বই খ্রীষ্টাব্দে পাঁচজন উপজাতি সর্দারের সহায়তায় ঝালদাতে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই রাজ্যের নামকরণ হয় পঞ্চকোট অর্থাৎ পাঁচ গোষ্ঠী, কোট শব্দের অর্থ হল গোষ্ঠী। রাজবংশের নাম হয় শিখর রাজবংশ যদিও মধ্যযুগের একদম শেষের দিকে তারা সিংহদেও উপাধি ধারণ করে। এরপরে রাজধানী কয়েকবার বদল হয় এবং এই বংশের আরেক শাসক কীর্তিনাথশেখর দশম শতাব্দীতে এই গড়ের নির্মাণ করেন ও এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই থেকে শিখরবংশের রাজধানী পঞ্চকোটের গড় বা গড়পঞ্চকোট নামে পরিচিত হয়। তখন গোটা অঞ্চলটি ছিল বৃহৎ দূর্গে ঘেড়া এবং তার কেন্দ্রে ছিল রাজধানী।
দূর্গটি ছিল এক অর্ধবৃত্তাকার বিশাল পরিখাতে ঘেড়া যেটি নৌকাতেই পার করা যেত এবং তাতে কুমীরও ছাড়া থাকত। মূল দূর্গটি পুরু পাথরের দেওয়াল দিয়ে আবৃত থাকত ও তার বাইরে আরো একটি বিশাল প্রতিরক্ষাপ্রাচীরের অবস্থান ছিল। এছাড়াও স্থানে স্থানে থাকত watchtower। বর্তমানে সেই প্রাচীরগুলির কিছু ধ্বংসস্তুপ পড়ে আছে ও পরীখাটি এখন ক্ষুদ্র একটি জলাশয়রূপেই আছে। এছাড়াও আরো কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল রাণীমহল, পঞ্চরত্ন মন্দির, কঙ্কালেশ্বরী মন্দির, জোড়াবাংলা মন্দির, watchtower, প্রবেশপথ ইত্যাদি। এগুলি সবই এখন ধ্বংসস্তুপ ও সংস্কারের অভাবে বিলীন হবার উপক্রম। তবে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ইদানীং সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু কোন মন্দিরেই আর বিগ্রহ অবস্থান করেনা।
শিখররাজারা বৈষ্ণব, শাক্ত ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এইকারণে পঞ্চকোট রাজ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও জৈন মন্দিরের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। অনেক মন্দির আবার নদীর তীর বরাবর স্থাপিত হত। মন্দিরগুলি পোড়ামাটি ও পাথর উভয়দ্বারাই নির্মিত হত। খোদ গড় পঞ্চকোটেই একসময়ে চল্লিশটির বেশী মন্দিরের উপস্থিতি ছিল।
এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমানের কিয়দংশে, সমগ্র পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ডের বোকারো, ধানবাদ, রাঁচী সিংভূমে। এছাড়াও কটক ও বারাণসীতে তাদের জমিদারী ছিল।
JD Beglar 1872 খ্রীষ্টাব্দে আঁখ দুয়ার, বাজার মহল দুয়ার, খড়িবাড়ি দুয়ার এবং দুয়ার বাঁধ নামক চারটি তোরণের বর্ণনা করেন। এর মধ্যে খড়িবাড়ি দুয়ার এবং দুয়ার বাঁধে মল্লরাজ বীর হাম্বীর মল্লদেবের নাম পাওয়া যায় যেটা থেকে এটাও ধারণা করা যায় যে তারা মল্লভূমের অধীনস্থ ছিলেন।
শিখররাজারা প্রজাহিতৈষী ছিলেন এবং নিষ্কর মৌজাদানের উদাহরণ পাওয়া যায় এই নিয়েও ঐতিহাসিকমহলের মত। বৃহৎ মানভূমের সংস্কৃতিকে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাদের সভা অলঙ্কৃত করতেন কথাসাহিত্যিক থেকে সঙ্গীতশিল্পী থেকে নর্তক-নর্তকীরা। (এখানে নাচ বলতে মূলত ছৌনাচের কথাই বলা হয়েছে)
বাংলাতে বর্গী আক্রমণের সময়ে এই দূর্গনগরী বর্গীদের নজরে পরে ও হামলাতে এই নগরী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্মশানে পরিণত হয়। কথিত আছে, রাজার সতেরো রাণী সম্ভ্রম বাঁচাতে কুয়োতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। অবশিষ্ট রাজবংশ কাশীপুরে প্রস্থান করে ও সেখানেই রাজধানী স্থাপন করে। সেখানেও ইতিহাস আছে, তবে তা অন্য পোস্টে বর্ণনা করা যাবে।
মারাঠা ধ্বংসলীলার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই গড় পঞ্চকোটের ধ্বংসস্তুপ। এককালে এইনগরী লোকজনে গমগম করত, রাজপাট বসত, দূরদূরান্ত থেকে বণিকরা আসত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এখন এটি একটি পাহাড়ি ধ্বংসস্তুপ।
Read MoreAuthor: Sayak Bhattacharya
Historical General 14-July-2022 by east is rising