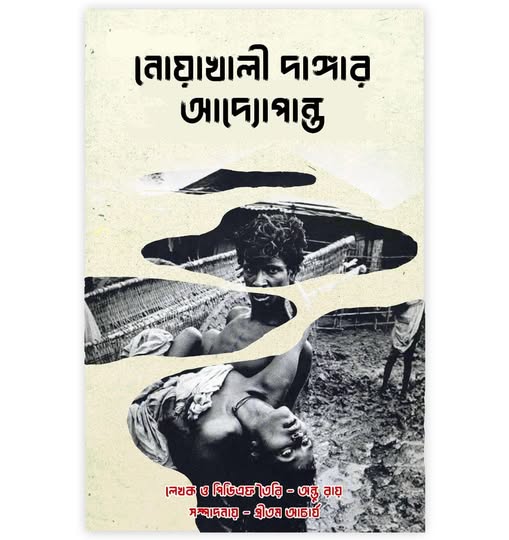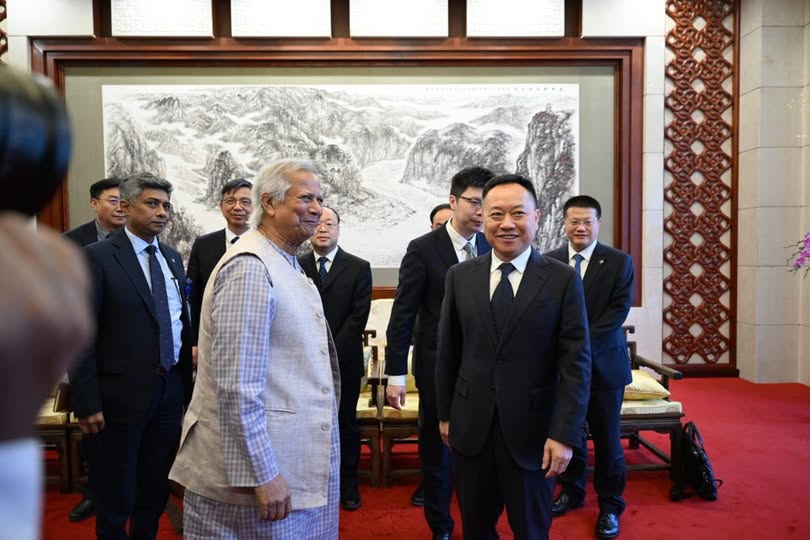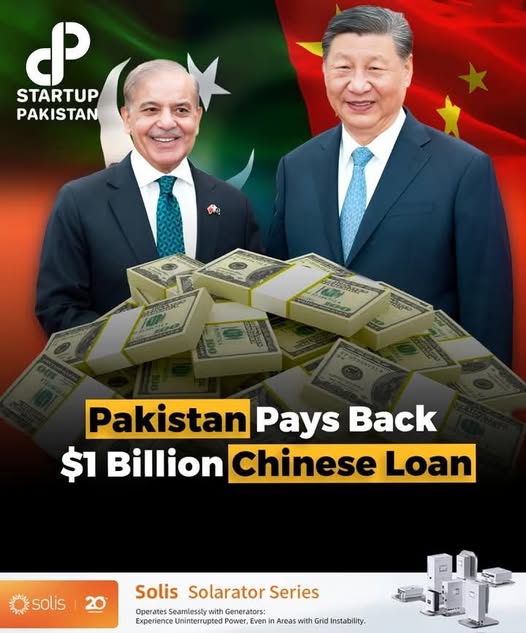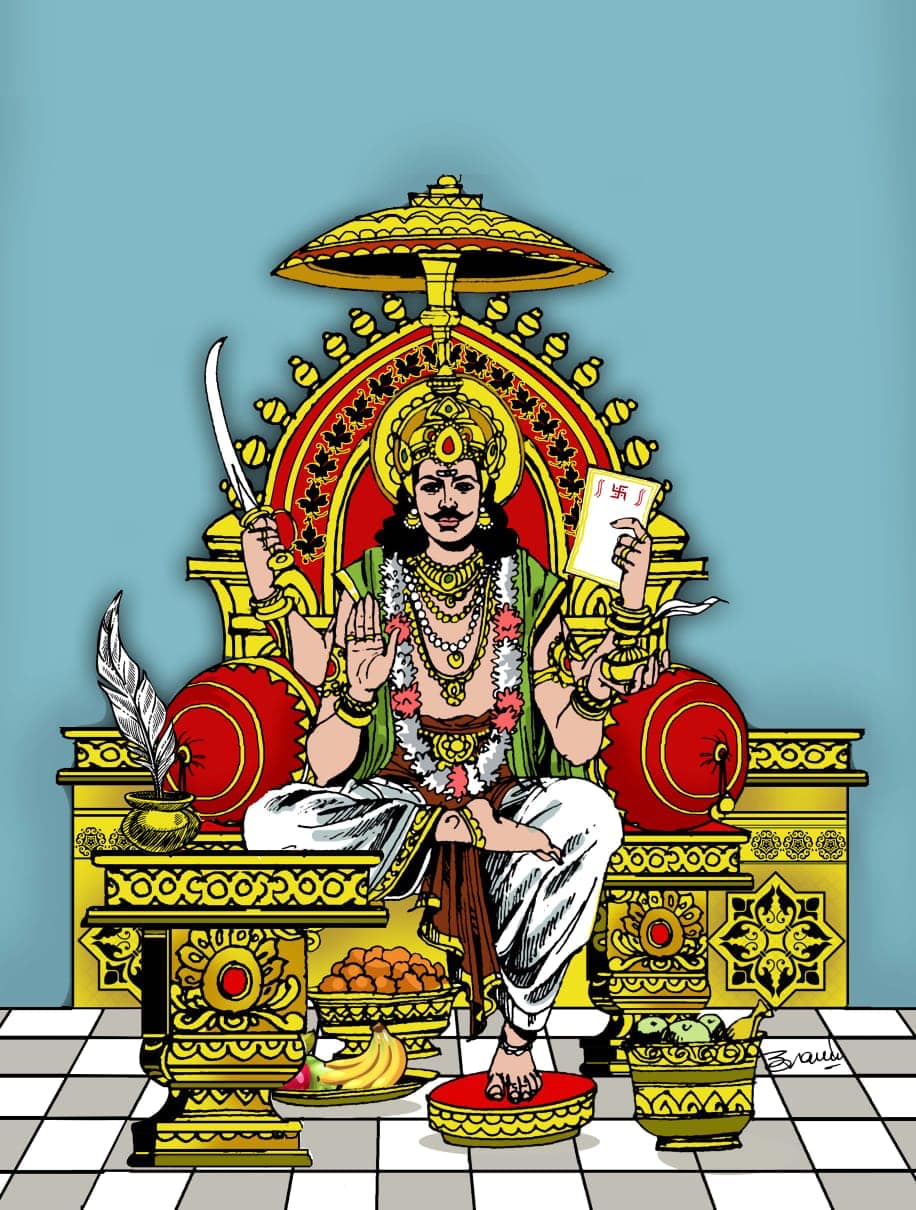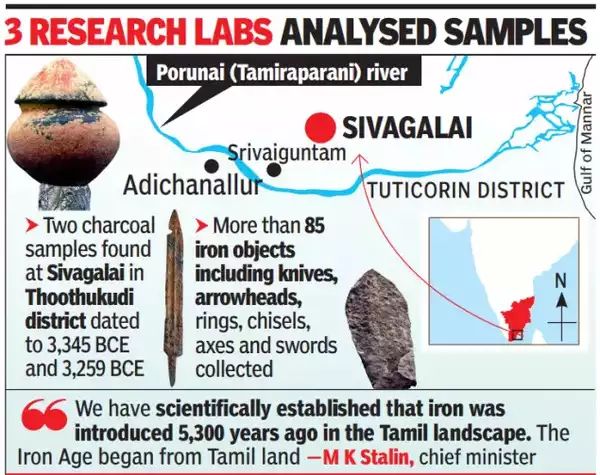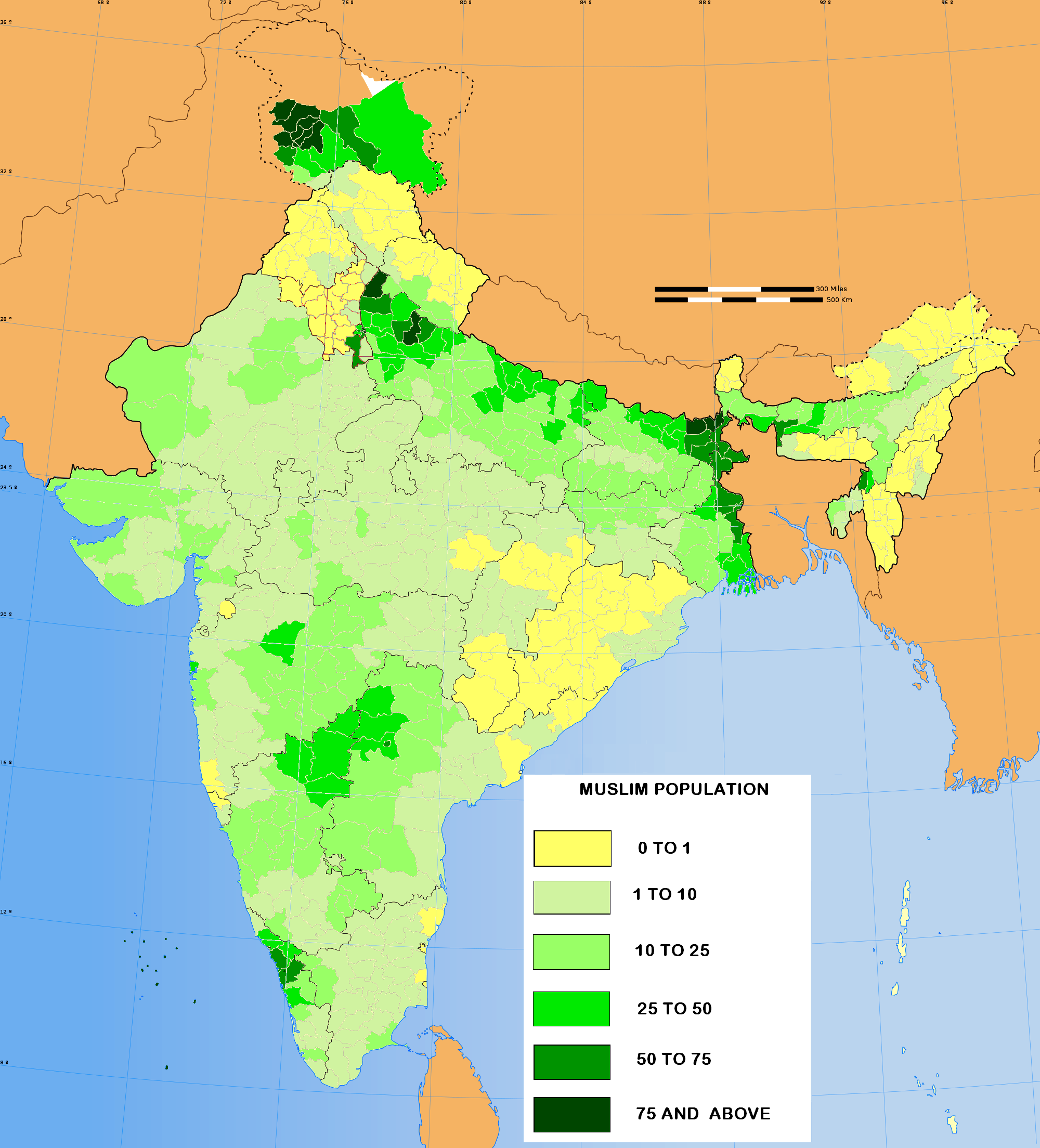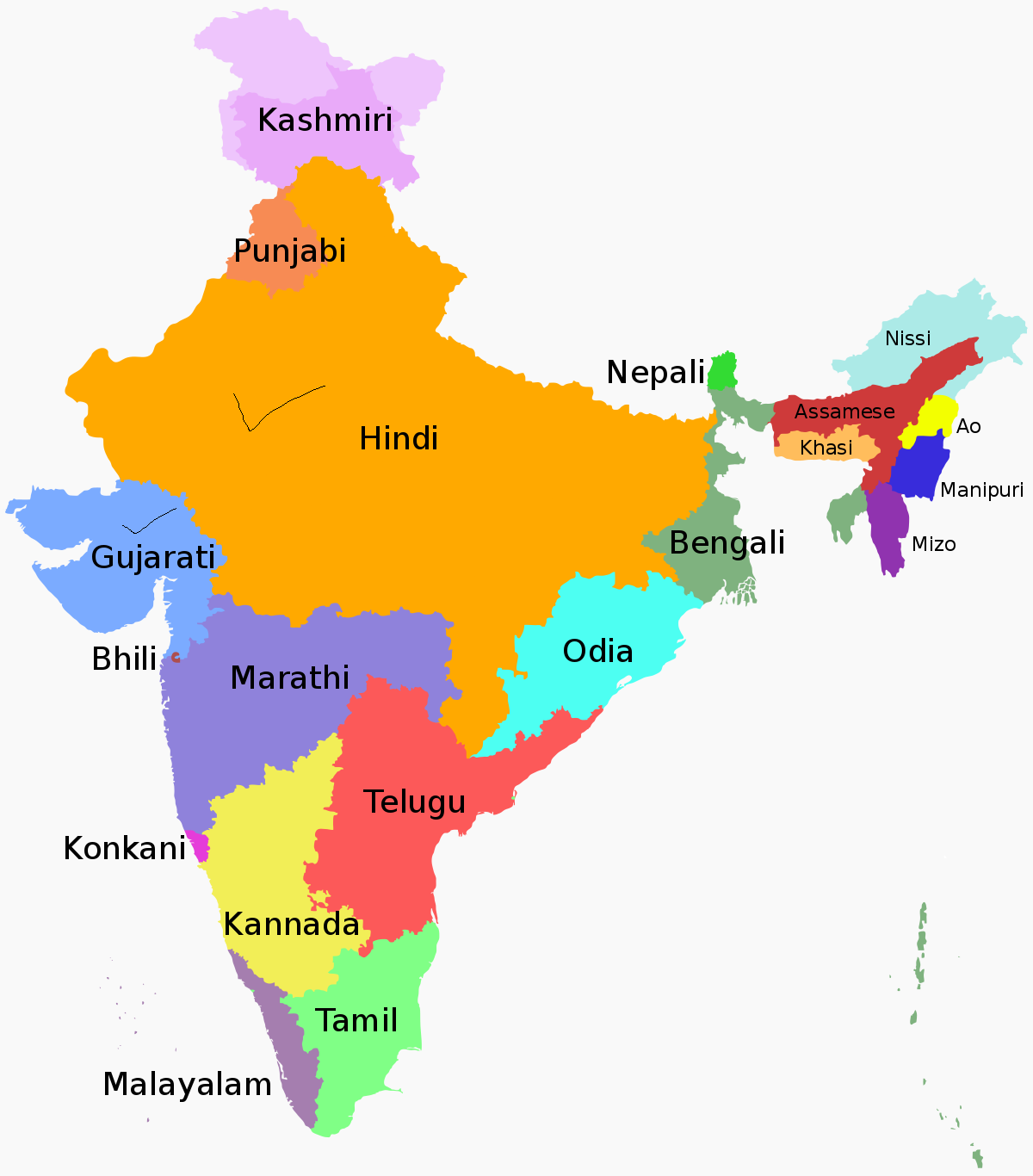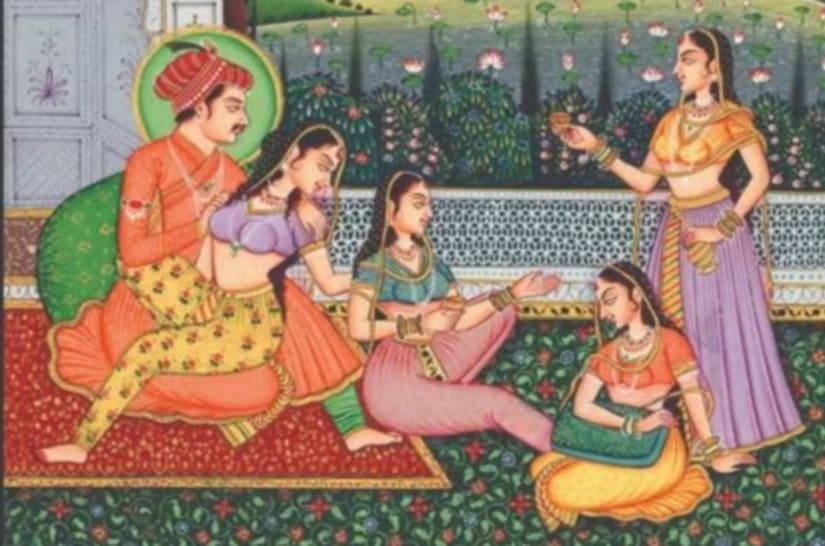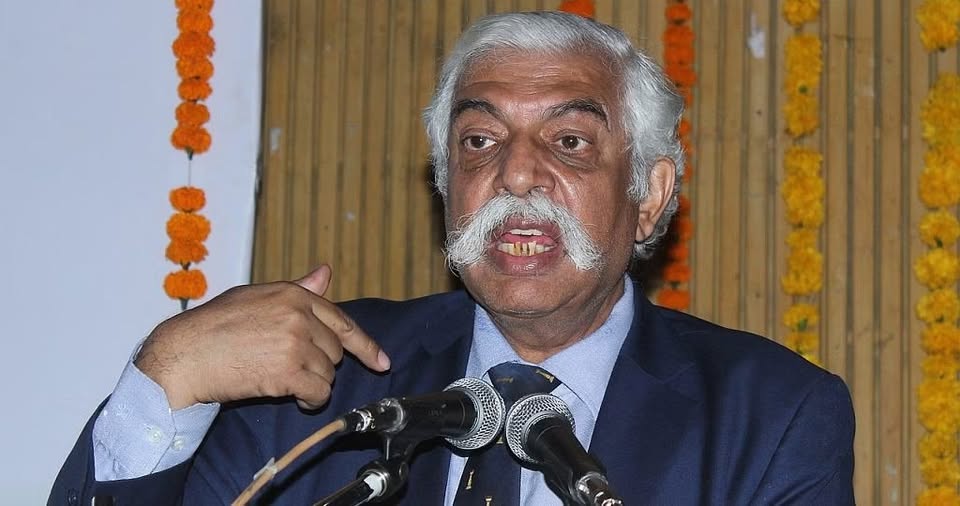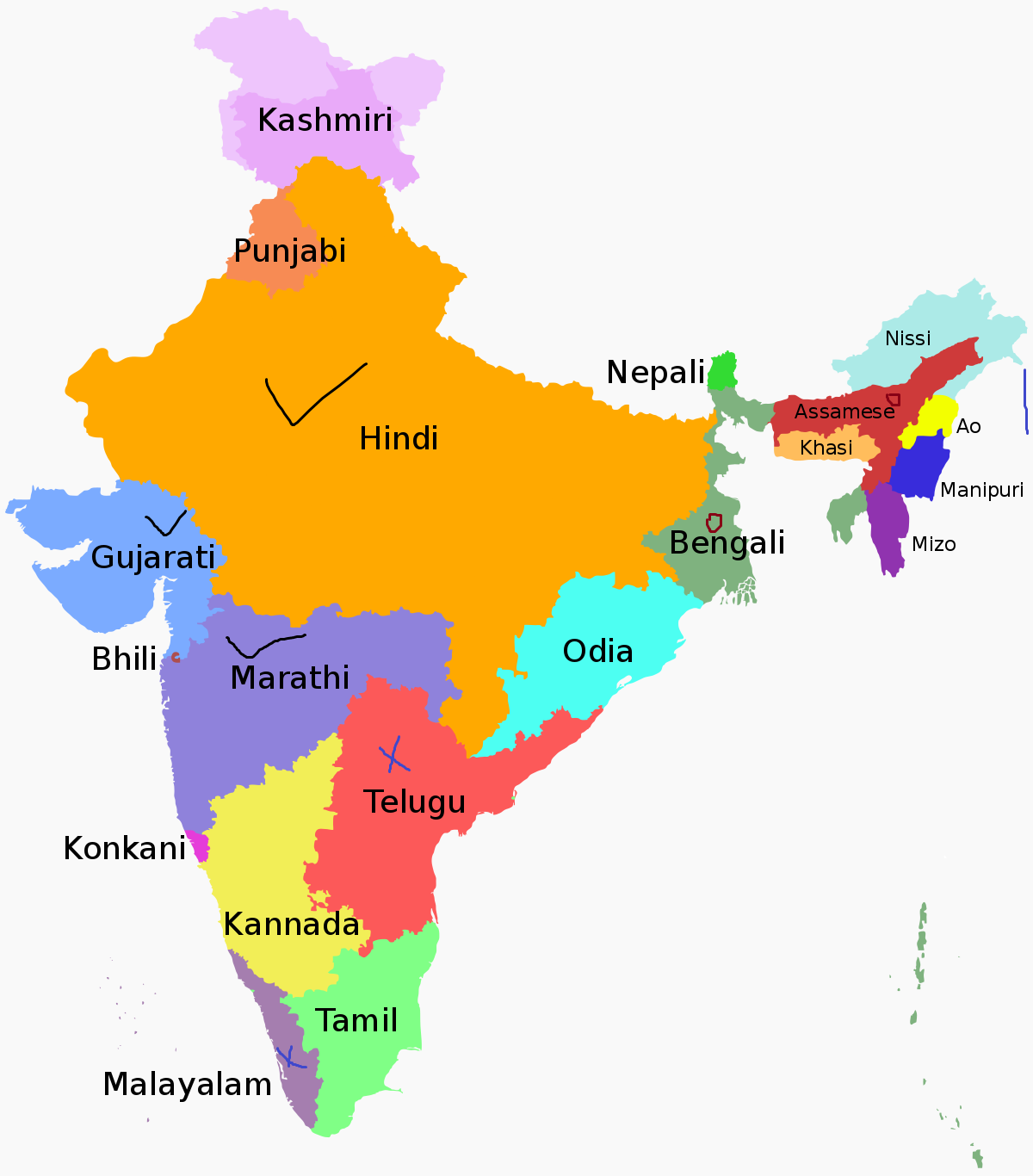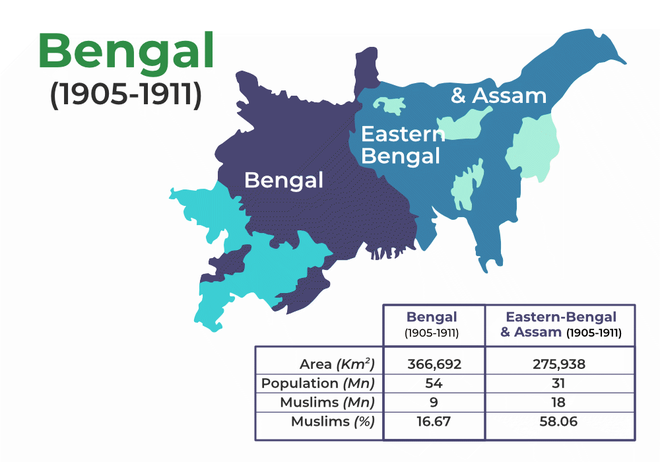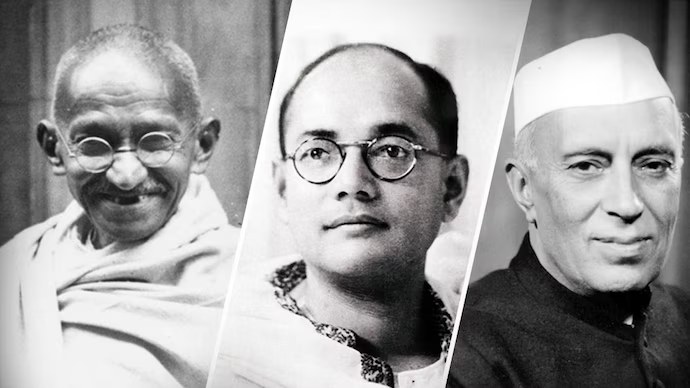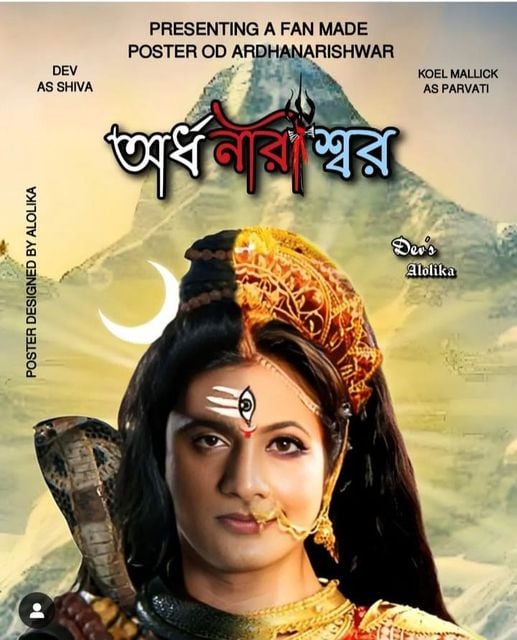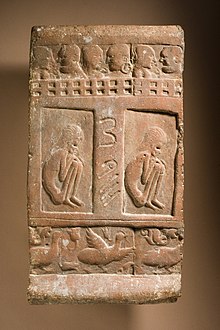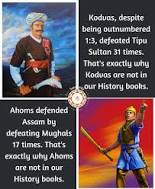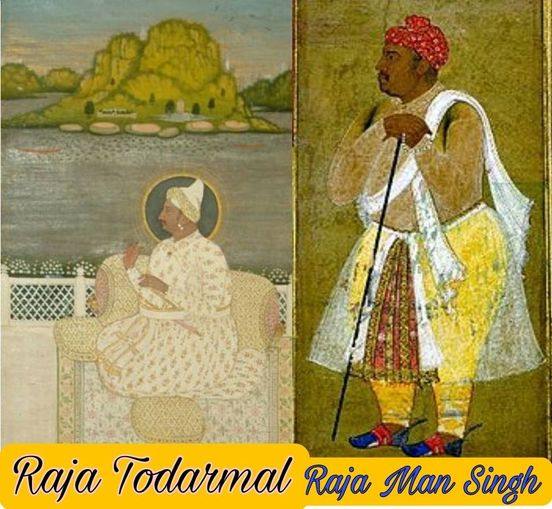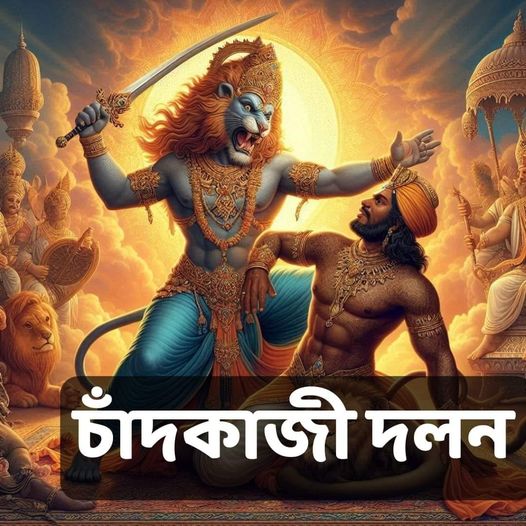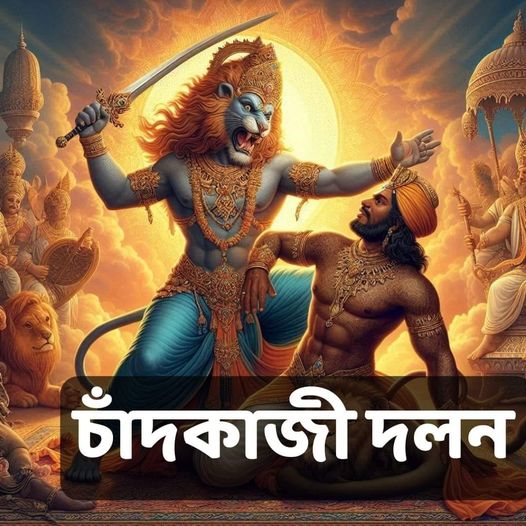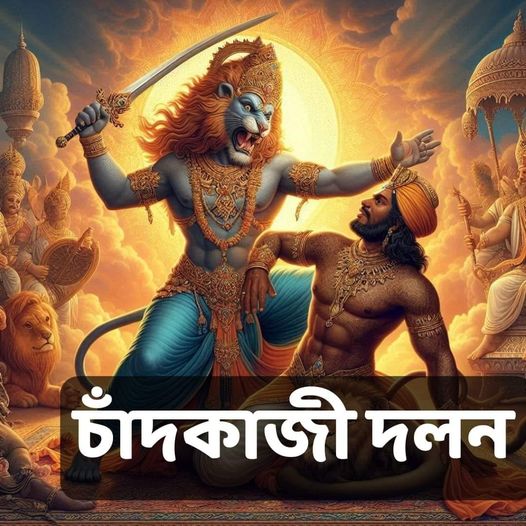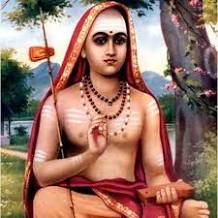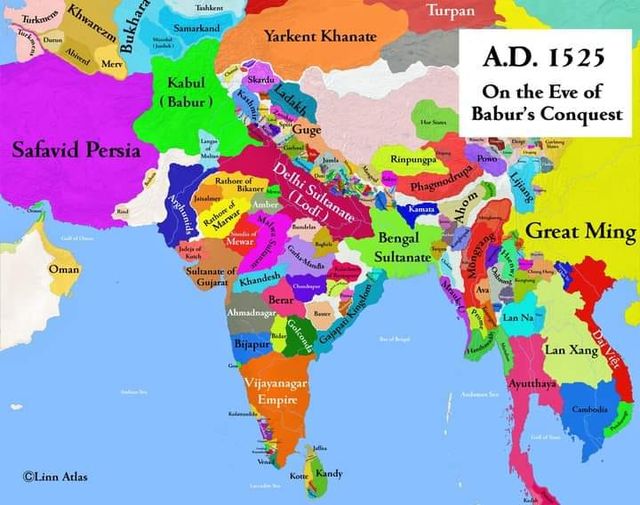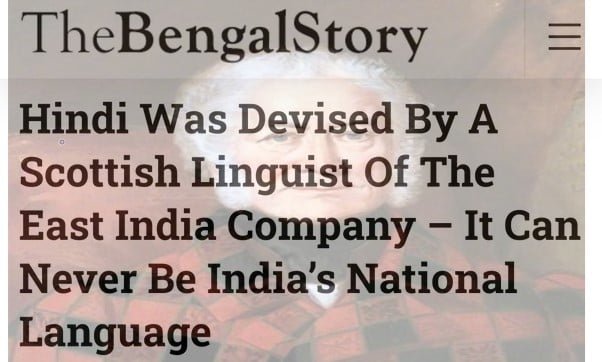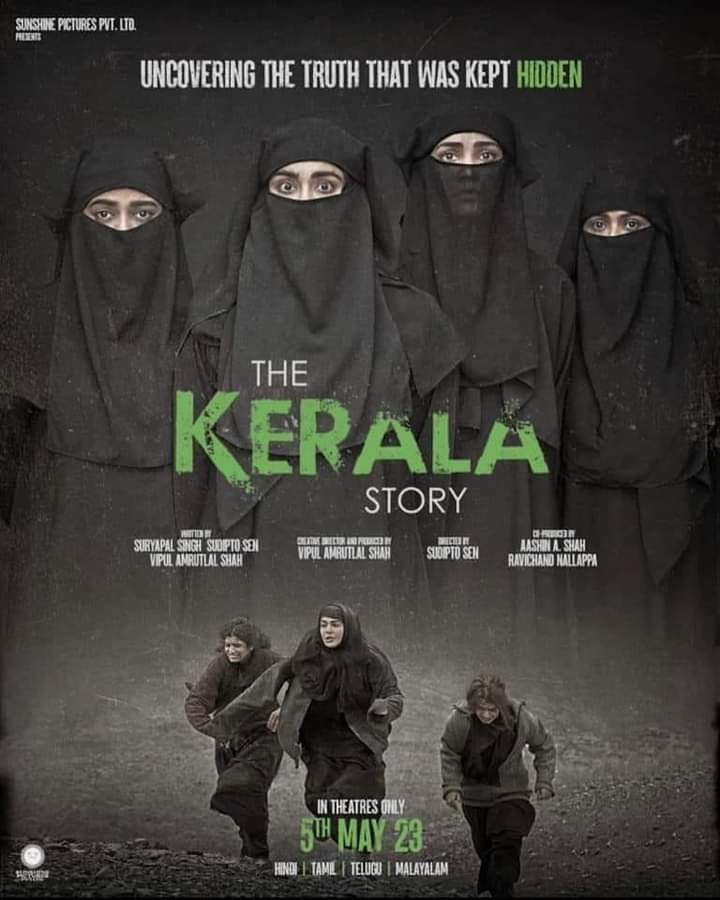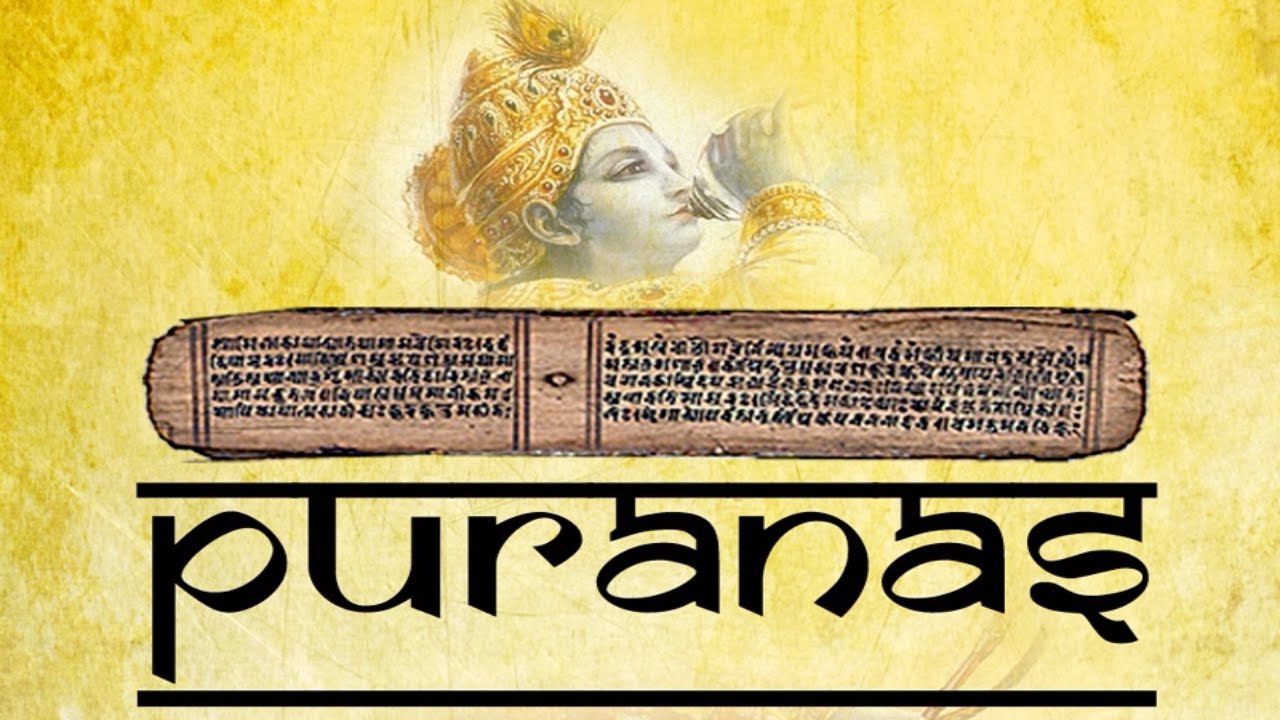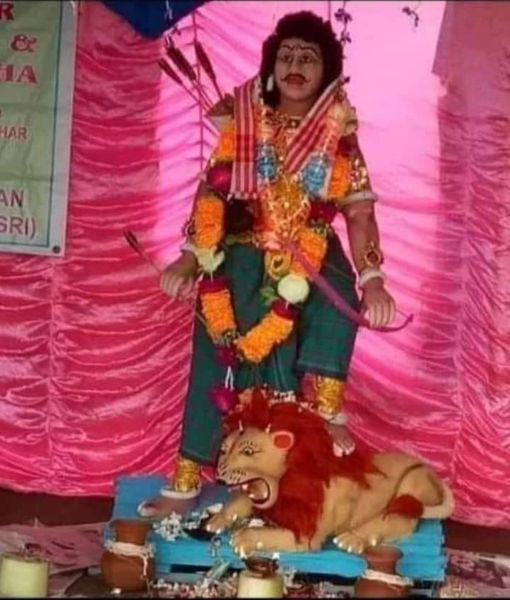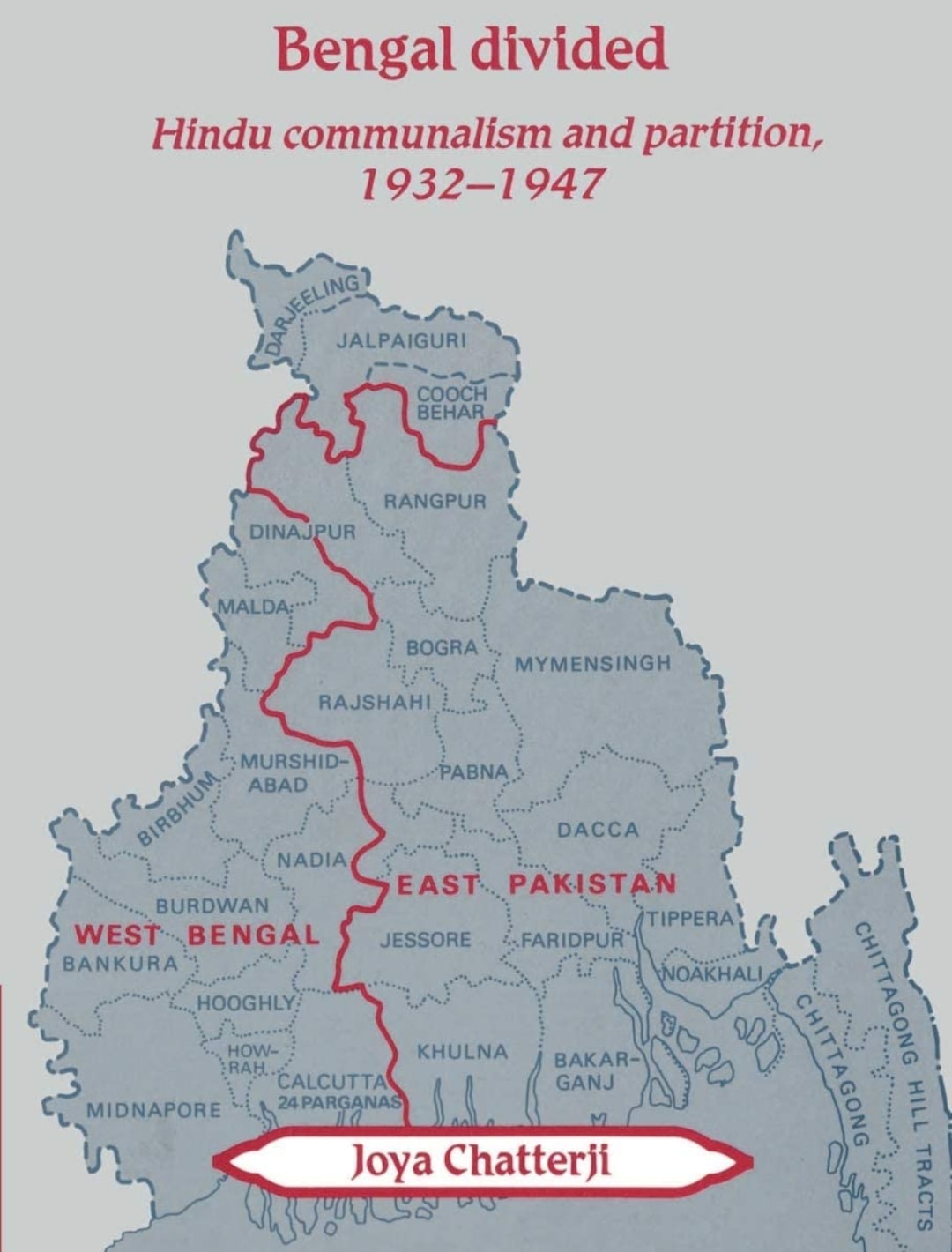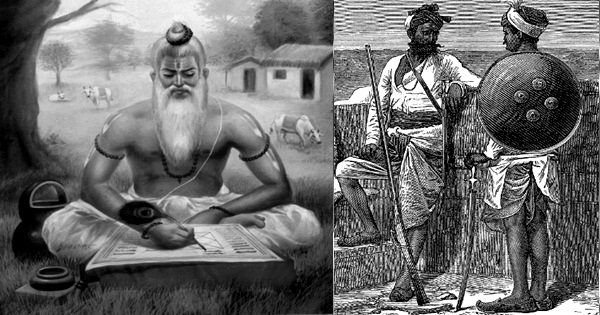আজ লক্ষ্মী পূজা ১৯৪৬ সালে এই দিনে নোয়াখালী বুকে শুরু হয় এক নির্মম হত্যাকাণ্ড।
বিভিন্ন আর্টিকেল ও কিছু বই থেকে এই হত্যাকাণ্ড নিযয়ে একটি ছোট্ট সংস্করণ তৈরি করেছি এই সংস্করণ থেকে এই ঘটনাটির কিছু হত্যাযজ্ঞ ও গান্ধী ষজির স্বেচ্ছাচারিতা অংশটি তুলে ধরছি।
নােয়াখালির দাঙ্গায় চিত্ত দত্তরায়ের আত্মাহুতি :
শায়েস্তানগরের চিত্ত দত্তরায়ের বাড়ি কয়েক হাজার মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর বৃদ্ধ মা ও সন্তানদের নিজের বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে নিজেও গুলিতে আত্মহত্যা করেন। গুলি না থাকায় তার স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান রক্ষা পায়।
সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমন :
“এমনই একটি দল স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এরপর জনতা সুরেন্দ্রবাবুর কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা অনেক হিন্দুনারী ও শিশু ঐ কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই আগুনে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। যারা কোনোক্রমে এই জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদেরও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমন-
“অপর একটি দল নোয়াখালির District Bar-এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি (করপাড়া গ্রাম) আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে দাঙ্গাকারীরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশের হিন্দুগ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দেবস্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রলাল রায় বেগমগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এবং দ্রুত পুলিশী নিরাপত্তা দাবী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশাসনিক কোন সাহায্যই তিনি পাননি।”
“পরদিন সকাল আটটায় এক বিরাট জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেন। এভাবে পর পর তিনবার দাঙ্গাকারীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য চতুর্থব ↑ সফল হয়। মুসলীম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে আক্রমণকারীরা প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর তাঁর পরিবারের সবাইকে এবং সবশেষে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করা হয়। ***
(৫০) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46
রাজেন্দ্রলাল রায়ের কাটা মাথা একটি রূপার থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়। গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে তাঁরই দুই সেনাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের দুই সুন্দরী মেয়েকে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করে।”
রাজেন্দ্রলাল রায় বা সুরেন্দ্র কুমার বোসকে এভাবে হত্যা করার পিছনে মুসলীম লীগ নেতাদের যে পরিকল্পনা ছিল তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন
রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই অধ্যাপক এম. এল. রায়। ইনি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন,
“মুসলমানরা সমস্ত নোয়াখালিকেই ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তাই ওরা বেছে বেছে এমন লোকদেরই প্রথম আক্রমণ করেছিল যাঁরা ওদের বাধা দিতে পারতেন। আমাদের পরিবারের সকলের মৃত্যুর এটাই একমাত্র কারণ।
কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। পুলিশ কখনোই আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে যায়নি, বরং তাদের ‘রক্ষাকর্তা’র ভূমিকা পালন করতে অস্বীকার করেছিল।
সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস নোয়াখালি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন,
"No Police help was given to the persons and families attacked though timely appeals for help were made."**
গােপাইবাগের দাসদের বাড়ি :
কয়েক হাজার মুসলমান এই বাড়ি আক্রমণ করে ১৯ জন পুরুষকে নির্মভাবে হত্যা করে। অর্ধমৃত পুরুষদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহিলাদের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার।
গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতা
নোয়াখালিতে হিন্দুদের এই মুসলমান বর্বরতা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য গান্ধীজীকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু মহাত্মা নোয়াখালি আসতে সম্মত হলেন না। কারণ নোয়াখালি গিয়ে তাঁর 'কর্তব্য' কী হবে 'ঈশ্বর' তাঁকে নির্দেশ দেননি। তাই দাঙ্গ ।পীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ জানিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন।
দিল্লীতে বসে গান্ধীজী যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া হল : "Ever since I have heard the news of Noakhali, indeed, ever since the blood bath in Calcutta, I have been wandering what my duty is God shall show me the way."**
গান্ধীজী নোয়াখালির হিন্দুদের মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক অসাধারণ 'অহিংস' পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের আহ্বান জানালেন “তারা যেন কখনোই অহসায়ভাবে মৃত্যু বরণ না করে। বরং, তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরোবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।” ধর্ষিতা বা অপহৃতা মেয়েদের কাছে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন, তারা যেন তাদের অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ, “মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুতরাং খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং এর জন্য একটুও শোক করা উচিত নয়। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর এই অত্যাচার (ধর্ষণ ও অপহরণ) বন্ধ হবে।" (women must know how to die... women (should) face death bravely and without a murmur. Then only would the terrible killing now going on, stop)**
গান্ধীজীর অহিংসার এই উদ্ভট ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি আচাৰ্য্য কৃপালনী। তিনি তখন নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন, “গত কয়েকদিন ধরে আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কিছু করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর (হিন্দু) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।” (from what I have seen and heard the day before and yesterday. I am clearly of the opinion that whatever the Government's, provincial or central, may or may not do, every Bengali, male or female, has to defend himself or herself.)**
আচার্য্য কৃপালনী আরও বললেন, “আমি যদিও সম্পূর্ণ অহিংসার বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রত্যেক বাঙালীর সামনে আমি রাজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর পরিবারের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই যাঁরা দুদিন ধরে লড়াই করে আক্রমণকারী উন্মত্ত জনতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ১
রেফারেন্স
Kripalani: Gandhi-His Life and Thought.
বিনয়ভূষণ ঘোষ : দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও বাঙালী
V. V Nagarkar-Genesis
Amrita Bazar Patrika.(1946)
The Statesman (1946)
Pirzada Foundation of Pakistan
R. C. Majumdar: History of the Freedom Movement. Vol-3
Mcinery Papers. 1976
G. D. Khosla: Stern Reckoning: A Survey of the Events before and following the Partition of India
Bengal Press Advisory Committee Report, 1946 (Oct.)
V. P. Menon Transfer of Power
মূল বই - নোয়াখালী নোয়াখালী
Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman
Historical Hindu 30-March-2025 by east is rising১৯৪৬-৪৭ এর বেঙ্গল division কে বাঙ্গালী হিন্দুদের একটা বড় অংশ একটা সাফল্য মনে করে। Hard কমিউনিস্ট বাঙালি হিন্দুকেও দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের আলাদা হয়ে যাওয়াকে একটা achievement ভাবতে। কিন্তু, আদৌ কি তাই?
উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে।
প্রথমেই একটা Crystal Clarity রাখা দরকার - সেটা হল পশ্চিম পা কিস্তান ও পূর্ব পা কিস্তান এক নয়।
১. বর্তমান পা কিস্তানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর আফ গানিস্তান অর্থাৎ, বর্তমান পা কিস্তানের ৩ দিকের ২ দিকই ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ দ্বারা আবৃত। কিন্তু, পূর্ব পা কিস্তান বা, বর্তমান বাং লাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভাগ এবং, যেকোনওদিকে সুদূর সীমান্ত অব্দিও কোনো ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ অনুপস্থিত। এটা একটা গভীর demographic difference
২. অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুরা কোনোভাবেই Minority ছিলনা। ৪৮-৫২ এর Ratio তে, ৪৮ যাদের সংখ্যা তাদেরকে কোনোভাবেই Minority বলা চলেনা।
৩. ১৯৪০ এর দশকে বাংলাভাষী মুস লমানদের হাতে মোটের ওপর অর্থ ছিলনা। তাদের অনেকেই স্বচ্ছল ছিল কিন্তু, উচ্চবিত্ত ছিলনা কেউই। আর্থিকভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারকাছ এও কেউ ছিলনা তারা। শিক্ষায় ও আন্তর্জাতিক Connections একেবারেই ছিলনা তাদের।
৪. ব্রিটিশ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে বাঙালি হিন্দু UC দের সম্পর্ক Way better ছিল যেকোনো মুসম্মান নেতার থেকে।
এগুলো ছিল হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের কিছু sharp edge! তাহলে, এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা যেত?
১. বাংলায় উগ্র বাংলাবাদ এর প্রচার, এবং বাংলায় বসবাসকারী পাঠান, ইরানি, পাঞ্জাবি মুস দের eliminate করা।
২. হিন্দুস্থানী UC হিন্দুর বাংলায় প্রয়োজন না থাকলেও, খুব সহজেই হিন্দুস্থানী Non UC হিন্দু এবং, কিছুক্ষেত্রে NE এর লোকদের বাংলায় ঢুকিয়ে ২০-২৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড বাংলায় হিন্দু পপুলেশন ৬০% আশেপাশে করে নেওয়া যেত।
৩. এই পুরো process টাকে continue করানোর জন্য রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যে Connections প্রয়োজন সেটা হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের ছিল।
৪. হিন্দু UC দের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে Movement টা হচ্ছিল, সেটা অনেকটাই ১৯৮০ এর দশকেই বিহার UP তে যাদব, বা রাজস্থান হরিয়ানাতে জাঠ দের উত্থানের সমতুল্য। দুটোই জমিদার শ্রেনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জোতদার (Mid Caste) শ্রেনীর ক্ষমতা দখলের কাহিনী। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মূলত Middle Caste জোতদার সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল, যারা পূর্বে ই সলাম নিয়েছিল।
এটার একমাত্র এবং, "রামবান" Counter হল, Communism। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার শ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় জমিদারি ছেড়ে দিয়ে Communist Movement এ নিজেদের সঁপে দিয়ে, জোতদার মধ্যবর্ণ এর সাথে ভূমিহীন কৃষকদের সফল সংঘর্ষ তৈরি করতে সক্ষম হত তাহলে, তারা বাংলার ক্ষমতা Clean sweep করতো আবার আরেকবার।
**এমনিতেও ব্রিটিশ আমলে যখন ব্যবসার ভিত্তিতে জমিদারি নিলামী শুরু হয়, সেই তখন থেকেই জমিদারির রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়।
৫. এখনও অব্দি, চার নম্বরে বলা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কেবল ও কেবলমাত্র সম্ভব ছিল যদি ভূমিহীন সমাজ এই কাজে হিন্দু উচ্চবর্ণকে সহায়তা করতো। ভূমিহীন সমাজ অর্থাৎ, নমশূদ্র, পো দ আদি সমাজ। ভূমিহীন হিন্দু সমাজ ও ভূমিহীন মুসলমান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি Ground Zero তে ভূমি অধিকার করে থাকা কৃষক সমাজ (যারা ধর্মে মুলমান পূর্ববঙ্গে, ও হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে) এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু, এর জন্য দরকার হতো, যোগেন মন্ডলদের সাহায্য, যা পাওয়া যায়নি।
৬. Communist রাষ্ট্র একমাত্র Communism বাদে অন্য কোনো কিছুর সামনে মাথানত করেনা। Hinduism এমনিতেও communist রাষ্ট্রকে challenge করার জায়গায় নেই, কিন্তু ইস ,লামপন্থী faction যদি এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেত, সেক্ষেত্রে Communist রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য থাকতো। USSR বা, Communist China এর সমান শ্রেনীর action সেক্ষেত্রে হত। অর্থাৎ, হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা Communist রাষ্ট্রেই হত।
Conclusion - উপরিউক্ত তত্ত্ব পুরোটাই একটা Realizable Plausibilistic Theory। যা করলেও করা যেত।
তবে, এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই, বর্তমান বাংলাদেশ আজকের পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে গেছে প্রায় সমস্ত parameters এই, যে বাস্তবতাকে অধিকাংশ বাঙালিই মানতে চায়না কারণ, সেটা মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গ যে একটা Failed Project সেটা মেনে নেওয়া হয়।
Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman
Historical Hindu 30-March-2025 by east is risingবাংলায় ব্রাহ্মণ বাদে বাকি কেউ সবর্ণ নয় - কথাটি আদতে পুরোপুরি ভুল নয়।
বাংলায় ব্রাহ্মণ পরবর্তী দুটি উচ্চজাতি হল - কায়স্থ ও বৈদ্য।
Interestingly, বাংলায় এই দুটি জাতির শৈক্ষিক মান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান চিরকাল ব্রাহ্মণদের প্রায় সমকক্ষ। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার প্রথম বাংলা মহাভারত রচিত কাশীরাম দেব (কায়স্থ) দ্বারা।
মালাধর বসু এর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য হোক - মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে আমরা প্রচুর সংখ্যক কায়স্থ ধর্মজ্ঞাতার নাম পাই।
বাসুদেব ঘোষ গোস্বামী, নরোত্তম দত্ত ঠাকুর - এদের কথা বাদই দিলাম। ঈষৎ, পূর্বকালের কালীপ্রসন্ন সিংহ এর, বা রাজশেখর বসু এর মহাভারত হোক, কিংবা ধর্মজগতে ঋষি অরবিন্দ বা, স্বামী যোগানন্দ বা, স্বামী প্রনবানন্দ বা, স্বামী বিবেকানন্দ - এঁরা সকলেই কায়স্থ। আসামের সর্ববৃহৎ ধর্মগুরু শংকরদেব কায়স্থ। বিদ্যতীর্থ (মিত্র) এর মত কায়স্থ ব্যক্তিত্ব সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় টোলের আচার্য পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছেন অতীতে।
উল্লেখজনকভাবে, বাংলায় ব্রাহ্মণদের পরে সবথেকে অধিক সংখ্যক ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাতা কিন্তু কায়স্থরাই।
জনসংখ্যা অনুযায়ী কায়স্থদের সংখ্যা ব্রাহ্মণদের সমতুল্য। তাই, বাংলার ধর্মীয় জগতে এত অধিক সংখ্যায় কায়স্থদের উপস্থিতি প্রমাণ করে,
যে কায়স্থ কদাপি *কেবল যোদ্ধা জ ঙ্গী Tribe নয়*,
কায়স্থ জাতির মধ্যে একটা ভীষণ Strong Brahminical Factor আছে।
পূর্বভারতে তো নয়ই, এমনকি সমগ্র উত্তর ভারতে কায়স্থ বাদে অন্য অব্রাহ্মণ কোনো জাতি খুঁজে দেখানো সম্ভব নয়, যারা ধর্মীয় বিষয়ে যুগ যুগ ধরে Involved হয়েছে, বা যারা শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ।
কোলকাতা Medical College এর First Generation Batch এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল ৫ জন, বৈদ্য ছিল ৫ জন, কায়স্থ ছিল ১৫ জন। (পূর্বেই বলেছি, কায়স্থ জনসংখ্যা ব্রাহ্মণদের Comparable, যা জনপ্রতি কায়স্থ পরিবারে শিক্ষার হার উল্লেখজনকভাবে বেশি প্রমাণ করে। )
উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষার গুণ বা, "ব্রাহ্মণগুণ" সুপ্রাচীন অতীত থেকেই বিদ্যমান। অথচ, কায়স্থদের সংস্কার হয় ক্ষত্রিয় মতে।
অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় বা, ব্রাহ্মণতুল্য ক্ষত্রিয়" - কায়স্থ জাতির সামাজিক মান্যতার ব্যাখ্যা সম্ভব কেবলমাত্র এই শব্দের দ্বারা।
মিথিলার বিখ্যাত মৈথিলী ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যাপতি এর রচনা এই যুক্তিকে আরও বলিষ্ঠ করে। বিদ্যাপতি লিখছেন - "কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নতর এবং রাজপুত অপেক্ষা উচ্চতর জাতি"।
উল্লেখ্য , রাজপুত জাতি ক্ষত্রিয় হলেও, শিক্ষিত নয় বা, ধর্মীয় বিষয়ে কোনো অবদান পাওয়া যায়না এদের। বাঙালি কায়স্থ জাতির সামরিক অবদান ও ধর্মীয় অবদান দুইই পাওয়া যায়। তাই, শুধু ক্ষত্রিয় বলা সম্ভবত কায়স্থ জাতির সামাজিক অবস্থানের কিছুটা ভুল পর্যবেক্ষণ। কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা সম্ভব - ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা, ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় হিসেবে।
অন্যদিকে বদ্যিদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, এরাও যথেষ্ট শিক্ষিত জাতি। এবং, ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজার অধিকার প্রাপ্ত না হলেও, এঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য মিশ্রণ বলে থাকেন।
অর্থাৎ, কায়স্থ = ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়
এবং, বৈদ্য = ব্রাহ্মণ + বৈশ্য
যা প্রমাণ করছে, বাংলার দুটি অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের দুইজনের মধ্যেই Strong Brahminical Elements আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য - তিনটি জাতি জাতিগত ও বৈবাহিকভাবে আলাদা হলেও, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাংলায় ব্রাহ্মণ বাদে কোনো সবর্ণ নেই কথাটার মধ্যে তাই খুব একটা ভুল নেই, কারণ এখানে ব্রাহ্মণ বলতে জাতিব্রাহ্মণ বাদেও ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন অন্য দুই উচ্চজাতিকেও Mean করা হয়েছে।
Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman
Social Hindu 05-March-2025 by east is risingশুধু লোহার ব্যবহার জানলেই লৌহ যুগ আসেনা।
লৌহ যুগ আনতে হলে তিনটে শর্ত পালন করতে হবেঃ
১) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত কৃষি জমিতে লৌহ লাঙ্গল ব্যবহার করে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে,
২) তার পরিণামে বাড়াতে হবে জন্ম হার ও জনসংখ্যা (অর্থাৎ শক্তিশালী পিতৃতন্ত্র আসতে হবে) এবং
৩) এই বর্ধমান জনসংখ্যা লৌহ কুঠার ব্যবহার করে জঙ্গল কেটে আরও বেশি বেশি জমি নিয়ে আনবে কৃষি ও বাণিজ্যের উদ্যেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে।
তামিল নাড়ু-তে ১ পাওয়া যায়নি আর ২ হওয়ার কোন নিদর্শন নেই।
শুধু ৩ অর্থাৎ লৌহ কুঠার পাওয়া গেছে।
ফলে লোহার কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার হলেও লৌহ যুগ আনতে পারেনি দ্রাবিড়েরা।
সেটা হিতাইত-রাও (বর্তমান তুর্কি) আনেনি কারণ তারা লোহার জিনিস কেবল উচ্চবিত্ত-দের বিলাস দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করেছে।
লৌহ যুগ নিয়ে আনে মূলত অসিরীয়রা (বর্তমান উত্তর ইরাক)।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 24-January-2025 by east is risingএজন্যই বলি ধর্মের হোতা হবার আগে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।
2000 সালেও 13 কোটির বেশি মুসলিম ভারতে বসবাসকারী ছিল।
আমার সাথে যেসব মুসলিম ছেলে পড়তো, তাদের অনেকের পরিবার আমি দেখেছি, অনেকেই বিয়ে করেছে তবে ওদের পিতামাতার কোন চারটে বিয়েও নেই আর 8-10 জন সন্তান ও নেই।
বড়জোর 4 জন দেখেছি বেশি।
এবার হিন্দুদের মেয়েরা বাচ্চা নিতে চাইছে না তার কারণ আগে স্বামীজি বের করুক।
সবথেকে বড় কথা এই সব ভেকধারীরা হিন্দু পুরুষ বিদ্বেষী পশ্চিমা মদদপুষ্ট " হিন্দু কোড" বিলের বিপক্ষে বলে না,যে আইনের কারণেই প্রায় 33% হিন্দু পুরুষ ভারতে বিয়েই করছে না কারণ জেনে বুঝে কেউ তো আর গরল পান করতে যাবে কথা।
সবথেকে বড় কথা, অতুল সুভাষের কেইসের পর ভারতে হিন্দু পুরুষ যে আইনিভাবে চরম নির্যাতনের স্বীকার সেটা বার বার উঠে আসছে।
একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার সুপ্রজনন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করে বেশিরভাগই হিন্দু নারীপুরুষ বিয়ে করে দেরীতে আর বাচ্চা ও নেয় কম(আসলে হয় ও কম)।
বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা আইনি অধিকারে নিজেদের যা খুশি তাই করছে এবং নিজেদের আকর্ষণীয় রাখতে বাচ্চা ও কম নিচ্ছে।
একারণেই বিগত আদমশুমারিতেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার 80 এর নিচে নেমে গেছে।
আরে মুসলমান তো আর হিন্দুদের বাচ্চা হওয়াতে বাঁধা দিচ্ছে না।
সবথেকে বড় কথা আমি তো জানি মুসলিম জনসংখ্যা আছে 25 কোটি, স্বামীজি বলছেন 38 কোটি, অনেকেই আবার 40 কোটিও বলে।
মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু বিবাহকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয় তখন তারা এগোবেই তার উপর নিজেদের মুসলমান আইন থাকায় তারা পশ্চিমা আইনের স্বীকার হিন্দুদের মতো হয় না।
মুসলমানদের মধ্যে ওতো নারী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা নেই।
সবথেকে বড় কথা এখন তো হিন্দু পুরুষরাই মনে মনে ইসলামধর্মে যে নারীর পাশাপাশি পুরুষদের ও অধিকার আছে সেটা বলছে।
শুধু তাই নয় বিভিন্ন কারণ না থাকলে অনেকেই ইসলাম নিয়ে নিবে।
স্বামীজিকে বলবো উণি আগে পশ্চিমা মদদপুষ্ট পুরুষ বিদ্বেষী এবং এক চোখা নারী সাপেক্ষিক হিন্দু আইনের বিপক্ষে উনারা লড়ুক, পুরুষদের পক্ষে আইন এনে আইনের সমানাধিকার দিক নয়তো তারা ধর্ম ছাড়বে কারণ সবাই সাধুও হবে না,সবাই অতুল সুভাষ ও হতে চাইবে না।
Read MoreAuthor: Prosenjit Dey
Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 15-January-2025 by east is risingভারত বিশেষ করে কাশ্মীর ও পঃ বঙ্গ-আসাম-উঃ পূঃ বিহার জুড়ে মুসলমান উচ্ছ্বেদ কেন আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে করতেই হবে হিন্দি গুজারাতি শাসকদের?
ভারত কি প্রত্যাশা করে আর বৃহৎ ভারতের?
- না।
কেন?
- কারণ দঃ এশিয়াতে মুসলমান জনসংখ্যার শেয়ার ১৯৪১-এ ছিল ২৪% আর ২০২৪-এর শেষে ৩৮%। অর্থাৎ বৃহৎ ভারত তৈরি হলে (ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল আফঘানিস্তান এক দেশ হয়ে গেলে) মুসলমান ভোটার শেয়ার ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যাবে আর তখন ক্ষমতা আর হিন্দি গুজারাতি-দের হাতে কুক্ষিগত থাকবেনা। তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকরা বৃহৎ ভারত গড়ার বিরুদ্ধেই থাকবে, তা মুখে যতোই বৃহৎ ভারত চাই বলুক না কেন।
তাহলে ২০২৪-এ ভারতের হিন্দি গুজারাতি শাসকদের পরিকল্পনা কি?
- ভারতের হিন্দি গুজারাতি শাসকরা বর্তমান ভারত থেকে মুসলমান-দের বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।
কিভাবে ভারত থেকে মুসলমান-দের বের করে দেওয়া হবে?
- ১। মুসলমান লারীদের মধ্যে লারীবাদ ঢোকাতে হবে যাতে তারা যৌন স্বাধীনতা চায়। আর সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির লারী যৌন স্বাধীনতা পেলেই সংখ্যাগুরু ক্ষমতাবান জাতির পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং এর ফলে সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির পুরুষদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির লারী বেশি সন্তানের জন্ম দিতে অস্বীকার করবে। মুসলমানদের জন্মহার ভারতে হিন্দুদের চেয়েও কমিয়ে দিলে তাদের নিয়ে আর চন্তার কিছু থাকবেনা। মোটামুটি দালাল-বেশ্যার জাতিতে পরিণত হবে তারা। (ভালো করে বুঝতে এই লেখা পড়ুন https://www.eastisrising.in/view-news/174 )।
২। মুসলমান জনসংখ্যা যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের না না ভাবে "অপরাধী" হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া। যেমন- "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" না "জঙ্গী" বা "লারী স্বাধীনতা বিরোধী", ইত্যাদি। এর পরের ধাপ হবে এই উচ্চ জনসংখ্যার অঞ্চলে তথাকথিত দাগিয়ে দেওয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানো। পঃ বঙ্গ-নীম্ন আসাম-উঃ পূঃ বিহার, পঃ ইউপি, হায়দেরাবাদ সংলগ্ন তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক অঞ্চল এবং উত্তর কেরালা ও কাশ্মীর উপত্যকা- এই অঞ্চলগুলোতে মুসলমান জনসংখ্যার শেয়ার উচ্চ (২৫% থেকে ৭৫%)।
এদের মধ্যে বাংলাদেশের পাশেই অবস্থিত পঃ বঙ্গ-নীম্ন আসাম-উঃ পূঃ বিহার ও পাকিস্তানের পাশেই অবস্থিত কাশ্মীর উপত্যকা হিন্দি গুজারাত শাসকদের মাথা ব্যথার মূল কারণ। তাই কাশ্মীরি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদেরই বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে আর হবে। এর সঙ্গে বলা যায় যে বাঙালি হিন্দু ও শিখরা যদি যথাক্রমে বাঙালি মুসলমান ও কাশ্মীরি মুসলমানদের সাথে হাত মেলায় তাহলে হিন্দু গুজারাতি শাসকদের সাম্রাজ্য অনিবার্য ভাবেই ভেঙ্গে পড়বে। কাশ্মীরি মুসলমানদের সাথে শিখরা হাত মেলালে পঃ ইউপি-র মুসলমানেরাও তাদের সাথে একত্রিত হতে পারবে। আবার বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান হাত মেলালে উঃ পূঃ বিহার, সিকিম ও উঃ পূঃ রাজ্যগুলোও একত্রেই হাতছাড়া হয়ে যাবে।
তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকদের আজ নয় কাল পঃ বঙ্গ, আসাম ও উঃ পূঃ বিহার জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাতে হবে। তারা চাইবে রোহিঙ্গাদের মতো তাদের জোড় করে বাংলাদেশে রিফিউজি করে পাঠিয়ে দিতে। হিন্দি গুজারাতি শাসকরা এটা চাইবে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। কারণ ২০৩০-এ বাঙালি হিন্দু ও আসামী হিন্দুদের জনসংখ্যার শেয়ার দ্রুত কমে যাবে কারণ এই দুই জাতির মধ্যে বুমার প্রজন্মই (যাদের জন্ম ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে) সংখ্যায় অধীক এবং তাদের মৃত্যু হবে ২০৩০-এর দশকেই। বলা বাহুল্য এই দুই জাতির জেন এক্স (যাদের জন্ম ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে) ২০৩০-এর দশকে ৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সী হবে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। অন্যদিকে বাঙালি ও আসামের মুসলমানেরা হবে তারুণ্যে ভরপুর। তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকদের হাতে সময় বেশি নেই।
আসলে হিন্দি গুজারাতি শাসকদের পক্ষে বৃহৎ ভারত গড়া সম্ভব না। আবার কাশ্মীর উপত্যকা ও পঃ বঙ্গ-আসাম-উঃ পূঃ বিহার মুসলমান অধ্যুষিত যত হবে ততই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেদের পরিধি বাড়াতে পারবে এমন আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এই অঞ্চলগুলো থেকে মুসলমান উচ্ছ্বেদ না করে উপায় নেই হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যের। আর তা করতে হবে আগামী ৫ বছরের মধ্যেই।
মনে রাখা দরকার বিজেপি যেখানে মুসলমানদের উচ্ছ্বেদ করার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে, কংগ্রেস, তৃনমূল, বামদের মতো দলগুলো কিন্তু মুসলমান লারীকে লারী স্বাধীনতার স্বাদ দিয়ে মুসলমান ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। এদের লক্ষ্য এক, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়টা আলাদা। যেহেতু হিন্দি গুজারাতি শাসকদের দ্রুত বাঙালি মুসলমান উচ্ছ্বেদ ও কাশ্মীরি মুসলমান উচ্ছ্বেদ করতে হবে, তাই আপাতত বিজেপি-কে সামনে রাখা হয়েছে। বিজেপি যখন নিধন চালাবে তখন কংগ্রেস, তৃনমূল, বামদের মতো দলগুলো তখন "জঙ্গী দমন" অভিযানকেই সমর্থন করবে। তাই ভারতের বিশেষ করে পঃ বঙ্গ আসাম ও উঃ পূঃ বিহারের মুসলমানদের আর ভোটের রাজনীতি করা উচিত নয়। এখনই তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে নিকট ভনিষ্যতের নিধন যোগ্যের বিরুদ্ধে।
ভারতের মুসলমান-দের নির্দ্বিধায় বলতে হবে তারা "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" মানবেননা কারণ তা মুসলমান সমাজে লারীবাদ ঢুকিয়ে মুসলমান সমাজকে দালাল-বেশ্যার জাতিতে পরিণত করবে, আবার একই সাথে বুঝতে হবে এমন দেশে গোলাম হয়েই থাকতে হবে যেখানে ভোটব্যঙ্ক দুর্বল। এর মানে এমন দেশ বানানো দরকার যেখানে ভোটব্যাঙ্ক-এর গুরুত্ব থাকবে।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
International geopolitics Hindu feminism 05-January-2025 by east is risingwritten by Zahid Mollah
প্রশ্ন করুন ভারত একটা 'দেশ' নাকি 'সাম্রাজ্য'?
১৯৪৭ সালে ভারত কিন্তু কোনো দেশ হিসেবে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। সত্যি কথা বলতে ভারত পাকিস্তান কেউই স্বাধীন হয় নাই। এরা উভয়েই ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি বা Transfer of Power এর মাধ্যমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছিলো।
ভারতের পলিটিক্যাল বাউন্ডারির বাইরে তখনও কাশ্মীর, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, সিক্কিমের মতো ৫৬৫ টা স্বাধীন প্রিন্সলি স্টেট্ ছিল যে গুলাকে ভারত মিলিটারি আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে নিয়ে নিজের ভূমিতে আত্তীকরণ করেছে।
ভারত হচ্ছে Ex British Empire যেটার মালিকানা পরিবর্তন হয়ে এখন Neo Hindi Empire এ পরিণত হয়েছে। এবং এটার মালিকানা হস্তগত হয়েছে গুজরাটি, মাড়োয়ারি (রাজস্থানি) পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে।
হিন্দি-গুজরাটি কেন্দ্রিক সেই শাসক গোষ্ঠীর অধীনে প্রায় ১১৬টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী শাসিত হচ্ছে যাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে এবং এই সকল জাতিগোষ্ঠী কিন্তু পরস্পর বিরোধী এবং সংঘর্ষ প্রবণ ।
এত্ত কিছুর পরেও ভারত তাদেকে একটা ইউনিয়নের অধীনে কিভাবে রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে?
এর উত্তরে প্রথমটা হচ্ছে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদ (যেটার ভিত্তি মুসলমান বিদ্বেষ) আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভারতের ব্রুটাল মিলিটারি ফোর্স।
হিন্দু জাতীয়তাবাদই ভারতকে বহুধর্মের, বহুভাষিক, বহু সংস্কৃতির দেশ থেকে একটি একক শক্তিশালী থিওলজিক দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। আর এই প্রসেসে মারা পড়বে ভারতের মুসলমানেরা।
ভারতের গুজরাটি মাড়োয়ারি হিন্দি পুঁজিবাদ কেন্দ্রিক শক্তি তাদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের প্রতি ভারতের সামাজিক বুনিয়াদকে যেভাবে বিষাক্ত করে দিয়েছে তাতে ভারতের অমুসলমান সকল জাতিগোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভারতীয় মুসলমানদের মারবে।
এবং এই গণহত্যা সিস্টেমেটিক্যালি নানান উপজীব্যের আড়ালে হবে, দেখে মনে হবে না যে সেখানে গণহত্যা হচ্ছে।
যেমন বিহারি হিন্দুদের উস্কে দেয়া হচ্ছে বিহারি মুসলমানদের উপর, উত্তরভারতে ভারতীয় বাংলাভাষী মুসলমানদের কে বাংলাদেশী দাগিয়ে উস্কে দেয়া হচ্ছে , নর্থ ইস্টে হিন্দু মেইতেইদের উস্কে দিচ্ছে খ্রিস্টান কুকিদের উপর গণহত্যা করতে।
যখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বাংলাদেশী হিসেবে তকমা দিয়ে মারা শেষ হবে, এর পর ধরা হবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুদের। বাঙ্গালী হিন্দুরা যদি স্বেচ্ছায় হিন্দি গ্রহণ করে এবং তাদের ঘরের মেয়েদের ইউপি, বিহারি, রাজস্থানি বা গুজরাতিদের খাটে তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মহাভারতে বিলীন হয় তবে তারা রক্ষা পাবে।
কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের কোনো রক্ষা নাই সেটা এক প্রকার নিশ্চিত।
গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং হিন্দু মনোবলকে পুরুষোচিত জোশে চাঙ্গা করতে ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী তাদের ভারতীয় নেটিভ মাতৃতান্ত্রিক ধর্মগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে।
আর এইখানেই উত্তর ভারতের হনুমান এবং জয় শ্রী রামের উত্থান হয়েছে।
রাম হনুমান কেন্দ্রিক ধর্মীয় উন্মাদনার মূল লক্ষ্য মুসলমানদের ম্যাসকুলিন যোদ্ধা মনোভাবকে কাউন্টার করতে বৃহত্তর হিন্দু পলিটির মধ্যে সহস্রাধিক বছর ধরে লালিত মাতৃতান্ত্রিক ধর্মীয় চেতনাকে হত্যা করে পুরুষোচিত উগ্র মনোভাবের পুনর্জাগরণ ঘটানো।
তাই বাঙ্গুল্যান্ডের সিভিল সোসাইটি এবং আর্মিকে অনুরোধ করবো আপনারা বৃহত্তর কনফ্লিক্টের জন্য প্রস্তুত হন।
Vedic Frontier এর পুনরুত্থানে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ-চীন কেন্দ্রিক একটা সিভিলাইজেশনাল কোর স্টেট্ ওয়ার অসম্ভব কিছুই না।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Theoretical Hindu 12-December-2024 by east is risingপ্রথম প্রশ্ন রাজপুত কারা?
রাজপুত দের দুটি শ্রেণিতে আমরা ভাগ করবো -
১. রাজস্থান অঞ্চলের রাজপুত
২. UP বিহারের ঠাকুর সম্প্রদায়, হিমাচলের খাসি, জম্মুর ডোগড়া
রাজপুত যত Icon এর নাম পাওয়া যায়, তারা প্রত্যেকে প্রথম শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণী এর যে শুধুমাত্র নিজের কোন Icon নেই এবং তারা প্রথম শ্রেণীর Icon Borrow করে কাজ চালায়, তাই নয়; এরা আর্থিকভাবেও অনেকেই বেশি দরিদ্র, এবং Genetics বা চেহারার দিক থেকেও দুই শ্রেণীতে মিল নেই। প্রথম শ্রেণীর রাজপুত দের আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল অনেকেই, এবং চেহারার দিক থেকে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ না হলেও, একেবারে বাজে দেখতে হয়না। Whereas, একটা average ভোজপুরি ঠাকুর এর চেহারা অতীব জঘন্য।
বস্তুতঃ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০ -৯০% আদিতে কেউ Gond, কেউ পাসি ইত্যাদি জাতির অংশ ছিল। মুঘল আমল এর শুরুর দিক থেকে Pre Brittish Era অব্দি, মোটামুটি যেকোনো কাস্ট এর লোক যে একটি পয়সা করতো, কিংবা লোকবল সঞ্চয় করতো (সেটা ডাকাতি করার লোকবল বহুক্ষেত্রে), তারা রাজপুত কাস্ট এর অন্তর্গত হয়ে যেত, এই পদ্ধতির নাম Rajputisation বা, রাজপুতকরণ। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, রাজস্থান বাদে অন্য অঞ্চলের রাজপুতদের Fake রাজপুত বলে উল্লেখ করবো, Central Politics (দিল্লী) এ এদের প্রভাব অতীব সামান্য হওয়ায় এদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখলাম না।
তবে, Rajputisation এর মজা হল - এই পদ্ধতিতে নতুন রাজপুত হওয়া কোন ব্যক্তি/ পরিবার মূল রাজপুত বা, রাজস্থানি রাজপুতের থেকে বংশ মর্যাদায় নিম্নতর বা, অবিশুদ্ধ বলে পরিচিত হল।
এখান থেকে দেখছি Rajputisation এর দুটো Interesting Effect ~
১. মূল রাজপুত সেনানায়কের সেনায় Manpower Supply দেওয়া এর সমস্যা মিটছে একদিকে, তেমনই একজন Fake রাজপুত নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদে একজন মূল রাজপুতের সেনায় মরতে ও মারতে প্রস্তুত থাকছে।
২. যেকোনো নিম্নজাতির কেউ যে আর্থিকভাবে সক্ষমতা বা, লোকবল বৃদ্ধি করছে, তার Caste Conversion করিয়ে তাকে রাজপুত বানিয়ে দেওয়ায় রাজপুত বাদে দ্বিতীয় কোন কাস্ট এর Military Activity Run করার ক্ষমতা থাকছেনা উত্তর ভারতে।
এখনও অব্দি আমাদের discussion এ এটা প্রমাণ হয়েছে, Rajputisation এর process কতটা Effectively পশ্চিম ভারতীয় মূল রাজপুত দের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই মূল রাজপুত ঠিক কারা?
একটা Conceptual Clarity এখানে আগেভাগে দরকার। সেটা হল - রাজস্থান কিন্তু আর্যধর্মের কেন্দ্র নয়। বাংলাকে যেমন মূল আর্য সংস্কৃতির বলয়ের বাইরে assume করা হতো, রাজস্থানকেও তাই। ১৬ মহাজনপদের একটি জনপদও আজকের রাজস্থানে ছিলনা। তবে, এই মূল রাজপুত কারা?
মূল রাজপুত হল আদতে গুপ্ত আমলের শেষের দিকে ভারতে আক্রমণ করা, ও শেষে পশ্চিম ভারতে settle করা হুন (Hun) দের বংশধর, যারা কালক্রমে এরা হিন্দু ধর্ম (law of the land) গ্রহণ করে।
আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হল, মুঘল রাজপুত সম্পর্ক এর ভিত্তি কী?
১. বাল্যকালে রাজস্থানের রাজপুত পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার ফলে, মুঘল সম্রাট আকবর একটা জিনিস বোঝেন - রাজপুতরা মূর্তিপূজক হলেও আদতে এদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ কোনো প্রীতি নেই। এদের উদ্দেশ্য - নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম ভারতে অক্ষুন্ন রাখা, এবং সর্বোপরি Hun Brotherhood। হিন্দু থাকা আর না থাকাটা সেই প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করছে।
২. আকবর ও মুঘলরা বোঝে, ভারতে সাধারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করা কঠিন। তাই, ইসলামের তরবারি হাতে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লে, সম্পূর্ণ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবেনা। বরং, সহজ উপায় হল - যদি একটা হিন্দু কাস্টকেই নিজেদের Alliance হিসেবে গ্রহণ করা যায়, যারা নামে হিন্দু হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি অন্তরে এদের কোন শ্রদ্ধাভক্তি থাকবেনা;
এই এরা যদি সাধারণ হিন্দুদের গণহত্যা করে, তাহলে তাতে সাধারণ হিন্দুদের এটা মনে হবেনা যে, বিধর্মীরা তাদের ওপর অত্যাচার করছে। তাদের কাছে এটা হবে কোন প্রাত্যহিক রাজনৈতিক ঘটনা।
এবং, Most Importantly, যদি Mainland India তে কেউ লোকবল বৃদ্ধি করে, তাকে Rajputisation এর মাধ্যমে এই মূল রাজপুতরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে। মূল রাজপুতরা যেহেতু মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে Alliance এ থাকছে, তাই এই Rajputisation এর product গুলোও by default মুঘল সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকবে, এবং মুঘল সেনার অফুরন্ত Manpower supply অব্যাহত থাকবে।
অর্থাৎ, মুঘল সাম্রাজ্য নিজেদের প্রসারের জন্য ধর্মান্তরকরণ বা, Conversion of Religion এর বদলে Conversion of Caste করার সিদ্ধান্ত নেয়।
৩. Hun দের আসল উদ্দেশ্য ছিল Inner India বা, গাঙ্গেয় অববাহিকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কারণ, সহস্র বছর ধরে এটিই ছিল সবথেকে prosperous region, যে উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে পারেনি গুপ্ত সম্রাটদের হাতে পরাজিত হওয়ায়। মূল রাজপুত দের হৃদয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই শেষ না করা কাজের সমাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা জ্বলমান ছিল।
৪. আর্থিক দৃষ্টিকোণ - মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করার প্রধান কারণ ছিল, মুঘলরা খুব সফলভাবে অবিভক্ত ভারতের পুরো উত্তর পশ্চিমকে (পাঠান, রাজপুত) এক ছাতার তলায় আনে। লক্ষ্য করুন, রাজস্থান বা, আফগানিস্তান এর অর্থনীতি সম্পূর্ণ Based On Trade Roots, তাই এই অঞ্চলের Ruling Class (হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে) এর জন্য বাকি ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল Question of Survival,
তাই মুঘল সাম্রাজ্যকে বলা যায়, Peak of North West Imperialism
মুঘল সাম্রাজ্যবাদ যে গাঙ্গেয় অববাহিকাকে কতটা হিংস্রভাবে লুঠ করেছে, সেটার প্রমাণ এই থেকেই পাওয়া যায় যে, রাজস্থানের প্রতিটি দুর্গ ও প্রাসাদের বয়স ৩০০ - ৪০০ বছর, অর্থাৎ প্রতিটি ই মুঘল আমলে নির্মিত। বা, বলা যায়, রাজস্থানের প্রতিটি স্থাপত্য এর খরচা আদতে পূর্ব ভারতকে করা শোষণ থেকে প্রাপ্ত।
Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman
Historical Hindu 09-December-2024 by east is risingZahid Mollah
এর কারণ হচ্ছে বিগত ১৫ বছর শেখ হাসিনার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মডার্নাইজেশনকে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ৫ই আগস্টের পর নতুন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী দ্রুত বেগে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। হাসিনা ক্ষমতাচুত্য হওয়ার আগেও ও পরে কিছু বিভিন্ন ডিফেন্স পেজ এর সৌর্স সমেত এবং আনুমানিক কানাঘুষার মাধ্যমে মাধ্যমে অর্জিত শপিং লিস্ট দেখা যাক:
Bangladesh Army:
*** Recieved First regiment VT-5 and Rumered to have ordered a second regiment of VT-5 light tank and unknown number of (ARV).
*** Speculative collaboration with Turkiye for MLRS or SRBM.
*** Speculation of Chinese company Vanguard to help build large missile plant in Bangladesh.
*** Bangladesh recieved Huge shipment of Arms and Ammunition from Pakistan shortly after the resignation of Delhi's puppet Hasina.
*** Induction of TRG-230 with 70km range and TRG-300 Kaplan MLRS with a range of 120km, which boosted medium range offensive capabilities.
*** Induction of Independent Army Air Defense Core.
*** Induction of 12 Bayraktar TB-2 and also Army has initiated indegenous UAV program.
*** Induction of Boran 105mm Ultra Light Howitzer from Turkiye.
Air Force:
*** Speculation of 3 squadron of J-10C from China and 12 Rafale Fighter Jet from France. (This might be true even the Air Force chief said they're focusing on MRCA on urgent basis)
*** Operationalized Lalmonirhat Air Base which is within 12km of Chicken Neck
***According to Air Chief, Air Force opting to purchase MRSAM
*** Bangladesh set to sign defence purchase deal with Japan, includes Transfer of Technology (TOT)
*** Bangladesh officially operationalized two high-performance long range radar systems, namely Ground Master 400 (GM400), which have an instrument range exceeding 500km, along with Leonardo RAT-31DL long range air surveillance radar. (which India has objected before because the radar covers huge Indian Airspace)
এইসব মডার্নাইজেশন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ আর্মি এবং এয়ার ফোর্সের Qualitative Capability অনেকাংশে বাড়িয়ে দিবে, যেটা ভারতকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারে।
বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা যদি সত্যিই দুর্বল হতো হাসিনার পতনের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও বর্ডারে অন্তত একটা ক্লাশ করিয়ে চাপ সৃষ্টি করতো। এতোটুকু অসৎসাহস ভারতের আছে।।
কিন্তু সেটাও পারে নাই কারণ সামরিক বাহিনী আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী
ভারত বাংলাদেশের লং রেঞ্জ অফেন্সিভ ক্যাপাবিলিটিকে ভয় পায়। এদের রিটায়ার্ড (রিটার্ড) জেনারেলদের হাস্যকর পডকাস্ট গুলা দেখলেই বোঝা যায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ভারতের জন্য কতটা অস্বস্তিকর।
আর ড. ইউনুসের আমলেই যদি অফেন্সিভ ডিটারেন্স অর্জন করে ফেলে তাহলে ভারতের কফিনে পেরেক মারার মতো হবে। ভারত সম্ভবত তার ইন্টেলিজেন্স সোর্সের মাধ্যমে জানতে পেরেছে ড. ইউনূসের সরকার কিছু দেশের সাথে হয়তো স্ট্র্যাটেজিক চুক্তি করতে পারে।
সেনাপ্রধান গতকাল তার বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে আধুনিকায়নের কথা ব্যক্ত করেছে। আশা করা যায় বাংলাদেশের সামরিক শক্তি একটা বুস্ট নিবে।
INDIA is passing through GD Bakhsi Phenomena
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Technology news Hindu 06-December-2024 by east is risingমুখে যতোই গ্রেটার ইন্ডিয়ার কথা বলুক, ভারতের ডিপ স্টেট জানে যে গ্রেটার ইন্ডিয়ার স্বপ্ন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। গ্রেটার ইন্ডিয়া বলতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে যা ইন্ডিয়া পাকিস্তান নামে দুই দেশে ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে। জিন্নাহ বারবার ফেডেরাল ইন্ডিয়া চাওয়া সত্ত্বেও গান্ধী নেহরু প্যাটেল (গুজারাতি হিন্দি) নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কেন্দ্রীভূত ভারত-এর পক্ষে ছিল। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের লক্ষ্য ছিল হিন্দিভাষি হিন্দু অঞ্চলের ভোট যেন ভারত-এ শেষ কথা হয়, তাই হিন্দি ভোট কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করবে আর কেন্দ্রের কথা রাজ্য মেনে চলবে, আর এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার-এর সাহায্যে সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে নেবে গুজারাতি রাজস্থানীরা আর কেন্দ্রীয় চাকরী নেবে ইউপি বিহারীরা। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের এই অভিসন্ধি বুঝেই জিন্নাহ বলেন হয় ফেডেরাল ভারত নয় আলাদা দেশ পাকিস্তান। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের উদ্যেশ্য ছিল যেভাবেই হোক যতটা পারা যায় ব্রিটিশ ভারতের অংশ কেন্দ্রীভূত শাসনে রেখে দেওয়া আর এই লক্ষ্যে বোকা মুসলমানদের সাহায্য পেতে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি আউরাতে থাকা। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার পরেও নেহরু প্যাটেল-দের ধারণা ছিল পাকিস্তানের জমি ও প্রাচুর্য কম বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে ভেঙ্গে পড়বে আর পুণরায় ভারতের সাথে যুক্ত হোতে বাধ্য হবে। যখান তা হোল না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার ছক কষতে থাকে। ১৯৭১-এ সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গে ভারত সোভিয়েত-এর সাহায্য নিয়ে। অপেক্ষাকৃত ছোট দুর্বল রাষ্ট্র বাংলাদেশ-কে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ভারত এমন ধারণা ছিল। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আফঘানিস্তানে যুদ্ধ শুরু মূলত পাকিস্তান থেকে পুশ্তুন সংখ্যাধিক্য সম্পন্ন উত্তর পশ্চীম, বালুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ ভাঙতে। এর উদ্যেশ্য ছিল এক দিকে সোভিয়েত পাবে সিন্ধের ওয়ার্ম ওয়াটার বন্দর আর ভারত দুর্বল ছোট পাকিস্তান ভাঙ্গা রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভাঙ্গা কল্পিত রাষ্ট্র গুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র নামে দুটো শব্দ ভারতীয় সংবিধানে পর্যন্ত ঢোকানো হয় ১৯৭৬ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর প্রভাবেই তা হয়। কিন্তু সোভিয়েত ১৯৮৯ সালে আফঘানিস্তান থেকে বিতারিত হয় এবং ১৯৯১ সালে ভেঙ্গে যায়। এর ফলে হিন্দি গুজারাতি শাসক শ্রেণির একটা অংশ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র-কে ছুঁড়ে ফেলে হিন্দুত্ববাদ ও ধনতন্ত্র-কে আঁকড়ে ধরে। এভাবেই ক্ষমতায় আসে বিজেপি এবং আরও পরে মোদি। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ইসলামি সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-কে কাগে লাগিয়ে হিন্দুত্ববাদ-কে শুধু ভারতেই নয়, মার্কিন মুলুকেও শক্তিশালী করে তোলে। হিন্দুত্ববাদ যায়নবাদ ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ-এর জোট আজ মার্কিন শাসক শ্রেণির একটা অংশের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। ট্রাম্প ২০২৫ সালে এই জোট-কে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চলেছে তার মন্ত্রী সভায়। মার্কিন ভারত জুটি স্বপ্ন দেখতে থাকে আফঘানিস্তান-এ ঘাঁটি গড়ে পাকিস্তান-কে ভাঙ্গার আর চীন থেকে শিনসিয়াং প্রদেশকে আলাদা করার কিন্তু ২০২১ সালে ২০ বছর যুদ্ধ করার পরে মার্কিন সেনা পরাজিত হয়ে আফঘানিস্তান ছেড়ে পালায় এবং আফঘানিস্তানে ক্ষমতায় আসে পাকিস্তান ও চীন-এর বন্ধু তালিবান সরকার। এদিকে চীন-এর উত্থান মার্কিন কেন্দ্রিক এক মেরু বিশ্ব ব্যবস্থাও ভেঙ্গে ফেলে। আফঘানিস্তানে পাকিস্তানের সাহায্যে তালিবানের জয়, চীনের অর্থনৈতিক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের বুঝিয়ে দেয় তারা দঃ এশিয়াতে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। শেষে ২০২৪ সালের ৫ই অগাস্ট বাংলাদেশে ছাত্র জনতার বিপ্লব হিন্দি গুজারাতিদের বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বপ্নের শলীল সমাধি ঘটায়। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান ছিল ২৪%। তাই তখন গোটা ব্রিটিশ ভারত পেলে অনায়াসেই গুজারাতি হিন্দি-রা নিয়ন্ত্রণ করত গোটা ব্রিটিশ ভারত। কিন্তু আজ ২০২৪-এ ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩.৫% হয়ে গেছে মুসলমান আর প্রবণতা বলছে ২০৫০-এ তা হবে ৩৮%।
অর্থাৎ গ্রেটার ভারত তৈরি হলে সেখানে মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে আর তখন হিন্দিভাষি হিন্দুদের ভোটের জোড়ে হিন্দি গুজারাতিরা ব্যবসা ও কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা। এমনকি বাংলাদেশ দখল করে ১৬ কোটি মুসলমান ও ১৮ কোটি বাংলা ভাষি ভারতে ঢুকিয়ে হিন্দিভাষি হিন্দুদের ভোটের গুরুত্ব কমাতে পারবেনা হিন্দি গুজারাতি শাসক শ্রেণি। বাংলাদেশ-এর ৫ই অগাস্ট, ২০২৪ বিপ্লব বুঝিয়ে দিল ছোট রাষ্ট্র বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব না। তাই পাকিস্তান বা বাংলাদেশ দখলের স্বপ্ন বা পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ভারতের ডিপ স্টেট আর দেখেনা। যেহেতু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দখল করে আর লাভ নেই, তাই ভারতের হিন্দি গুজারাতি ডিপ স্টেট মনে করছে গান্ধী নেহরুর ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশের আর দরকার নেই। মোদি যোগী তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের মুখ। ভবিষ্যতে ভারতে বসবাসকারী মুসলমান-দের বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংগঠিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত এখনো গরীব দেশ। সেখানে জমি ভেরি নারী দখলের লড়াই আজও প্রাসঙ্গিক। আদি পুঁজি যোগাড় করতে সংখ্যাগুরু জাতি সংখ্যালঘু জাতির বিরুদ্ধে জেনোসাইড করেছে আধুনিকতার সূচনা লগ্ন থেকেই।
তাই হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক-এ অতি ক্ষুদ্র মুসলমান জনসংখ্যার বিরুদ্ধে জেনোসাইড হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। হায়দ্রাবাদ, কেরালা, পঃ বঙ্গ ও আসাম- যেখানে একটা ভাল সংখ্যা রয়েছে মুসলমানদের সেখানেও আঘাত হানার পরিকল্পনা করবে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। এই অঞ্চলগুলোই দাঙ্গার পক্ষে আদর্শ কারণ এই সব অঞ্চলে মুসলমানরা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। পৃথিবীর নিয়ম হল "হয় বৃদ্ধি, নয় হ্রাস", স্থবিরত্বের কোনও জায়গা নেই হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যের (যার পোষাকি নাম ভারত) বৃদ্ধির জায়গা আর নেই। অতএব এই সাম্রাজ্যকে শীঘ্রই সঙ্কুচিত হতে হবে।
হোতেই পারে হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক-এ জেনোসাইড-এর মুখে পড়ে বহু মুসলমান বিদেশে বা কাশ্মীর উপত্যকায় বা কেলায় বা হায়দ্রাবাদে বা পঃ বঙ্গে বা আসামে পালিয়ে যাবে। ফলে ভালো সংখ্যা আছে এমন জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার কম সংখ্যায় মুসলমান আছে এমন অঞ্চল মুসলমান শূন্য হয়ে যেতে পারে। আবার পঃ বঙ্গ ও আসামের মসুলমানদের বাংলাদেশে পুশ করার চেষ্টা করা হোতে পারে (যেমন মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুশ করেছে বাংলাদেশে)। পাকিস্তান শক্তিশালী বলে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষকে পুশ করতে পারবেনা। বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থান নিলে পঃ বঙ্গ ও আসামের মুসলমানদেরকেও পুশ করতে ব্যর্থ হবে। সব মিলিয়ে বলা যায় দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ ও কেরালা এবং পূর্বে পঃ বঙ্গ ও আসাম আর উত্তরে কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলে শীঘ্রই বিপুল সংখ্যক মুসলমান-এর জেনোসাইডের মুখে পড়ে আভিবাসী হিসেবে চলে আসার সম্ভাবনা আছে হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত ও মহারাষ্ট্র থেকে। জেনোসাইড দাঙ্গা ও জমি ভেরি নারী দখলের আদি পুঁজি সঞ্চয়-এর আরেকটা রাউণ্ড দেখতে চলেছে ভারত।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Theoretical Hindu 05-December-2024 by east is rising১) সাধারণ মানুষ-এর প্রবণতা দুর্বল-এর পাশে না থাকা আর ক্ষমতাবানের পা চাটাঃ বাঙালি মুস্লমান-এর চেয়ে যেহেতু হিন্দি গুজারাতিরা বেশি শক্তিশালী আর তাই সাধারণ বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুস্লমানদের থেকে বেশি পছন্দ করে হিন্দি গুজারাতিদের।
২) বাঙালি হিন্দুরা বাংলা সালতানাত আমলে (১৩৫৩-১৫৭৫) বাঙালি মুসলমান বলতে উচ্চ কিছু (সুলতান সম্ভ্রান্ত) বুঝত, কিন্তু মোঘল আমল (১৬১১-১৭১৭)-এ বাঙালি হিন্দুদের চোখে উরদু মুসলমান বলতে উচ্চ কিছু (মোঘল গভর্নর সম্ভ্রান্ত) আর বাঙালি মুসলমান বলতে নীচু কিছু (চাষা) বুঝতে থাকে আর ব্রিটিশ আমল-এ (১৭৫৭-১৯৪৭) নিজেদের উচু (জমিদার আধুনিক) ও বাঙালি মুস্লমানদের নীচু (চাষা ধর্মময়) ভাবতে থাকে। নীচু বাঙালি মুস্লমান-দের এক ভাবতে বা নিজেদের থেকে উঁচু ভাবতে তাই কষ্ট হয় বাঙালি হিন্দুদের।
৩) মহাভারত রামায়ণ মূলত হিন্দি গুজারাত কেন্দ্রিক মানে মথুরা দ্বারকা কুরুক্ষত্র অযোধ্যা সবই হিন্দি ও গুজারাত অঞ্চলে। ফলে বাঙালি হিন্দুদের এক ধরণের আদর্শগত আনুগত্য আছে হিন্দি গুজারাত-এর প্রতি। (যদিও ঐতিহ্যগত ভাবে বাঙালি হিন্দুদের কালিকা পূরাণ বা মোঙ্গল কাব্য-এর মতো নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থ আছে, কিন্তু পুরুষালি রামায়ণ মহাভারত-এর কাছে রমণি কেন্দ্রিক কালিকা পূরাণ ও মোঘল কাব্য ক্রমেই হেরে গেছে।)
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Social Hindu 04-December-2024 by east is risingহিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যবাদ বাংলার (বাংলাদেশ পঃবঙ্গ ত্রিপুরা) ওপর আঘাত বাড়াচ্ছেঃ বাংলাদেশের মেধার অধিকারের আন্দোলন, সুকান্ত মজুমদার-এর পঃ বঙ্গ থেকে উত্তর-এর অংশকে আলাদা করার ডাক, নিশিকান্ত দুবের মালদা ও মুশিরদাবাদ জে্লাকে কেন্দ্রীয় শাসিত করতে বলা, সবই আসলে এক সূত্রে গাঁথা।
হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যবাদ জানে বাঙালি জাতি জনসংখ্যার দিক থেকে ৩০-৩৫ কোটি। বাংলার আছে বিশাল সমুদ্র তট যেখান থেকে বাঙালি অনায়াসে বিদেশের সাথে বাণিজ্য চালাতে পারবে এবং বিদেশি মুদ্রা আয় করতে পারবে এবং সেই মুদ্রার বলে স্বাধীন রিসার্ভ ব্যঙ্ক বানাতে পারবে যা স্বাধীন রাষ্ট্রের আধুনিক যুগে সবচেয়ে বড় বুনিয়াদ।
বাঙালি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে গেলে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হবে আর তা হলে গোটা গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই যেভাবে হোক বাঙালিকে শেষ কর। শেষ করতে এক দিকে বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকারকে নিয়ন্ত্রণ কর। আর অন্যদিকে পঃ বঙ্গ-এর রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ কর। যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তো নানাভাবে সরকারকে বেকায়দায় ফেল। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আপাতত নিয়ন্ত্রণে আছে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু পঃ বঙ্গের রাজ্য সরকার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই পঃ বঙ্গের যে অংশটায় বিজেপি জিতেছে অর্থাৎ উত্তরের অংশকসক আলাদা করার দাবি জানাচ্ছে।
এবার প্রশ্ন পঃ বঙ্গ-এর রাজ্য সরকার কিভাবে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে কাজ করছে?
এক, পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনারজি তিস্তার জলের ভাগ বাংলাদেশকে দিতে রাজি নয় আর এর কারণ হল তিস্তার জলের বেশি ভাগ বাংলাদেশকে দিলে পঃ বঙ্গের উত্তর বঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেখানকার চাষাবাদে ভয়ঙ্কর পরিণাম নেমে আসবে। গুয়াজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় তিস্তার জল বাংলাদেশকে দিয়ে একদিকে তার পোষা বাংলাদেশ-এর সরকারকে স্থায়িত্ব দিতে আর অন্য দিকে পঃ বঙ্গের উত্তর বঙ্গে ভয়ানক ক্ষরা তৈরি করে সব দোষ পঃ বঙ্গ সরকারের ওপর চাপিয়ে উত্তর বঙ্গকে পঃ বঙ্গ রাজ্য থেকে আলাদা করা। উত্তর বঙ্গ আলাদা রাজ্য হলেই সেখানকার প্রশাসনে বিজেপি গেঁড়ে বসবে এবং আস্তে আস্তে বাংলা ভাষা তুলে দিয়ে হিন্দি চালু করবে। এই পথেই পূর্ব বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে বাংলাকে মুছে দিয়েছে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। মমতা তিস্তার জল না দিয়ে একদিকে বর্তমান বাংলাদেশের সরকারকে বিপাকে ফেলছে আর অন্যদিকে উত্তর বঙ্গকে আলাদা হতে আর শুঁকিয়ে মারতে বাঁধা দিচ্ছে।
দুই, পঃ বঙ্গ সরকার-এর প্রধান মমতা ব্যনারজি মুসলমান ভোটের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বাচনের পর নির্বাচন জিতছেন আর এর কারন পঃ বঙ্গে এখন ২০২৪ সালে মুসলমানের সংখ্যা ২০১১-এর আদম সুমার সুমারির প্রজেকশন ধরলে দাঁড়ায় ৩০%। এই সংখ্যা আগামী দশ বছরে ৩৮% হতে পারে। বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যা অন্য দিকে বর্তমানের ৫৫% থেকে কমে ৪০%-তে নেমে আসতে পারে। হিন্দিভাষী হিন্দুদের সংখ্যা ১১% থেকে ১৭% হবে। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল পঃ বঙ্গে বাঙালি ও উর্দু মুসলমানেরা ভূমি পুত্র আর হিন্দি হিন্দুদের অধিকাংশই অন্য রাজ্য (মূলত রাজস্থান বিহার ইউপি থেকে আগত)। ভুমি পুত্রদের জন্মহার কমবে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে আর অন্য রাজ্য থেকে আগমনও বৃদ্ধি পাবে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে। অর্থাৎ পঃ বঙ্গে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে তবে মুসলমানদের জন্ম হার আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত কমবে আর অন্যদিকে হিন্দিদের আগমনের হার ও তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়বে। তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় পঃ বঙ্গে শিল্পায়ন নগরায়ন দ্রুত হোক। কিন্তু শিল্পপতিদের হাত থেকে চাষিদের জমি বাঁচানোর আন্দলনের বলে ক্ষমতায় আসা মমতা ব্যনারজি শিল্পায়নের পথে যাচ্ছেনইনা। ফলে হিন্দিদের আগমনের গতি মন্থর হচ্ছে আর মুসলমানদের জন্মহার যতটা দ্রুত কমার কথা ২০১১ আদম সুমারির প্রজেকশন অনুযায়ী তার থেকে জন্মহার কমছে অনেক কম গতিতে।
বিজেপি হল গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের উগ্র রূপ আর কংগ্রেস হল তার নম্র রূপের মুখোশ। কংগ্রেস পঃ বঙ্গে শেষ আর বিজেপি গোটা পঃ বঙ্গে জয়ী হতে পারবেনা। লারি পূজারি বাঙালি হিন্দু ক্রমেই জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে আর বাঙালি হিন্দুর ক্ষয়ের সুযোগ বেশি তুলছে মুসলমানেরা। কিন্তু গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় বাঙালি হিন্দুদের ক্ষয়ের মূল লাভ তুলুক হিন্দিরা। মমতার শিল্প করায় অনাগ্রহ ও দান-এর রাজনীতি পঃ বঙ্গে মুসলমানেদের অবস্থান হিন্দিদের তুলনায় শক্ত রাখছে। যদিও মমতার লারি কেন্দ্র করে নানা দান মুসলমান লারিকে ধর্ম বিমুখ করছে আর এর ফলে পঃ বঙ্গের মুসলমানেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে কিন্তু হিন্দিদের থেকে তারা তুলনামূলক ভাবে সুবিধেজনক বস্থায় থাকছে। বিজেপি বুঝতে পারছে আগামী ১০ বছরে বাঙালি হিন্দু বুমার জেনারেশনটা (১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে যাদের জন্ম) শেষ হয়ে যাবে আর তা বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যার শেয়ার অনেক কমিয়ে দেবেই। মুসলমানেদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দিদের চেয়ে পঃ বঙ্গে বেশি থাকলে (শিল্পায়ন গতি মন্থর বলে), ২০১১ সালের প্রজেকশন ধরে যত ভাবা হচ্ছে তার চেয়েও বেশি হবে মুসলমানেদের সংখ্যার শেয়ার। আমার গণিত বলছে আগামী ১০ বছর পরে পঃ বঙ্গে মুসলমানেদের সংখ্যা ৩৮% নয়, হবে ৪১% আর হিন্দিদের হবে ১৫%।
মজার ব্যপার অসমের লারি পূজারি হিন্দুরাও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু আর আসামের শিল্প সম্ভাবনা ও নগরায়ন সম্ভাবনা ভৌগোলীক কারণে অনেক কম। ফলে সেখানে মুসলমানেদের সংখ্যা ৫০%-এর কাছে পৌঁছে যাবে আগামী ১০ বোছোড় পরেই। আসামের মুখ্যমন্ত্রী একে জীবন মরণ সমস্যা বলেছেন।
গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ জানে যে বাঙালি হিন্দুর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা। স্বল্প জন্মহারর ফলে বাঙালি (ও আসামিয়া) হিন্দুদের জনসংখ্যার শেয়ার পড়তেই থাকবে এবং বয়স্কদের সংখ্যা যুবাদের সংখ্যার চেয়ে কম হবে। যার অস্তিত্বই থাকবেনা তার হিন্দুত্ব বা বাঙ্গালিত্ব কোনটাই বহন করার ক্ষমতা থাকবেনা। এর সঙ্গে যোগ করা যায় যে বাঙালি হিন্দুদের একটা বড় অংশ হিন্দি গুজারাতিদের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলেছে। নতি স্বীকারের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছে কারণ এখন বাঙালি হিন্দু মেয়েরা হিন্দি গুজারাতি স্বামী পেলে বরতে যায় আর বাঙালি পরিবারগুলোও তাতে শ্লাঘা অনুভব করে। তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ জানে যে বাঙালি হিন্দুরা বাঙ্গালিত্বের জন্য লড়াই করতে পারবেনা। কিন্তু লারি পূজারি বাঙালি হিন্দু হিন্দিদের দালাল হিসেবে পঃ বঙ্গ থেকে মুসলমান হটাতে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে? পরের পর্বে আমরা এর উত্তর খুঁজব।
Read More
Author: Saikat Bhattacharya
Theoretical Hindu 26-July-2024 by east is risingশেষ লারী পূজারী জাতি কিভাবে ধ্বংস হবে?
কেন কিছু বাঙ্গু হেদু হয় হিন্দি ভাষা নিয়ে হিন্দি হেদু হয়ে যাবে নয়তো ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাঙালি মুসলমান হয়ে যাবে ?
পশ্চীম বাংলায় বাঙ্গু হেদু ৫৫%, হিন্দি হেদু ১২%, অন্যান্য হেদু যেমন নেপালী ২%।
বাঙ্গু হেদু লারী পূজারী আর তাই জন্মহার অত্যন্ত কম প্রায় ৪০ বছর ধরে।
তাই বলা যায় ৫৫%-এর অন্তত ২৭% আগামী ২০ বছর পরে ৬০ বছরের বেশি হবে।
২৮% অল্প বয়সীদের মধ্যে ৮% ১৫ বছরের নীচে হবে।
১৬-৫৯ বছরের মধ্যে থাকবে ২০%।
এদের ১০% হবে লারী আর ১০% হবে পুরুষ।
১০% লারীদের একটা বড় অংশ (৫%) অন্য জাতির পুরুষের সাথে ভেগে যেতে চাইবে।
আর একটা অংশ বিয়ে না করে বা বিয়ে করে বাচ্চা না দিয়ে কুকুর বিড়াল পুষবে (৩%)।
মাত্র ২% বাঙ্গুই হেদু লারী ঠিকঠাক সংসার করবে।
১০% পুরুষের একটা বড় অংশ (৫%) বিয়ে করার ঝামেলায় যাবে না বা বিয়ে করে ডিভোর্স করতে বাধ্য হবে।
৩% পুরুষ বিদেশে পালাবে আর ২% বাঙ্গু হেদু পুরুষ ঠিকঠাক সংসার করবে।
এই ২% বাঙ্গু হেদু স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সন্তানদের আর বাঙ্গু হেদু রাখতে পারবেনা।
শেষে কিছু বাঙ্গু হেদু হয় হিন্দি ভাষা নিয়ে হিন্দি হেদু হয়ে যাবে নয়তো ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাঙালি মুসলমান হয়ে যাবে।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Social Hindu 28-June-2024 by east is risingAshoka killed 18000 Ajivikas of Pundrahvardhana and eradicated the entire Ajivika faith. He also enforced vegetarianism and perscuted whoever did not follow that dictat. This destroyed livelihoods of many classes whose profession was tied to hunting, fisheries and animal byproducts. But he is considered 'The Great'. This is is what called propaganda. Here actions do not matter but affiliation is everything. This is the main peril of monotheistic religions.
Sharamanic faiths emerged in eastern gangetic plains as a reaction to Vedic Religion. Their main objection was Animal sacrifice in rituals and meat-eating, ban on moneylending and interests, restriction of the power of propertied classes and private property in general. It is the Shramanic religions that banned cowslaughter as Cow was an important animal in both agriculture and trade. Yet this crucial history is supressed to hide the true knowledge about how everything came into existence.
When Vedic religion died, their old followers also took on these Shramanic ethos.
Buddhism is one of the pioneer of state-sponsored theocracy, religious persecution and violence. It was from Kushans Buddhism started to become more evolved and humane.
Is it surprising that the narratives of monotheist reactionaries and indian state always converges or there is some deeper links?
Read MoreAuthor: Purandhar Khilji
Historical Hindu 16-June-2024 by east is risingKodavas are military caste of Kodagu district of Karnataka.
Kodagu is mountainous country and even today is a well forested.
Kodavas used this mountainous and forested landscape to their advantage - invading armies were lured deep into Kodagu, then relentlessly harassed by guerrilla warfare and then finished off by large scale surprise attacks.
Problems between Kodagu and Muslim rulers of Mysore began as early as 1765.
Hyder Ali of Mysore sent a large force under Fazalulla Khan to conquer Kodagu. Kodavas under Chikka Virappa defeated the force in four major battles and forced them into retreat.
Unfortunately in 1773, a succession dispute in Kodagu was taken advantage by Hyder Ali - Lingaraja, one of the contestants asked for Hyder Ali’s help and he invaded Kodagu with a Mysore army.
This force was thoroughly defeated at Battle of Yedavanad. But Lingaraja being a Kodava himself, persuaded many Kodavas to support his cause and this managed to win over the whole Kodagu without any fight!
Deposed king named Devapparaja and his entire family was murdered by Hyder Ali.
But soon nemesis struck - in 1780, Lingaraja died.
His sons Vira Rajendra and Lingaraja were minors - taking advantage of this situation, Hyder Ali took over the administration of Kodagu directly.
His pretext was that he will rule until princes became adults - though it was clear to all that his aim was annex Kodagu. Both princes were kept in captivity for 8 years (until 1788).
In 1782, a massive revolt broke out in Kodagu as people were angry with Hyder Ali deposing their king.
Kodavas drove out all Mysore forces from their land and became independent (Hyder had died in the meantime).
Now Tipu is the ruler of Mysore - he invades Kodagu in 1784 but was driven out by Kodavas in 1785.
Tipu then sent another army of 15,000 men but were defeated by 4,000 Kodavas at Battle of Ulagulli. Entire Mysore army had flee for their life and their whole baggage was looted by Kodavas.
Then as usual, Tipu used treachery - he promised to make peace with Kodavas and invited them for a peace talk at Talakkaveri.
But Kodava delegation was arrested and their 85,000 followers and their family members were forcibly converted to Islam.
Not content with this, Tipu then ordered his army to kill every single Kodava man they could lay hand on and enslave their women and children.
Terrible atrocities were committed - mass rape, enslavement of women, forcible conversions, destruction of temples, slaughter of cows, wholesale burning of villages, fields and orchards etc.
Kodavas refused to buckle and wage valiant guerrilla warfare from hills and forests.
In 1788, imprisoned VIRA RAJENDRA along with his family escaped from jail (due to help by Pazhassi Raja by some accounts).
Kodavas who were leaderless until then, rallied around this charismatic and energetic 24 year old prince.
He and his men launched a massive campaign that drove out Muslim forces from Mysore and even invaded and sacked Mysore proper itself.
Infuriated Tipu sent a large army under Ghulam Ali to deal with Kodavas - bitter fighting followed. Kodavas fought for every inch of land and Mysore army suffered heavy losses.
Luck also came to help Kodavas as Ghulam Ali and his army was re-directed to Malabar in 1789 to deal with massive revolt by Nayars there.
But Vira Rajendra was determined not to let Mysore army retreat in peace - He and his men launched a massive attack on retreating army of Ghulam Ali and slaughtered a large part of enemy force in Battle of Kodantur.
Another Mysore force sent against him was totally defeated at Battle of Heggala and their entire baggage was looted.
This was followed by Kodavas defeating another Mysore army in Battle of Kushalnagara and seized the Mysore fortress there.
He followed up this victory by defeating Mysore garrison stationed at Beppunad and then seizing several forts and outposts of Mysore army across Kodagu.
In 1790, Tipu sent another large force under Buranuddin into Kodagu - this force too was defeated by Vira Rajendra at Second Battle of Kushalnagara.
His next major victory was occupation of Amara Sulya.
Tipu for the last time, sent a large force under Kader Khan to defeat Vira Rajendra - but Khan was also defeated at Battle of Mullusoge and most important Mysore fort in Kodagu - Mercara was captured.
Rajendra and his troops then invaded Mysore proper once more and pillaged it thoroughly to retaliate the destruction done by Tipu’s troops in Kodagu.
With this, Kodagu was permanently free of Tipu’s threat.
Post Script:
Revengeful Tipu - unable to defeat Rajendra in battle - sent assassins to kill him. But they were caught and executed.
When Tipu faced British threat in Third Anglo-Mysore War, he tried to reconcile with Rajendra and asked his help.
Rajendra told him that he will not help him as he could never forget nor forgive the genocidal cruelty done to his people.
Reference:
Coorg Manual - G. Richter (1870)
Written in Quora by Sagar Meloth
Author: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 27-May-2024 by east is risingরাজস্থানীরা মোঘলদের পায়ে থাকতে রাজি হয়।
কেন?
রাজস্থান সমুদ্রতটহীন ও কৃষিহীন মরুভূমি। তাই রাজস্থানের বাইরের অঞ্চল দখল করে সেখানকার কৃষি ও বৈদেশিক ব্যবসা থেকে খাজনা তোলার লক্ষ্য তাদের তাকবেই। তাদের সাধ্যে কুলোয়নি কখণো গোটা দক্ষিণ এশিয়া দখল নেওয়ার। তারা উত্তর প্রদেশ অব্ধি এগিয়েছে কিন্তু বারবার দক্ষীনে মারাঠি ও পূর্বে বাঙালি ও পশ্চীমে আরব (সিন্ধু) পাঞ্জাবী কাশ্মিরীদের সাথে পেরে ওঠেনি। যেমন প্রতিহারেরা পাল ও রাষত্রকূট ও আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে কখনো জয়ী পারেনি।
কিন্তু উজবেক মোঘলরা বাংলা থেকে ডেক্কান সমস্ত সালতানাতকেই পরাজিত করার ক্ষমতা ধরত। তাই রাজস্থানীরা বুঝল মোঘলদের সঙ্গ দিলে উতর প্রদেশ বাংলা ডেক্কান সমস্ত এলাকার খাজনার বখরার ভাগ পাওয়া যাবে। রাজস্থানীরা যা একা পারতনা মোঘলদের সঙ্গী হলে তা পারা যাবে।
তাই রাজস্থানীরা সঙ্গ দেয় মোঘলদের। নিজের ঘরের মা বোন স্ত্রীদের মোঘলদের হারেমে দিয়ে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে মোঘলদের বিশ্বাস অর্জন করে মোঘলদের লিটের বখরা পেয়েছে।
(বঙ্কিম চন্দ্র "দুর্গেশ নন্দিনী" উপন্যাসে আবার মোঘল রাজপুত লটকে বৈধতা দিয়ে গেছেন আর বাঙালি রাজকুমারীকে রাজস্থানি রাজকুমাওরের কাছে সঁপে দিয়েছেন। গল্পে হোলেও বাঙ্গালির হিন্দি চাটা মনন-এর শুরু ওখানেই।)
বাঙ্গালির কি মোঘলদের থেকে বা রাজস্থানীদের থেকে কিছু পাওয়ার ছিল?
সেই সময় কোনও বাঙালি কি মোঘলদের সঙ্গী হয়নি?
বাঙ্গালির কৃষিজমি আর সমুদ্রতট দুইই আছে। তাই বাঙ্গালির থেকে বাইরে থেকে লোক ছিনিয়ে নিতে আসবে খাজনা সেটাই স্বাভাবিক। মোঘলরা ও তাদের অনুচর রাজস্থানীরা বাংলায় আসে বাংলার সুলতানের থেকে খাজনার ভাগ নিতে। সুলতান ও তার সঙ্গী রাজারা স্বাভাবিকভাবেই মোঘল বিরোধী অবস্থান নেয়। আবার দক্ষিণ বাংলার অনেক রাজাই যেমন পঞ্চানন গাঙ্গুলী (সাবর্ণ রায় চৌধুরী) মোঘলদের সঙ্গী হয়।
মোঘলরা জিতলে সাবর্ণরা কি পেতে পারে?
বড় জোড় সুলতানকে যে খাজনা দিতে হবে তার চেয়ে মোঘলদের কম দিতে হবে? মানে বাংলার সামস্তদের আসলে লাভের জায়গা ছিলনা সেরকম মোঘলদের সমর্থন করে। কারণ তাকে খাজনা দিতেই হবে আর সে লুটের বখরা সেভাবে পাবেনা কারণ তার কাছে সমুদ্র ব্যবসা ও কৃষিজমি আছে। রাজস্থানীদের ভারত লুটের ইচ্ছে বেশি। কারণ রাজস্থানে খাজনা নেই। যার খাজনার উৎস নেই তার মধ্যে বাইরের এলাকা দখল করার বাসনা বেশী। মোঘল আর রাজস্থানিদের লক্ষ্য ছিল এক। যাদের কৃষি আছে বা সমুদ্র কৃষি দুইই আছে তাদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনা নিচ্ছে। রাজস্থানীদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনার ভাগ দিচ্ছে। এটাই তফাত।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 26-May-2024 by east is risingসংকীর্তন পার্টি ঘনিয়ে আসায় কাজী ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। কীর্তন আরও জোরে জোরে হয়ে উঠল। হঠাৎ, তার দরজার বাইরে, এবং হরিনামের শক্তিশালী ধ্বনির উপরে, বজ্রের মতো একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "কোথায় সেই দুষ্টু ভক্ত চাঁদ কাজী যে আমার সংকীর্তন আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল? আমি পবিত্র ধর্মের সমবেত মন্ত্র প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি। ভগবান কৃষ্ণের নাম যেখানে আমার ভক্তরা আনন্দের সাথে আমার সংকীর্তন করে, সেই মৃদঙ্গকে ভাঙার সাহস কি করে? দেরি না করে আমার কাছে বদমাশ করো যে তোমার পথে দাঁড়ায়! প্রভুর কথা সিংহের গর্জনের মত শোনাল। সেই সময়, কিছু শ্রদ্ধেয় ও সাধু আত্মা মহাপ্রভুর পায়ে পড়ল এবং তাঁকে করুণাময় হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা বলেছেন যে বেদ পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বদা স্থির, সুখী এবং ক্রোধমুক্ত বলে বর্ণনা করেছে। এমনকি যখন ব্রহ্মা তার সমস্ত গোয়াল বন্ধু ও বাছুর চুরি করে নিয়েছিলেন, এমনকি ইন্দ্র যখন অত্যধিক বৃষ্টি দিয়ে ব্রজকে আক্রমণ করেছিলেন, তখনও ভগবান সজ্জিত ছিলেন। তারা ভগবানকে অনুরোধ করেছিলেন যে এইভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা ত্যাগ করবেন না এবং বৈদিক আদেশগুলিকে ছোট করবেন না। ভগবান চৈতন্য খুশি হলেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সম্মানিত সদস্যকে চাঁদ কাজীর বাড়িতে পাঠালেন। তারা তাকে এক কোণে পেল, ভয়ে কাঁপছে। শান্ত হওয়ার পর, কাজী মাথা নত করে প্রভুর সামনে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণলীলায় চাঁদ কাজী তাঁর মামা কামস হওয়ায় ভগবান চৈতন্য তাঁকে কাকা বলে সম্বোধন করেছিলেন।
কিছু ভদ্র আনুষ্ঠানিকতা বিনিময়ের পর, ভগবান চৈতন্য তাঁকে বললেন: যাও দুগ্ধা খাও, গাবি তোমারা মাতা। "তুমি গরুর দুধ পান কর, তাই গরু তোমার মা।" (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদি-লীলা, অধ্যায় 17, শ্লোক 153)
যদিও চাঁদ কাজী সম্রাট হুসেন শাহের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন, তবুও তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং কোরান থেকে উদ্ভূত দর্শন ছিল অপর্যাপ্ত এবং ঘাটতি। স্বয়ং মুসলিম কাজী উপসংহারে এসেছিলেন: সহজ যবন-শাস্ত্রে অর্দ্ধ ভিকার । 'মাংস ভক্ষণকারীদের ধর্মগ্রন্থের যুক্তি ও তর্ক খুব সঠিক বিচারের উপর ভিত্তি করে নয়।" (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদি-লীলা, অধ্যায় 17, শ্লোক 171)
চাঁদ কাজী বলেছেন যে মুসলিম গ্রন্থ কোরান অনুসারে গরু হত্যার কোনো উল্লেখ বা কোনো অনুমোদন নেই। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে যারা এই সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদিত বলে তারা পবিত্র কোরানের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তখন থেকেই চাঁদ কাজী ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি মাংস ভক্ষণ ও কোনো প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকেন । বিশৃঙ্খল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ও, চাঁদ কাজীর বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং হিন্দুদের সঙ্গে কখনও কোনো বিরোধ হয়নি।
ভগবান চৈতন্য প্রসঙ্গ পাল্টে কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সেই রাতে আগে তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন বন্ধ করেছিলেন কিন্তু আজ তিনি তা বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। কাজী কবরের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে বললেন, মৃদঙ্গ ভেঙে ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একজন মানুষের দেহ এবং একটি সিংহের মাথার সাথে একটি হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রাণী এবং যার ভয়ঙ্কর দাঁত এবং লম্বা নখ ছিল তিনি যদি আবার সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেন তবে তাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছেন । তার বুকে বসে ভয়ে গর্জন করে, সে তাকে আঁচড় দেয়। কাজী তখন তার বুক খালি করে, এবং ভক্তরা একটি সিংহের অস্পষ্ট পেরেকের চিহ্ন দেখতে পান। তারা তৎক্ষণাৎ নৃসিংহদেবের কথা মনে পড়ল এবং কাজীর কাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করল।
চাঁদ কাজী তখন অশ্রুসজল চোখে ভগবানের পদ্মের চরণে পড়লেন এবং শপথ করলেন যে, সেই দিন থেকে তিনি বা তাঁর বংশের কেউই এখন বা ভবিষ্যতে সংকীর্তন আন্দোলনে কোনো বাধা দেবেন না। . যদি কাজী বলেন, তার কোনো বংশধর যদি তা করে থাকে, তাহলে সেই বংশধরকে পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে বঞ্চিত করা হবে। এই কথা শুনে ভগবান চৈতন্য উচ্চারণ করলেন "হরি! হরি!" উত্থান, তিনি উল্লসিত এবং বিজয়ী সংকীর্তন দলের নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীধাম মায়াপুরে ফিরে আসেন। ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত শ্রীধরের বাড়িতে থামলেন।
চাঁদ কাজী দেহত্যাগ করার পর নবদ্বীপে তাঁর সমাধি স্থাপন করা হয়। তাঁর সমাধির উপরে অবস্থিত এই গাছটি 500 বছরেরও বেশি পুরনো। এই গাছটি আসলে অতীতের এই সব ঘটনার সাক্ষী। ভগবান চৈতন্যের ভক্তরা, নম্রতা অনুভব করে, চাঁদ কাজীর সমাধি প্রদক্ষিণ করেন কারণ তিনি প্রভুর করুণা লাভ করেছিলেন। আপনি যদি গাছের দিকে তাকান তবে আপনি দেখতে পাবেন যে এটি ভিতরে ফাঁপা হলেও এটি সর্বদা সুন্দর ফুল দেয়।
From Aranya Saha
Author: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু পনের শতকের শেষের দিকে, 1486 সালে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতের বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন, যেটি তখন পাঠান মুসলমানদের দ্বারা শাসিত ছিল । সতেরো বছর বয়সে চৈতন্য মহাপ্রভু তার সংকীর্তন আন্দোলন (ঈশ্বরের নামের সমবেত জপ) শুরু করেন। তিনি নবদ্বীপের সমস্ত নাগরিককে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র (স্তব) উচ্চারণ করার জন্য প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিটি বাড়িতে তারা নিয়মিত সংকীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে যখন সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়, তখন নবদ্বীপে কেউ "হরি! হরি!" শব্দ ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি শুনতে পায়নি। এবং মৃদঙ্গের (ঢোল) প্রহার এবং হাত করতালের সংঘর্ষ। হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের অবিরাম জপ শুনে স্থানীয় মুসলমানরা খুব বিরক্ত হয়ে চাঁদ কাজীর কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেশ করে।
নবদ্বীপ সিটি ম্যাজিস্ট্রেট কাজী উপাধি ধারণ করেন। তৎকালীন সিটি ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদ কাজী নামে পরিচিত ছিলেন। জমির মালিকরা জমির উপর কর ধার্য করত, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া কাজীর উপর অর্পিত দায়িত্ব। কাজী এবং জমিদার উভয়েই বাংলার গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, যিনি সেই সময়ে সুবা-বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিলেন। মাদিয়া, ইসলামপুরা এবং বাগোয়ানা জেলাগুলি হরি হোদা বা কৃষ্ণদাস হোদা নামে পরিচিত তাঁর বংশধরের অধীনে ছিল। কথিত আছে চাঁদ কাজী ছিলেন নবাব হোসেন শাহের আধ্যাত্মিক গুরু ।
এক মতে চাঁদ কাজীর নাম ছিল মাওলানা সিরাজুদ্দীন , অন্য মতে তার নাম ছিল হাবিবর রহমান । চাঁদ কাজীর বংশধররা এখনও মায়াপুরের আশেপাশে বসবাস করছে। লোকেরা এখনও চাঁদ কাজীর সমাধি দেখতে যায়, যা একটি চম্পাকা এবং নিম গাছের নীচে রয়েছে এবং এটি চাঁদ কাজীর সমাধি নামে পরিচিত। চাঁদ কাজী রাগান্বিত হয়ে একদিন সন্ধ্যায় শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন, এবং একটি আনন্দময় কীর্তন (গান) চলতে দেখেন, তিনি মৃদঙ্গ (ঢোল) ভেঙ্গে এইভাবে বলেছিলেন: "এত দিন ধরে আপনারা সবাই হিন্দু ধর্মের নিয়মনীতি অনুসরণ করেননি। , কিন্তু এখন আপনি খুব উৎসাহের সাথে তাদের অনুসরণ করছেন, আমি কি জানতে পারি আপনি কার শক্তিতে এমন করছেন?"
চাঁদ কাজী ছিলেন বাংলায় সম্রাট হোসেন শাহের রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মহাপ্রভুর সময়ে তিনি নবদ্বীপের শাসক এবং প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জানা গেছে যে তিনি কোরান নামক মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতেন এবং মুসলিম দেবতা আল্লাহর প্রতি তাঁর ভক্তি সম্রাটকে নির্দেশ দিতেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি সর্বক্ষেত্রে কট্টর ও একনিষ্ঠ অত্যাচারী ছিলেন এবং তিনি বিশেষ করে হরি নাম সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণলীলায় তিনি ছিলেন কংস, আর হোসেন শাহ ছিলেন জরাসন্ধ। একদিন চাঁদ কাজী শ্রীবাস অঙ্গনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন তিনি করতালের সুরেলা আওয়াজ এবং মৃদঙ্গের ছন্দময় প্রহার শুনতে পান। শঙ্খের ধ্বনি এবং হরিনাম সংকীর্তনের উচ্ছ্বসিত গান পরিবেশকে আনন্দে ভরিয়ে দিল। ভক্তদের উল্লাস শুনে কাজী তৎক্ষণাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং অন্যদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোরানের নির্দেশ তাঁর মনে আহ্বান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তিনি তা করতে পারেননি। আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শ্রীবাস অঙ্গন বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং এক ভক্তের কাছ থেকে একটি মৃদঙ্গ কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। তারপর তিনি তার লোকদের নির্দেশ দিলেন, তারা যাকে ধরুক তাকে মারতে। অবশেষে, তিনি আল্টিমেটাম জারি করেন যে কেউ কৃষ্ণের নাম গাইতে ধরলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। কাজী হিন্দুদের উপর পানি ছিটিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা করছিলেন।
পরের দিন ভক্তরা ভগবান চৈতন্যের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। প্রভু যখন শুনলেন যে চাঁদ কাজী সংকীর্তন আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও মহাজাগতিক বিনাশের শেষের দিকে রাগান্বিত শিব তাকায় ভগবান চৈতন্য যেভাবে ক্রুদ্ধ ছিলেন তার তুলনায় মৃদু ছিল। এমন এক দৃষ্টিতে যা নম্র বিদ্যুত এবং বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে অবিলম্বে সমস্ত বৈষ্ণবদের একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেককে একটি জ্বলন্ত মশাল আনার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে তারা একসাথে পুরানো নবদ্বীপ শহর জুড়ে একটি বিশাল নগর সংকীর্তন করবেন।
ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামগুলি গেয়েছিলেন এবং আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রথম জনসাধারণের সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ।
সমস্ত বৈষ্ণব একত্রিত হলে ভগবান চৈতন্য তাদের দলে বিভক্ত করেন। অদ্বৈত আচার্য একটি দলের নেতৃত্ব দেন। হরিদাস ঠাকুর আরেকটি দলের নেতৃত্ব দেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিত আরেকটি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিটি দলকে চারজন মৃদঙ্গ বাদক, ষোলজন করতাল বাদক, একজন কীর্তনের বিশেষজ্ঞ নেতা এবং একজন উচ্ছ্বসিত নর্তক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। প্রতিটি দলকে হাজার হাজার ভক্ত অনুসরণ করেছিল, সবাই তিলক দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল এবং প্রত্যেকে তুলসীর মালা দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছিল। শঙ্খের জয়ধ্বনি, কিছু গভীর এবং কিছু উঁচু, বাতাসে ভরে উঠল।
ভগবান শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন-লীলা পূর্ববর্তী কোন অবতারে প্রকাশ পায়নি। ভগবান চৈতন্যকে লক্ষাধিক সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সুগন্ধি মালতি ফুল তাঁর চুলকে সাজায়, এবং পাঁচ জাতের ফুলের একটি সুন্দর ফুলের মালা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলেছিল। তার শরীর গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং চন্দন কাঠের পেস্ট দিয়ে মাখানো হয়েছিল। একটি মিষ্টি হাসি তার মুখে শোভা পাচ্ছে। ভগবান চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দকে তাঁর পাশে রেখে, গঙ্গা নদীর তীরে উত্তর দিকে লক্ষ লক্ষ লোককে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি মহাপ্রভু ঘাট নামক তাঁর নিজের স্নানস্থলে গিয়ে উচ্ছ্বসিত নৃত্য করেন। এরপর তিনি মাধাই ঘাট, বড়কোনা ঘাট এবং নাগরিয়া ঘাটে নাচলেন এবং তারপর গঙ্গার তীরে চলে গেলেন। ভগবান চৈতন্য তখন গঙ্গানগর গ্রামের মধ্য দিয়ে নৃত্য করেন এবং তারপর সিমুলিয়াতে যান যেখানে চাঁদ কাজী বাস করতেন। এটি শ্রীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, 23ম অধ্যায়ে (298 নম্বর শ্লোক দিয়ে শুরু) শাব্দিকভাবে পড়া যেতে পারে।
কাজী যখন উত্তাল হৈচৈ শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার গুপ্তচরদের পাঠালেন গোলমালের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। গুপ্তচররা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বিশাল নগর সংকীর্তন দলকে দেখে এবং হরে কৃষ্ণ কীর্তনের গর্জন শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা কাজীর কাছে পৌঁছে তাকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। তারপর তারা যা দেখেছিল তা জানিয়েছিল।
From Aranya Saha
Author: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingনবদ্বীপের চাঁদকাজী পুরো নদীয়ায় হিন্দুদের কীর্তন গানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।
কিন্ত স্বপ্নে সে ভগবান উগ্র নৃসিংহের বিকট মূর্তি দেখলো।
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর।।
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়।।
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ–বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মানিল॥
জয় শ্রী নৃসিংহ Read More
Author: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingমাত্র ৩২ বছরের আয়ুতে...
★ ভারতবর্ষকে ৩ বার খালি পায়ে প্রদক্ষিণ করে,
★ তৎকালীন ভারতবর্ষে বিদ্যমান মোট ৭২ টি বিরোধী ও নাস্তিক্য মতবাদকে তর্কে পরাজিত করে,
★ মহাভারত থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরে,
★ ১১ টি প্রধাণ উপনিষদের ভাষ্য করে,
★ বেদব্যাস রচিত মহান ব্রহ্মসূত্রের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচনা করে,
★ ১৫১ টি শাস্ত্রীয়, জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে,
★ দেবদেবীদের নিয়ে বহু ভক্তিপূর্ণ স্তোত্র রচনা করে,
★ ভারতের ৪ প্রান্তে ৪ মঠ স্থাপন করে,
★ সেই ৪ মঠে নিজের ৪ প্রধাণ শিষ্যকে দায়িত্ব দিয়ে,
★ ৪ মঠে ৪ বেদের চর্চা ও ৪ মহাবাক্যের চর্চার নীতি স্থাপন করে,
★ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে...
পুনরায় সনাতন ধর্মকে উজ্জীবিতকারী জগৎগুরু ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব তিথিতে উনার শ্রীচরণে জানাই কোটি-কোটি প্রণাম
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 15-May-2024 by east is rising"Brahmins are mostly 5'8" tall, with good physique, given to very good personal hygiene, who shave daily and are extremely reliable, making them very good soldiers". This was the note circulated to all unit commanders in India by the British Indian Military Intelligence Branch in the 1897.
In the 19th century the British Indian Military Intelligence Branch issued special handbooks to its unit commanders. These handbooks were called “Caste Handbooks for the Indian Army”. All unit commanders were supposed to read them closely and use the insights they offered in managing their troops.
This is what the military handbooks compiled by the Intelligence Branch said:
India was divided into three caste groups. Brahmins, who studied; Kshatriyas who ruled; Vaishyas who produced wealth. Do notice that there is no mention of untouchables or of shudras.
This is what the note on Brahmins said (given below is an complete excerpt from chapter 1 of the Intelligence Branch Handbook on Brahmans):
“Endowed with subtle minds, trained to the utmost keenness, and intellectually far in advance of any other caste, the Brahmans were peculiarly fitted for the business of political administration. They were largely employed in civil capacities, not only by Hindu Princes, but also by the Mughal Emperors, who recognized their ability and fitness for positions of trust. The chief adviser of the Emperor Akbar in matters of revenue, finance, and currency, was the Raja Todar Mai, a Brahman of the greatest ability and integrity.
Throughout the centuries of Muhammadan dominion the Brahmans never relinquished their ascendancy over the rest of the Hindu world. As their numbers increased, however, it became impossible for the whole caste to devote itself exclusively to religious functions. In the Doaba and on the banks of the Ganges and Jumna, where the principal shrines were situated, Brahmans became very numerous. Many compelled to resort to agriculture as a means of livelihood, and as they collected in villages and acquired land, the unsettled state of the country compelled them to take measures for the defence of their rights against the encroachments of their warlike neighbours.
There thus arose a class of Brahmans who, while retaining the privileges of a Levite caste, were in all essentials an agricultural people, of naturally pacific tendencies, but ready and able to defend themselves whenever occasion required. War, pestilence, and famine, often compelled the younger member of these communities to seek employment at a distance from their homes, and, as their religion debarred them from the acceptance of menial offices, they naturally resorted to military service as the only form of employment which could be accepted without loss of caste.
The general anarchy which followed the breaking up of the Mughal Empire compelled most of the European settlers in India to entertain corps of native irregulars for the defence of their posts and factories. The idea of giving discipline to these levies originated with the French, but other nations, and the native princes, were not slow to follow their example, and by the middle of the 18th century the Madras and Bombay settlements of the English East India Company possessed a considerable force of wellU trained topasses «topasses were Portuguese half-castes and native Christians, enlisted by the East India Company, and so called because they wore topis or hats. They were armed and dressed exactly like Europeans» and sepoys, armed and equipped like Europeans.
After the recapture of Calcutta in 1757 it was decided to form a similar force for service in Bengal, and early in that year Clive raised the
1st Regiment of Bengal Native as the Lal Pultun, because it was the first native corps to be dressed in red.
Nearly all the warlike races of Northern India were represented in the new corps, for, owing to the Muhammadan conquest of Bengal, the province was overrun by bands of military adventurers from Oudh, the Punjab and even from beyond the Indus. It was from men of this stamp that Clive selected his recruits, and in the corps raised about this time in Calcutta were to be found Pathans, Rohillas, Jats, Rajputs, and Brahmans.
The majority of the men were Musulmans, but as most of our early campaigns were directed against Muhammadan princes, it was considered expedient to gradually replace them by Hindus. It thus came about that the ranks of the Bengal regiments were filled almost entirely by Brahmans and Rajputs from Behar, Oudh, and the Doab, until our military service became practically the monopoly of these classes. Other reasons tended to encourage the enlistment of high caste Hindus. They were more docile and easily disciplined, they were quicker to learn their drill; and their natural cleanliness, fine phusicque and soldierly bearing, made them more popular with their European officers than the truculent Muhammadans from the north, to whom pipeclay and discipline were abhorrent.
No historical notice of the Brahmans would be complete without some reference to their military services. It is, however, impossible to separate the deeds of our Brahman sepoys from those of their comrades of other classess, for as the Hindustani portion of the army was not organized on the class system until 1893, for its achievements could not be allotted to any particular caste without obvious injustice to the others.
Brahmans have served in our ranks from Plassey to the present day. They have taken part in almost every campaign undertaken by the Indian armies. Under Forde they defeated the French at Condore. Under Cornwallis they assisted at the capture of Seringapatam. Under Lake they took part in the Mahratta wars, including the siege of Bharatpupr. As volunteers, Brahmans took part in the conquest of Java, also in the Nepal campaign, and in the expeditions to Burma and China. Brahman sepoys shared in the victories and disasters of the first Afghan War, including the defence of Jelalabad. In the Sikh wars, Brahmans and other Hindustanis helped us to win the Punjab, and even the Great Revolt of 1857 furnishes many instances of their personal devotion and fidelity. In Sir Hugh Rose’s brilliant campaign in Central india, nothing could surpass the gallantry and loyalty of certain regiments of the Hyuderabad Contingent, which was largely composed of Brahmans, Rajputs, and other classes recruited from the North-West Provinces. ….
Since the Mutiny, Brahmans have taken part in the Afghan War, in the expedition to Egypt, in the conquest of Burma, and in numerous expeditions on the north-west and north-east frontiers of India. At the storming of Minhla, the Brahman sepoys of the 11th Bengal Infantry were the first to enter the fort, and on the conclusion of the war two Brahman native officers of this regiment were awarded the order of merit, for valiant and distinguyished conduct whilst holding independent commands. In the same campaign a detachment of the 4th Bengal Infantry, undera a Brahman. Subadar, made a forced march of 65 miles in 36 hours, stormed Kendat, and thereby saved a number of European officials from a cruel and untimely death. With such an excellent record in the past, it may be confidently predicted that the new organisation into class regiments will enable our Brahman sepoys to add yet further to their military reputation, and place them on an equality with the most warlike of the races now serving under the British colours.
Pic. Painting from 1900 of an Indian sepoy in the employ of the British Indian Army.
Collected from Facebook Page "India History"
Author: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 02-May-2024 by east is risingThrough electoral democracy, hindi votebank rules via numerical superiority. That creates hindi domination. Central government is be all end all in india so hindi belt runs indian government and exploits coastal non-hindi productive nations. Along with hindi belt, internal northeast, punjab, coastal odisha also joins this exploitation. Punjab and northeasten states bargain more freebies via threat of cessation, they actually do not seek to separate.
Hindi domination creates Gujarati, Rajasthani, Haryanvi, Sindhi etc baniya monopoly in economy. Only baniyas are allowed to own capital and state policies are made it such way. Baniya hegemony is maintained through hindi domination.
Through votebank reservation and other freebies of reserved castes and tribes established via exploitation of general castes.
Whoever forms votebanks gains their share according to bargaining power.
Upto 90s india maintained baniya hegemony through license raj and hindi domination through anti-colonial sentiments. India played the 'Democratic Socialist' card to gain blank cheques from USSR and maintaining their exploitative structure.
After 90s, this changed into 'West has democracy, west is best, so democracy is best.' But after USA hegemony is weakened, India needs new justifications for legitimacy. Then tgis new Indian nationalism and hindutva emerged. Rise of China has threatened Indian ruling class so much that they have decided that the heterogenity is a threat. So they seeks to homogenise india as soon as possible. This was always goal of indian ruling class but they did it in slow-poisoning manner so that nobody can understand what was happening. But indian ruling class has decided that this process was too slow and time is running out. So they have entered into direct and quick mode. This has also revealed the reality of indian state.
In slow-poisoning mode, indian polktics had several compradors and lackey beneficiaries like leftists, caste lobbies, postmodernist lobbies, religious minority lobbies etc. They often acted as diversion, controlled opposition and agents of state itself. But indian state has reached a material condition where they does not require any lackeys anymore. They are in a direct mode now so its over for compradors. But the more indian state is trying to homogenise, the more internal contradictions are getting significant. This will play crucial role in future.
With China's rise, all indian state constructs are slowly falling apart and also creations of anglo hegemony is getting irrelevant. This will also play another crucial factor.
Read MoreAuthor: Purandhar Khilji
Theoretical Hindu 30-March-2024 by east is risingরাম মন্দির নির্মাণ বুঝিয়ে দিল এখন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতের বাম ও সংখ্যালঘু অংশ ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আর কোনও লড়াই চালাতে পারবেনা। হয় বাম ও সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক পরিকাঠামোরই বিরুদ্ধে যেতে হবে অথবা চুপচাপ হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে। আমার ধারণা অধিকাংশ বাম ও সংখ্যালঘু মানুষই এই হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে বাধ্য হবে বা ভয়ে মেনে নেওয়ার ভনিতা করতে বাধ্য হবে। কারণ সাধারণ মানুষ কোনও দিনই রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে পারেনা বা লড়াই করার দায় নেয়না। ফলে হিন্দু রাষ্ট্র বিরোধিতা ঠিক্টহাক করতে গেলে ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে লড়াই করা ছাড়া আর উপায় রইলনা। এর একটা সুবিধে হল ঢপবাজ স্বার্থ লোটা হিন্দু বিরোধী অংশটা শেষ হয়ে যাবে। আর সেকুলার উদারবাদী ভারতের স্বপ্ন দেখানো যাবেনা।
রাম মন্দির নির্মাণকে প্রায় উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছে গ্রাম পশ্চীম বঙ্গ। কোথাও দীক্ষা গুরু নিরামিষ খাবার আদেশ দিয়েছেন রাম মন্দির নির্মাণের দিন, আবার কোথাও এক সন্যাসি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চারটে চাল দিয়ে বলেছে খিচুরি পায়েস করে খেতে। আর মোড়ে মোড়ে রামের মূর্তি বানিয়ে গাম চালিয়ে গেরুয়া ঝাণ্ডা তুলে নাচানাচি তো আছেই। গ্রাম পশ্চীম বঙ্গের হিন্দুরা বলছে দারুণ কারণ মুসলিমরা না কি এই সব দেখে "চুপসে" গেছে। এই "চুপসে যেতে" দেখেই সাধারণ মানুষ এবার বিজেপি-কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। ২০২৪-এ বড়ো জয় নিয়ে এসে "ডিলিমিটেশন ২০২৬" করে সাংবিধানিকভাবেই হিন্দি-গুজারাতি-দের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে কারণ সংসদের দুই কক্ষের সাংসদ-দের ৫২% আসবে হিন্দি প্রদেশগুলো আর গুজারাত থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় লারী পূজারী পাপাচারী জাতিটা পাশের বাড়ির লোককে "চুপসে যেতে" দেখেই আনন্দে মসগুল আসল ক্ষমতাবান অর্থাৎ গুজারাতি-হিন্দিদের হাতে সব চলে যাচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা এদের নেই।
ভারত রাষ্ট্র সবসময় গুজারাতি-হিন্দিদের অধিকারে থেকেছে। গুজারাতি ও রাজস্থানীদের (হিন্দিদের একটা অংশ) পুঁজি আর হিন্দিভাষিদের ভোটব্যঙ্ক সবসবয় ভারতের বাকিদের থেকে বেশি শক্তিশালী থেকে গেছে। জন্মহারে বাকিদের পিছিয়ে পড়া গুজারাতি-হিন্দিদের ক্ষমতাকে আরও স্থায়িত্ব দিয়েছে ও শক্তি যুগিয়েছে। ফলে আজ আর সমাজতান্ত্রিক বা সেকুলার সাঁঝার প্রয়োজন নেই গুজারাতি হিন্দি অক্ষের। আজ তারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের আগ্রাষণ চালাবে। একে আটকাবার শ্রেণিবাদী, ভীমবাদী নারীবাদী বা সংখ্যালঘুদের নেই। দক্ষিণ ভারতে তামিল-তেলেগু-মালোয়ালী-কণ্ণড়-টুলু দ্রাবিড়ীয় অক্ষের কাছ থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ একটা প্রতিরোধ অবশ্যই পাবে। শিখ, কাশ্মীরি, উত্তরপূর্বের ও মধ্য ভারতের কিছু উপজাতিও কিছুটা লড়াই দেবে।
তবে আরও দুটো জায়গা থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ ঝামেলায় পড়বে। এক, গুজারাতি ব্যবসায়ী ও হিন্দি রাজনীতিবীদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে মোদী পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে অমিত শাহ বনাম যোগী হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দুই, আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি। চীনের উত্থান ভারতের ক্ষমতা দক্ষিণ এশিয়াতে কমিয়ে ফেলেছে এবং চীন ভারতের জমিও আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আটকাতে ভারতকে বলির পাঁঠা বানাতে চাইছে। গুজারাতি-হিন্দি চরিত্র ঝুঁকি প্রবণ বা দুঃসাহসী চরিত্রের নয় আর তাই মার্কিন কথায় তারা সরাসরি চীনের সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চায়না।চীন অন্যদিকে জানে যে ভারত-কে শেষ করে দিলেই মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল খতম। তাই চীনও ভারতের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন দুর্বলতাগুলো ভালভাবে বুঝে নিচ্ছে। গুজারাতি-হিন্দি অক্ষের এক ভাষ এক ধর্মের ভারত চীনের কাছে ভাবী হুমকি। নিজের পাশে একটা সমান ক্ষমতাধর দেশ কোনও দেশই চায়না। ভারত আজ সত্যি এক ঐতিহাসিক দিন দেখল।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 22-January-2024 by east is risingআজকাল একটা হিড়িক উঠেছে - বাঙালির কোনো একটা অক্ষমতার বা, ক্ষতিকর দিক উঠলেই,
"আরে এর কারণ ৩৪ বছরের বাম শাসন" - এই oneliner
অন্য কিছু বলার আগে একটা সহজ প্রশ্ন ,
সুচেতা কৃপালিনী এর জন্ম যখন, তখন বাম ভাবধারা ছিল ?
উত্তর - না।
জানা না থাকলে জেনে নিন, এই সুচেতার পৈতৃক পদবী কিন্তু মজুমদার।
সুচেতা মজুমদার - যার বাঙালি পিতা
এই পর্যায়েও কিন্তু সেরকম উল্লেখ কোনো বাঙালি পুরুষ পাওয়া যাবেনা, যে হিন্দি মেয়েকে বিয়ে করেছে।
আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে আরো একটা উদাহরণ দিই,
ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি - প্রসিদ্ধ নাম !
তাই তো?
এই ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির ইতিহাস কি?
এক বাঙালি বিধবা সৌদামিনী আর একজন পর্তুগিজ পুরুষের প্রেম সম্বন্ধ এর কাহিনী হল এই ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি।
একটু feel করার চেষ্টা করুন scenario টা -
দেশ আপনার, সেই দেশের নারীর ওপর প্রথম অধিকারও সেই দেশের ভূমিপুত্র পুরুষের,
সেই দেশে শুধু যে একজন বিজাতীয় বিধর্মী পুরুষ আসছে তাই নয়, সে বিজাতীয় পুরুষের সাথে আপনার দেশীয় নারীদের সম্পর্ককে incentivise করছে যে architecture (মন্দির) সেখানে লোক দলে দলে ভক্তি ভাব নিয়ে পুজো দিতে যাচ্ছে।
তাই, যারা সবকিছুর root cause হিসেবে বাম আমলের নাম নেয়, they're nothing else than cheap political stooge
বাম আমলের বহু আগে ১৮৭০ থেকেই কোলকাতার বদলে বোম্বেকে incentivise করা শুরু করে ব্রিটিশ সরকার,
১৯৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই কলকাতা থেকে আর্মেনিয়ান , ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ রা একে একে নিজের ব্যবসা তুলে দিচ্ছিল,
আর তুলে দেওয়ার আগে সেই ব্যবসা দিয়ে যাচ্ছিল নিজেদের প্রিয় মারওয়ারি, বানিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে
এখনও, কিন্তু বাম আমল আসা আরো ৩০ বছর বাকি!
তাই, বাম আমলের অনেক আগে থেকেই বাঙালি মৃত্যুশয্যা রচিত হয়ে গেছিল,
বাম আমল বাঙালির ধ্বংসের কারণ নয়, বরং বাঙালির ধ্বংসের ফলাফল।
Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman
Historical Hindu 16-November-2023 by east is risingAniket Mitra লিখেছেন ফেসবুকে
বাস্তব:-
হিন্দি ভারতের কোনো দেশজ ভাষা নয়, মাটির ভাষা নয়। তাই হিন্দিতে কোনো লোকসংস্কৃতি নেই। কিন্তু ভারতের বাকি ভাষাগুলির আছে।
হিন্দিতে কোনো ধ্রুপদী সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির সৃষ্টি ও রচনা নেই। কিন্তু ভারতের বাকি ভাষাগুলিতে (অধিকাংশতেই) আছে।
পেছনের ইতিহাস:-
ব্রিটিশ হানাদারদের লুটতরাজ ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত এই অর্বাচীনতম খিচুড়ি ভাষা, হিন্দিভাষা। ব্রিটিশদের উদ্যোগেই হিন্দির যাত্রারম্ভ। ব্রিটিশ আগমন তো দূর, ব্রিটিশ উদ্যোগের আগে অবধি হিন্দি নামক কোনো ভাষার অস্তিত্ব ছিলোনা ভূভারতে!
"ভারতীয়দের ভাষা" নামক একটি মিথ্যা তকমা এঁটে ইংরেজির বদলে অন্য ভাষার মাধ্যমে একই কাজ সুসম্পন্ন করার নীলনকশার প্রথম ধাপ হিন্দি নামক কৃত্রিম একটি ভাষার নির্মাণ। ভারতীয়দের বোকাও বানানো গেল, ব্রিটিশদের কাজকম্ম অব্যাহত থাকলো।
এরপরের ধাপে ব্রিটিশ দালাল গুজরাটি-পারসি-মাড়োয়াড়ি বানিয়া গোষ্ঠীর অর্থপুষ্ট দিল্লী থেকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় ভূরাজনীতির প্রবর্তন। তারপরে মাঠে নামানো হলো বলিউডকে, বিনোদনের মাধ্যমে মগজধোলাই করার জন্য -- একপ্রকার social engineering।
হিন্দি ভাষার পূর্বসূরীর জন্ম বহিরাগত হানাদার মোঘলদের সেনাছাউনি এবং হারেমে। সুলতানদের দরবারি ভাষা আরবি মিশ্রিত ফারসির সাথে দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খড়িবলি ভাষার মেলবন্ধনে প্রচলিত একটি ততোধিক মিশ্র ভাষা তৈরী হয় যার পোষাকি নাম জুবান-ই-ওর্দু। এর আক্ষরিক অর্থ, সেনাছাউনির ভাষা। তার থেকেই উর্দু। মোঘলরা যেহেতু সরকারি কাজের মাধ্যম হিসেবে এই ভাষাটাকে বেছে নিয়েছিল, তার ফলে প্রচুর প্রচুর আরবি ফার্সি তুর্কি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। সে ভাষার লিপি ছিল পারস্য-আরবি লিপি বা নাস্তালিক লিপি।
এই জুবান-ই-ওর্দু মধ্য এশিয়াতে জুবান-ই-হিন্দভি বা হিন্দুস্তানি নামে প্রচলিত ছিলো। তাই ব্রিটিশরাও এই নামটাই তুলে নিয়ে এই ভাষাকে 'হিন্দুস্তানি' নামে ডাকতো।
সেই জুবান-ই-উর্দু ওরফে জুবান-ই-হিন্দভি ওরফে হিন্দুস্তানি ভাষা থেকে ১৮০০-র শুরুর দিকে স্কটিশ ভাষাবিদ জন বর্থউইক গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে মাড়োয়াড়ি বানিয়া তাঁবেদার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, গুজরাটি ব্রাহ্মণ তাঁবেদার লাল্লু লাল এবং আরো ২-১ জন কর্তৃক কলিকাতার বুকে ভারতের সর্বপ্রথম ফ্রীমেসনস্ লজ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উর্দুর থেকে কিছু ফারসি আরবি সরিয়ে তার জায়গায় সংস্কৃত গুঁজে এবং বাংলার শব্দভাণ্ডার থেকেও কিছু ধার করা শব্দ গুঁজে দিয়ে একটি বকচ্ছপ ভাষা নির্মিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'হিন্দি'।
পূর্বতন নাস্তালিক লিপিটা উর্দুর জন্যেই বরাদ্দ রেখে পশ্চিমী নাগরী লিপিতে হিন্দির প্রমিতকরণ করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ক্রিয়াকলাপ সেপাই বিদ্রোহের (ব্রিটিশ প্রভুকে ভাল্লাগছেনা তাই মোঘল প্রভুতে প্রত্যাবর্তনের নামে যে হইহট্টগোল, সেটাই 'সেপাই বিদ্রোহ') আরো আগে। একটু তলিয়ে ভাবলেই হিসেব মিলবে।
আপাতবৈপরীত্য ও দ্বান্দিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে একটু একটু করে ঘেঁটে দেওয়ার কারসাজি।
বিশ্বাস না হলে উর্দু এবং হিন্দির ব্যাকরণ, ভাষার ব্যবহার, গঠন, লিঙ্গের ব্যবহার ও নিয়মবিধি ঘাঁটলেই উভয় ভাষার অভিন্নতা প্রকট হবে।
কার্যত, হিন্দি হচ্ছে লিপ্যন্তরিত উর্দু।
ব্রিটিশ তাঁবেদার ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ব্রিটিশদের থেকে এই বাংলার বুকে জমিদারি পায় এবং তাঁবেদার লাল্লু লাল তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাবের সেবায় রত ছিল। বাংলার বুকে মাড়োয়াড়ি জমিদারদের বংশধর ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ আমলে বাংলার নগজাগরণ প্রত্যক্ষে করে। সেটা দেখাদেখি তার নিদান ছিল -- "বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের সহায়তায় হিন্দি ভাষায় উন্নতিবিধান।" এদেরকেই ব্রিটিশরা বেছে নেয় হিন্দি নির্মাণপ্রকল্পে সাহায্যের জন্য।
এবারে আসা যাক, হিন্দুস্তানি ভাষায় বৈদগ্ধ্য অর্জনকারী স্কটিশ ভাষাবিদ John Borthwick Gilchrist সাহেবের ব্যাপারে। এই গিলক্রিস্ট সাহেব ছিল অধুনা ব্যবহৃত হিন্দি ভাষার জনক, হিন্দুস্তানি ভাষার সর্বপ্রথম অভিধানপ্রণেতা এবং বৈয়াকরণ। তার রচিত শব্দকোষ পারস্য-আরবি বা নাস্তালিক লিপি, নাগরী লিপি এবং রোমান লিপিতে প্রকাশিত হয়। সাহেব আবার নিজের কাজের অর্থযোগানের চাহিদা মেটাতে আফিম এবং নীল চাষও করাতেন; সেসব চাষের কালো ইতিহাস অনেকেই জানে!
এই "মহানুভব" সাহেবের রচিত কিছু গ্রন্থাদি নিম্নরূপ:-
১. A Dictionary: English and Hindoostanee
২. Dialogues, English and Hindoostanee, calculated to promote the colloquial intercourse of Europeans, on the most useful and familiar subjects, with the natives of India, upon their arrival in that country
৩. A Grammar of the Hindoostanee Language
৪. The Hindee-Arabic Mirror; or improved Arabic practical tables of such Arabic words which are intimately connected with a due knowledge of the Hindoostanee language
৫. The Hindee-Roman Orthoepigraphical Ultimatum
৬. Dialogues, English and Hindoostanee; for illustrating the grammatical principles of the Strangers' East Indian Guide, and to promote the colloquial intercourse of Europeans on the most indispensable and familiar subjects with the Natives of India immediately upon their arrival in Hindoostan
গিলক্রিস্ট সাহেবের গ্রন্থগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, ইংরেজদের অপশাসন, লুন্ঠন ও শোষণের সুবিধার্থে হিন্দুস্তানি তথা হিন্দি-উর্দুর যথাসম্ভব ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়াস হয়েছে গোটা উত্তরভারত জুড়ে। যার ফলে উত্তরভারতের বিভিন্ন জাতীয় ভাষাগুলি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজরা ইংরেজি এবং হিন্দুস্তানির মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পেয়েছিল। এও সত্যি যে আরবি এবং হিন্দিরও একটি সংযোগ আছে... উর্দুর গর্ভজাত ভাষা বলে কথা!!
ফরাসি ভাষাবিদ Jules Bloch, যিনি একটি ভাষার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে সেই ভাষার গবেষণা করতেন, তিনিও লাল্লু লালের গ্রন্থ 'প্রেম সাগর' নিয়ে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছেন যার নিম্নরূপ --
"Lallu Lal, under the inspiration of Dr. Gilchrist, changed all that by writing the famous Prem Sagar, whose prose portions are on the whole Urdu, from which Persian words have been throughout replaced by Indo-Aryan words… The new dialect gave a lingua franca to the Hindus."
প্রেমসাগর-কে হিন্দিতে সৃষ্টি ভেবে হিন্দির গর্বে গর্বীয়ান কল্পজগৎনিবাসীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে!
A History of Hindi Literature নামক গ্রন্থে লেখক K.B. Jindal বলছেন -- "Hindi as we know it today is the product of the nineteenth century."
ওদেরই লোক হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে!
মান্য বা প্রমিত হিন্দি বা তথাকথিত খাঁটি হিন্দি সম্পর্কে প্রখ্যাত আইরিশ ভাষাবিদ George Abraham Grierson বলছেন -- "an artificial dialect the mother tongue of no native-born Indian, a newly invented speech, that wonderful hybrid known to Europeans as Hindi and invented by them."
এই গ্রিয়ার্সন সাহেবের নামেই হিন্দির জন্য একটি সাহিত্য পুরস্কার চালু করা হয়, Dr. George Grierson Award... ভিনরাষ্ট্রে হিন্দি ভাষা প্রচার ও উন্নয়নের জন্য ভারতের হিন্দি অধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হয়। কিন্তু কালের কি অমোঘ পরিহাস: বহু আগেই গ্রিয়ার্সন সাহেব হিন্দির কাছা খুলে সেটার অর্বাচীনতা ও বকচ্ছপ প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়ে দিয়ে গেছেন!! যার নামে পুরস্কার বিতরণ করে নিজের চুরি ঢাকবে ভেবেছিল সেই কবে বলে দিয়ে গেছে "ছিঁচকে চোর!"
মোদ্দাকথা হলো গিয়ে উলেখযোগ্য ভাষাবিদগণ এবং হিন্দি ভাষার ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে একমত যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি ছয়-আঁশলা সংকর বকচ্ছপ ভাষার উদ্ভাবন ও নির্মাণ করা হয় ব্রিটিশদের দ্বারা। এই ভাষা না তো ভারতের কোনো জাতির দেশীয় ভাষা আর নাই এখানকার কোনো ভূমিসন্তানদের মাতৃভাষা।
হস্তান্তরিত ভারতে কংগ্রেসী আমলে মধ্যপ্রদেশের বেওহর রাজেন্দ্র সিনহা, উত্তরপ্রদেশের হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, মহারাষ্ট্রের বালকৃষ্ণ কালেল্কার, উত্তরপ্রদেশের মৈথিলীশরণ গুপ্তা এবং মধ্যপ্রদেশের নামী ব্যাংকিং পরিবারের শেঠ গোবিন্দ দাস (অবাঙ্গালী) প্রমুখ সংসদবভবন এবং ভারত জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে। সমাবেশ বসায়, চাপ সৃষ্টি করে।
এতো অনুনয়বিনয়, তর্কবিতর্ক আর দালালির পরে অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সাধারণাব্দে বেওহর রাজেন্দ্র সিনহার জন্মদিবসকেই 'হিন্দি দিবস' হিসেবে গ্রহণ করা হলো এবং হিন্দিকে ভারতের একটি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে সকলের উপরে চাপানোর পথ প্রশস্ত করা হলো।
উপসংহার:-
ক) ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল বলেই সর্বত্র হিন্দির এত রমরমা। ইংরেজির সাথে হিন্দি মেলানো যেতো বলেই ইংরেজরা এই ভাষাটার প্রসার, প্রচার ও প্রমোশান করেছিল।
খ) হিন্দি ভারতের নিজস্ব ভাষা নয়, ভারতের কোনো জাতি কিংবা জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়। হিন্দির উৎসে আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজির ছাপ বেশী। বলতে গেলে হিন্দির আগাপাশতলা অ-ভারতীয় অথচ হিন্দি দিয়ে ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষাগুলিকে গেলানো হচ্ছে। উত্তর, পূর্ব ও মধ্যভারতের ভাষাসমূহ ব্রজ, অওধি, ডোগরি, পাহাড়ি, হরিয়ানভি, রাজস্থানি, মেওয়ারি, গাঢ়ওয়ালি, বুন্দেলখন্ডি, বাঘেলখন্ডি, ভোজপুরি, মগধি, অঙ্গিকা, মৈথিলীর মতন ভাষাগুলি হিন্দির কবলে গিয়ে আজ মুমূর্ষু।
গ) ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে হিন্দি আগ্রাসন, সম্প্রসারণ ও সাম্রাজ্যবাদ আসলে প্রাক্তন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। অভিন্ন চরিত্র, অভিন্ন অভিসন্ধি। প্রভুদের কাজ তাদের ছেড়ে যাওয়া ভৃত্যেরাই করে চলেছে কারণ ভৃত্যেরা সেইরক্মই দাসখত দিয়েছিল। আজকে ভারতের যেসকল সরকার হিন্দি ও উর্দুর পেছনে অঢেল, অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করছে, তারা আসলে প্রভুদের আজ্ঞাপালন করছে। চাটুকার প্রবৃত্তি।
ঘ) ভারতের সংবিধানে যেই ধারায় শুধুমাত্র ইংরেজি ও হিন্দিকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিশেষভাবে হিন্দির প্রসারের নিদান দেওয়া হয়েছে, এইসব আসলে কাদের আদেশে করা হয়েছে আশা করি তা অনুমানে কষ্ট হবেনা!
ঙ) তথাকথিত "স্বাধীন" ভারতে আজও যারা "হিন্দি-হিন্দুস্তানি" বলে সপ্তম সুরে চেঁচিয়ে ক্যাওড়ামি করে, তারা আসলে নির্দিষ্ট সুরের তালে নাচছে?!!
চ) যে কাজ ইংরেজরা শুরু করেছিল, সেটা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে কংগ্রেস করেছে। কংগ্রেসের পর আজকে আরএসএস-চালিত বিজেপি করছে। ভারতের কিছু প্রাদেশিক সরকারও দোসর হিসেবে কাজ করছে। সব্বার সুঁতো যেন এক জায়গা থেকেই টানা হচ্ছে! আর জনগণ, থুড়ি, ভেড়াগণ যেন সংশোধনাতীত। জানবেনা, ভাববেনা, বুঝবেনা, শিখবেনা, শোধরাবেনা, জাগবেনা।
উপলব্ধি:-
এখনো আমাদের আগের ২-৩ প্রজন্ম মোটের উপরে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা মনে করার ভুলটা করে থাকে। সে তাদেরকে সংবিধানের ধারা বলে দিলেও তাদের গেঁতোমি যায়না -- এটাই হলো cognitive dissonance। বহুদিন ধরে মিথ্যের পুনরাবৃত্তি হতে হতে সেটা সত্যের ভেক ধরেছে যে সত্যি জানলে অস্বস্তি হয়।
আজকাল নাগরী লিপির দোহাই দিয়ে হিন্দিকে এখন সংস্কৃতের আধুনিক রূপ ভাবানো হচ্ছে। "দেবনাগরী" শব্দখানি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়, যাতে সাধারণ মানুষের অবচেতনে একটা অগাধ ভক্তিভাব জন্মে -- এটাকে বলে psychological operation।
হিন্দির ভিত এতোই দুর্বল যে নানান মিথ্যে ও কপটতার আবরণে ঢেকে রাখতে হয়। এই আবরণ সরিয়ে দিলেই হিন্দি ধপাস হয়ে যাবে, চুরমার হয়ে যাবে।
হিন্দি ভাষার পত্তন, প্রসার এবং গ্রহণ যেহেতু স্বাভাবিকভাবে হয়নি সেহেতু ছলে-বলে-কৌশলে আগ্রাসন একমাত্র উপায়।
১৪ই সেপ্টেম্বর মিথ্যাচারের দিবস
১৪ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জাতির দেশজ ভাষা গিলে খাওয়ার দিবস
১৪ই সেপ্টেম্বর নবরূপে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের দিবস
১৪ই সেপ্টেম্বর আদ্যোপান্ত একটি অভারতীয় ভাষিক-সাংস্কৃতিক একাধিপত্যের দিবস
১৪ই সেপ্টেম্বর একটি কালো দিবস
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 17-September-2023 by east is risingভবিষ্যতে এই পুরুষবিদ্বেষী আইনগুলোর কারণে হিন্দু পুরুষ এরপর বিদ্রোহী হয়ে না কালাপাহাড় হয়ে উঠে
হিন্দুত্বের সাথে হিন্দু আইনের কোন সম্পর্ক নেই,হিন্দু আইনগুলো তৈরি হয়েছে কলোনিয়াল পশ্চিমা আইনের অনুকরণে....
সবথেকে হাস্যকর কথা হলো যে আম্বেদকরকে ভারতের সংবিধান প্রণেতা হিসেবে ভারতবাসী জানে এটা চরম মিথ্যা।তার প্রমাণ হলো- আম্বেদকর যে আইনগুলো হিন্দু আইন হিসেবে তথাকথিত স্বাধীন ভারতের জন্য বলবৎ করেন সেগুলোর প্রত্যকটাই তিনি বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের সংবিধান হতে নিয়েছিলেন।
আজকাল হিন্দুত্ববাদীদের চরম আদর্শ হলো এই আম্বেদকর কিন্তু এই আম্বেদকর হিন্দু ধর্ম বিরোধী কম ছিলেন ন আর শেষ বয়সে গিয়ে বৌদ্ধ ও হয়ে গিয়েছিল।
চরম নারীবাদী এই নিম্ন মস্তিষ্কের ধুরন্ধর আম্বেদকর দেশ ভাগের পক্ষে ছিল।
দেশভাগের প্রক্কালে তিনি সবর্ণ হিন্দুদের বিশ্বাস অর্জনে হিন্দুত্বের কথা বলে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের জন্য অহিতকর পশ্চিমা আইনগুলো প্রণয়ন করেন।
হিন্দুদের সবথেকে বড় সমস্যা হলো তারা তাদের পক্ষে কেউ একটু বেশি বললেই তাকে ভগবান বানিয়ে দেয়,তার মূর্তি বানিয়ে পূজা করে।
আম্বেদকর ও তেমনই একজন,যে আম্বেদকর সংরক্ষণ করে হিন্দুদের এতো ক্ষতি করলো, পশ্চিমা আইন বলবৎ করে এতো ক্ষতি করলো তাকেই হিন্দুরা পূজা করে।
তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্রের সপ্নে মশগুল থাকা ছাগলগুলো এগুলো বুঝবে না।
নিজের বাপকে তারা অস্বীকার করে বা না মেনে অপরের বাপকে বাপ ডাকে বা মানে তাদের মতোই অবস্থা হিন্দুর!
নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে তাদের কোন আইন নেই, তাদের সব আইন পশ্চিমা বৃটিশদের অনুকরণে তৈরি!
যে জাতি পরানুকরণ করে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়,হিন্দুর ভবিষ্যত তমসায় ঘেরা।
ভবিষ্যতে এই পুরুষবিদ্বেষী আইনগুলোর কারণে হিন্দু পুরুষ বাধ্য হবে হিন্দু ধর্ম ছাড়তে এরপর বিদ্রোহী হয়ে না কালাপাহাড় হয়ে উঠে।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 08-August-2023 by east is risingPeople who migrated INTO Indian subcontinent to create India:
1. Stone Age Africans 40,000+ years
2. Neolithic Iranian farmers 7,000+ years
3. Steppe Pastoralists (Arya) 3,500+ years
4. Tibeto-Burmese, Austroasiatic 3,000+ years
5. Yavanas, Sakas, Pahalavas, Kushan, Hun, Gujar 2000 years
6. Turks, Afghans, Mongols, Arabs, Persians, Africans <1000 years
7. Europeans <500 years
This is based on archeology, history & genetic research.
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 12-May-2023 by east is risingসাকিব হাসান, কলকাতা:
From ‘In the Name of Love-Melancholy of God's Own Country’ to 'The Kerala Story' : Sudipto Sen's movie or 'Sanghthing'
বর্তমানে মিডিয়ার একাংশ "The Kerala Story" ফিল্মের জন্য যেভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সেই ফিল্ম নির্মানের পিছনে কারা রয়েছেন সেটা জানলে ফিল্ম নির্মানের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যাবে। এই ফিল্মও সেই রকম যেরকম লিবার্টি অফ আর্টের নামে মিথ্যার পাহাড় তৈরি করে কাশ্মীর নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। "The Kerala Story" -এর প্রযোজক, পরিচালকেরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ, ফ্যাসিস্ট নেতা ও কর্মীদের সমর্থন পাবেন। 'The Kerala Story' ছবির পটকথা লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী ছবিটি ওমান চান্ডির বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে (সেই বয়ান তৎকালীন বিধানসভার কার্যক্রমে রেকর্ড করা হয়েছে)। সেই বক্তব্যকে সঙ্ঘী মানসিকতার একটি দল মনগড়া করে গঠন করা হয়েছে। যা একেবারেই মিথ্যা।
তবে সত্য কি? আসল সত্য হলো- '25 জুন, 2012' -এ কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ওমান চান্ডি বিধানসভায় বলেছিলেন যে 2006 থেকে (2012 সাল পর্যন্ত) রাজ্যে মোট 2,667 জন মেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ওমান চান্ডি তার বিবৃতিতে একেবারেই বলেননি যে, কেরালায় প্রতি বছর 2,667 জন মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যে হিসেব পেশ করেছিলেন সেটা মোট প্রায় সাড়ে ছয় বছরের ছিল। অর্থাৎ, কেরালায় সাড়ে ছয় বছরে 2,667 মেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে ওমান চান্ডি ISIS -এ যোগদানকারী মহিলাদের বিষয়ে কিছু বলেননি। সহজ কথায়, কেরালার 32,000 মেয়ে কখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, না কেরালার কোনো ধর্মান্তরিত মুসলিম মেয়ে কখনও ISIS -এ যোগ দিয়েছেন। "The Kerala Story" -এর প্রযোজক হলেন 'বিপুল অমৃতলাল শাহ', যিনি একজন কট্টর গুজরাটি এবং নতুন ভারত কুমারের (পুরানো কানাডা কুমার) অংশীদার, যার সাথে তিনি প্রায় ছয়টি চলচ্চিত্র করেছেন। এবং 'The Kerala Story' -এর পরিচালক হলেন 'সুদীপ্ত সেন'। 'The Kerala Story' -এর পূর্বে পরিচালক সুদীপ্ত সেন ‘In the Name of Love-Melancholy of God’s Own Country’ শিরোনামের একটি ফিল্ম নির্মান করেছিলেন। 2018 সালে এই ফিল্মের স্ক্রিনিং তিনি JNU তে করছিলেন। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিও হয়। সেই সময়েও সুদীপ্ত সেন কেরল ও ম্যাঙ্গালোর থেকে হিন্দু মেয়েদের কথিত ধর্মান্তর, ইসলামিক জিহাদ, ISIS, কথিত ইসলামিকরণ নিয়ে একই সঙ্ঘী সুর তুলেছিলেন। আর 'In The Name of Love' ফিল্ম নির্মানের পিছনে তৎকালীন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দনের একটি বক্তব্যের অজুহাত দিয়েছিলেন, যেটা মিথ্যা ছিল। তখন এই সংখ্যা বলা হয়েছিল ১৭ হাজার, এখন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সংখ্যাও ইনি ইচ্ছা মতো বাড়িয়ে দিয়েছেন।
আমরা সবাই জানি কেন এই ধরনের ফিল্ম নির্মান করা হয়। যেহেতু সমাজের একটা বড় অংশ এতে সন্তুষ্ট, তাই এই ধরনের ফিল্ম তৈরি করা হচ্ছে। যাতে করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে সংখ্যাগুরু সমাজের মানুষের মন জয় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংস্মাত্মক মানসিকতা নির্মাণ করা যায়। আর এর ফলে BJP অর্থাৎ 'ভারত জ্বালাও পার্টি' ভোটে তার লাভ তুলতে পারে।
Author: তাহা আলী খান
Social Hindu 11-May-2023 by east is risingদুর্গাকে আমরা মা বলে ডাকি। দুর্গা পুজো আসলে মাতৃ পুজো। মানুষ যখন কৃষি শেখে তখন জমির উর্বরতা ও নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে এক সূত্রে গাঁথতে থাকে। তখন থেকেই "মাটি মানে মা" তত্ত্ব সমাজে প্রসারলাভ করে। কৃষির প্রসার বাড়লে, খাদ্যোতপাদন বাড়ে, ফলে আরও বেশি জনসংখ্যা ধারণ করা সম্ভব হয়, এবং এই বর্ধমান জনসংখ্যা ব্যবহার করে আরও বেশি অঞ্চল কৃষির আওতায় আনা যায়। তাই কৃষি সমাজে মাতৃ পুজোর প্রসার বাড়তেই থাকে।
এছাড়াও কৃষি আরম্ভ হওয়ার আগে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই বহুগামী ছিল। তাই কে বাবা তা জানা যেতনা আর তাই সন্তান মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হোত। তাই আদি মাতাকে পুজো করাও রেওয়াজ ছিল কৃষির বিকাশের আগে থেকেই।
তবে কালের নিয়মে যখন গবাদি পশু চারণ শুরু হয়, ছোট হস্তশিল্প আস, পণ্যের সংখ্যা বাড়ে, বাণিজ্য শুরু হয়, নগর গড়ে ওঠে, সেই নগরকে ও বাণিজ্যকে রক্ষা করতে দস্যুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তখন পুরুষের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। যোদ্ধা পুরুষ ও ব্যবসায়ী পুরুষকে বাদ দিয়ে আর সমাজ ভাবতেই পারতনা। তখন পুরুষ পুজো শুরু হয়। শেষে রাষ্ট্র গড়ে উঠলে নিরাকার দেবতা ধারনা আসে। কিন্তু সেই নিরাকার দেবতাকেও পুরুষ হিসেবেই ধারণা দেওয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র খাজনা বাড়াতে যুদ্ধ ও ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাই রাষ্ট্রের সাহায্যে যোদ্ধা-ব্যবসায়ী পুরুষের পুজো বিস্তারলাভ করে।
পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গাতেই সমাজের বিকাশ হয়েছে এবং সভ্যতা কৃষি ছাড়িয়ে সমাজ গবাদি পশু চারণ, ছোট হস্তশিল্প, ব্যবসা, নগর-এর পথে এগোতে থাকে। ফলে মাতৃ পুজো ছাপিয়ে সর্বত্রই যোদ্ধা-ব্যবসায়ী পুরুষের পুজো বিস্তারলাভ করে। তবু নানাভাবে কৃষি সমাজে মাতৃ পুজো টিকে থেকেছে। গ্রাম বাংলাতেও মাতৃ পুজো সেভাবেই টিকেছিল। রাষ্ট্র নিজের ব্যবসা এবং যুদ্ধের স্বার্থে পুরুষ পুজো প্রচার করলেও কৃষি সমাজের বিশাল একটা অংশ জুড়ে মাতৃ পুজোর প্রভাব রয়ে যায়।
বাংলাতে সেভাবেই মাতৃ পুজো টিকে ছিল। কিন্তু প্রথমে মোঘল এবং পরে ব্রিটিশ আঘাতে যখন বাংলা তার স্বাধীন রাষ্ট্র হারায় তখন বাঙালিকে ব্যবসা করতে, যুদ্ধ করতে, যোদ্ধা-ব্যবসায়ী পুরুষ পুজো করতে- বলার কেউ থাকলনা। তখন সমাজের প্রান্তরে টিকে থাকা মাতৃ পুজো সমাজের একমাত্র আরাধ্য হয়ে ওঠে। বাঙালি প্রথমে যুদ্ধ ভোলে, তারপরে ব্যবসা ভোলে। এখন সরকারী চাকরীর জন্য ধর্না দিয়ে বসে আছে। সমাজের বিকাশ থেকে শিক্ষা নিলেই বোঝা যায় বাঙালির মাতৃ পুজোর বাড়বাড়ন্ত আসলে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতারই প্রতিক।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 20-October-2022 by east is risingঅষ্টাদশ পুরাণের নামগুলি হল -১) ব্রহ্ম, ২)পদ্ম, ৩) বিষ্ণু, ৪) শিব, ৫) ভাগবত, ৬) নারদীয়, ৭) মার্কন্ডেয়,৮) অগ্নি, ৯) ভবিষ্য, ১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, ১১) লিঙ্গ, ১২) বরাহ, ১৩) স্কন্দ, ১৪) বামন,১৫) কূর্ম, ১৬) মৎস্য, ১৭) গরুড় এবং ১৮) ব্রহ্মান্ড।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 13-October-2022 by east is risingমহিষাসুর কোনও অশুভ শক্তির প্রতীক নন। তিনি শহিদ। আর্য সভ্যতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে ‘খুন’ হন হুদুড় দুর্গা নামে অনার্য বীর।
প্রাচীন কালে এই জনপদের নাম ছিল “বোঙ্গাদিশম” এবং যার মহান সম্রাট ছিলেন এই বোঙ্গাসুর বা মহিষাসুর। হুদুড় (বজ্রের ধ্বনিকে হুদুড় বলা হয়) বা বজ্রের মত ছিল তাঁর প্রভাব ও প্রতাপ। তাই তাঁর আর এক নাম হুদুড় দুর্গা। আনন্দস্রোতের বিপরীতে এ এক আশ্চর্য শোকগাথা৷ আকাশে-বাতাসে যখন শারদীয়ার আনন্দ, তখন এই ভারতীয় মানচিত্রেরই আর এক দিকে পালিত হয় দাসাই, যা আসলে শোক-উৎসব৷ মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে খুন করা হয়েছিল, এমনটাই দৃঢ় বিশ্বাস উপজাতির মানুষদের। তাই দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে একাংশ উপজাতির ঘরে আলোও জ্বলে না৷
পুরুলিয়ার ভালাগোড়া গ্রামে বহু বছর ধরে হুদুড় দুর্গার পুজোর প্রচলন৷ ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তৎকালীন সম্পাদক জিতেন্দ্র যাদব ছবি এঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এই পুজোয়।
মুখে মুখে প্রচলিত উপজাতিদের গানে বারবার ফিরে আসে জনগোষ্ঠীর পুরোনো ইতিহাস৷ চাঁইচম্পা বা চম্পা ছিল তাদের বাসভূমি৷ সেই আদিম জীবনে মেঘ ঘনায় আর্যদের দখলদারি শুরু হলে৷ প্রচলিত বিশ্বাস, হুদুড় দুর্গার সঙ্গে বাহুবলে এঁটে উঠতে না -পেরে অন্য কৌশল নেয় দখলদারেরা৷ রমণীর সঙ্গে লড়াইয়ে নীতিগত আপত্তি ছিল হুদুড় দুর্গার৷
তাই ছলনা করে এক আর্য নারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তাঁর৷ সেই নারীর হাতেই শেষপর্যন্ত মৃত্যু হয় এই অসীম বলশালী উপজাতি নেতার৷ হুদুড় দুর্গা বধ হওয়ার পর খেরোয়ালদের(উপজাতি) নেতৃত্ব দেওয়ার আর কেউ ছিল না৷ ধর্মগুরুদের পরামর্শে তারা সরস্বতী নদীতে স্নান করে মহিলাদের পোশাক পরে নাচতে নাচতে পূর্ব দিকে পালাতে থাকে৷ এই নাচই ‘দাসাই’ নাচ নামে প্রচলিত৷ আশ্বিন মাসও উপজাতিদের কাছে এক অর্থে দাসাই৷ দাসাইয়ের অর্থ অসহায়৷ নেতাহীন খেরোয়ালরা সেসময় যথার্থই অসহায় হয়ে পড়েছিল৷ দাসাই নাচের গানেও সেই হা -হুতাশ আছে৷ তাতে বলা হয়, ‘দুর্গা অন্যায় সমরে মহিষাসুরকে বধ করেছেন৷ হে বীর, তোমার পরিণামে আমরা দুঃখিত৷ তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ৷ আমাদের প্রণাম নাও …৷’
নবমীর দিন রঙিন পোশাক পরে, মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে, বাজনার তালে তালে নাচ -গান করেন সাঁওতালরা৷ সেদিন স্মৃতিতর্পণের পর হুদুড় দুর্গা তথা মহিষাসুরের উদ্দেশ্যে ছাতা উত্তোলনের অনুষ্ঠান চলে৷ যা পরিচিত ‘ছাতা ধরা’ উৎসব নামে৷ বীর বন্দনার এই পালা ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে আদিবাসী সমাজে৷ এই পুজোর প্রসারও ঘটছে ক্রমশ৷ দেশে এখন প্রায় ১৫০টি এলাকায় হুদুড় দুর্গার পুজো প্রচলিত আছে৷ হুদুড় দুর্গা পূজাকে নিজেদের সমগ্র জাতি চেতনার অহংকার হিসেবে দেখেন সাঁওতাল জনজাতির অনেকেই। এ যেন অনেকটা সরাসরি হিন্দু দেবতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রান্তমানুষের বীরগাথা, শোষিতের জয়গান।
ইতিহাসবিদরা এমনও বলেন, গ্রামীণ কৃষিপ্রধান সভ্যতার বাহক অনার্য জাতির কাছে মহিষরূপী মহিষাসুর চিরকালই খুব আপন। আজও ষষ্ঠী থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত উপজাতির (মূলত সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জাতি) পুরুষেরা সেরেঞ বা ভুয়াং হাতে ‘দাসাই নাচ’-এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষার একটা প্রয়াস করেন। মহিষাসুরের শোকগাথার মাধ্যমেই তাঁরা প্রমাণ করতে চান মানুষ হিসেবে তাঁরা আজও কতটা বঞ্চনা আর অবহেলার শিকার। দুর্গাপূজার পনেরো দিন পরেই আদিম আদিবাসীদের দ্বারা পালিত বাঁদনা পরবে গৃহপালিত পশু হিসেবে মহিষের পুজো করা হয়।
রাঁচি থেকে ৯০ কিলোমিটার এগলে গুমলা শহর। তারই কিছু দূরে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ঝাড়খণ্ডের ঘাগরা, চৈনপুর, বিষণপুর। দুর্গাপুজো এলেই ঝাড়খণ্ডের অসুর জাতি অধ্যুষিত এই তিন গ্রাম ডুবে যায় শ্মশানের নৈঃশব্দে। ঘরে ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ থাকে পুজোর চার দিন। যাতে আলোর রোশনাই তো দূর, ঢাকের আওয়াজটুকুও যেন ভুল করে ঢুকে না পড়ে! ‘পূর্বপুরুষ মহিষাসুরের হত্যার উৎসবে কেন সামিল হব আমরা,’ বেশ ঝাঁঝিয়েই উত্তর আসে প্রান্তজনদের কাছ থেকে। আগে তো নবরাত্রি উৎসবের টানা ন’দিনই গ্রামগুলিতে শোকপালন হত। সাদা থান পরে থাকতেন সকলে। মেয়েরা সাদা শাড়ি পরতেন। এখন সময় পাল্টেছে। সাদা কাপড় পরা বা শোকগাথা পাঠ হয় না। তবে দুর্গাপুজোর সঙ্গে এখনও সম্পর্কহীন এই প্রান্তজনেরা।
শুধু মহিষাসুর বধ নয়, পুজোর পরে ঝাড়খণ্ডের বিষণপুরের অসুর সম্প্রদায় দশেরায় রাবণ বধও মেনে নিতে পারেন না। রামলীলা উৎসবে গিয়ে রাবণের মূর্তি জ্বালানোর বিরোধিতা করেন আপামর সবাই। মহিষাসুর এবং রাবণই এই এলাকার অধিবাসীদের আত্মার আত্মীয়। আরাধ্য দেবতা। দুর্গাপুজোকে তারা কার্যত ‘গণ-বয়কট’ করেছে। পুরাণ ঘেঁটে অসুর জনজাতির আসল রহস্য, আর্য-অনার্য তত্ত্বের হাল-হকিকত বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন ইতিহাসবিদ, গবেষকরা। বাংলা ও ঝাড়খণ্ড জুড়ে অসুর জাতি অধ্যুষিত-গ্রামগুলির এই সংস্কারের আসল কারণ কিন্তু আজও রহস্যে ঘেরা। বছর বছর আশ্বিনের শারদপ্রাতে বিষাদের মেঘ জমে অসুরদের ঘরে ঘরে।
আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস বা নষ্ট করার প্রচেষ্টা উচ্চবর্ণকুল চালিয়ে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। তবু কোনও ধর্মবিরোধী তীব্র লড়াই ছিল না এতদিন। অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা বহুবার গর্জে উঠলেও হিন্দু ধর্মকে আঘাত করেনি কখনও। বরং উপজাতিকুল হিন্দু ধর্মকে সবসময় মর্যাদা দিয়ে এসেছে। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গার কাহিনী পরিবেশিত হয়।
আদিবাসীদের আদি পুরুষ হুদুড়দুর্গা তথা মহান রাজা মহিষাসুর বিদেশি আর্য রমণীর দ্বারা অন্যায়ভাবে নিধনের ফলে ভারতের আদিবাসী খেরওয়ালগণ দেশের শাসন ক্ষমতা হারিয়েছিল। সারা দেশে গ্রাস করেছিল বৈদিক সংস্কৃতি। বৈদিক সংস্কৃতির সেই প্রবলতার সামনে সারা ভারতের মূলনিবাসীরা দলিত -অন্ত্যজ- নীচ ইত্যাদি আখ্যা যে লাভ করেছিল তার প্রমাণ আজও মেলে।
বাংলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তীসগড় অন্ধ্রপ্রদেশের যেসব অঞ্চলে ভারতের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার, সেই সব অঞ্চলের জঙ্গল ও পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। সেসব অঞ্চলে এখন অনেক আইনি ও বেআইনি খনি। সংবিধানের পঞ্চম তফসিলকে মানা হয়নি। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করে জঙ্গল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাঁর ভূমিসন্তানদের। বাধ্য করা হয়েছে মহাজনের কাছে জীবন বিকিয়ে দিতে। পাশাপাশি চলেছে জল- জঙ্গল- খনিজ সম্পদ লুঠতরাজ। নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন না থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁরা উগ্র-বামপন্থী মাওবাদী রাজনীতির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অতএব আখ্যা মিলেছে রাষ্ট্রদ্রোহীর!
দেশের অগ্রগতির নামে মৌ চুক্তিতে আদিবাসীদের দেবতা পাহাড়গুলিকে বেচে দেওয়া হল কর্পোরেট সংস্থার কাছে। কারণ এই পাহাড়গুলি থেকে বক্সাইট পাওয়া যায়। ডিনামাইট ফাটিয়ে আসলে তখন আর খনিজ উত্তোলন হচ্ছে না, বামিয়ান বুদ্ধের মতই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার বছরের অস্ট্রিক দেবতাকে।তাঁদের আরাধ্য মারাংবুরুকে চোখের সামনে টুকরো টুকরো হতে দেখছেন আদিবাসীরা। আজ হুদুড় দুর্গার মতই অসহায় মূলবাসীরা। কর্পোরেট সংস্থার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে আগামীতেও হয়ত শহিদ হবেন অনার্য বীরেরা। রচিত হবে নতুন পুরাণ।
@অভিমন্যু মাহাত
ফেসবুক থেকে নেওয়া
Author: Saikat Bhattacharya
Religion Hindu 03-October-2022 by east is risingদ্বিজাতি তত্ত্বের জন্য স্যেকুলারপন্থীরা জিন্নাহ আর মুসলিম লীগকে দায়ী করে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই হিন্দু জাতির ধারণার উদ্ভব হয়। হিন্দু শব্দটা জাতি শব্দের সমার্থক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এই হিন্দুত্বের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন সাভারকার। তিনি “হিন্দু” শব্দকে ডিফাইন করেন এভাবে “He who considers India as both his Fatherland and Holyland” এর মানে “ভারতকে পবিত্রভুমি এবং পিতৃভূমি হিসেবে যারা বিবেচনা করে তারাই হিন্দু জাতি”। Koenraad তার Decolonizing the Hindu mind বইয়ে বলেছেন এই সংজ্ঞা সকল আব্রাহামিক ধর্ম যেমন মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদীদের হিন্দু জাতিসত্বার বাইরে ঠেলে দিল। ধরে নেয়া হল তাঁরা বিদেশী। এই হিন্দু জাতি গঠনের বাইরে যাদের রাখা হল তাদেরকে তো সাভারকারই আলাদা আরেকটা জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হিন্দু জাতির ধারণা প্রতিষ্ঠা করার ফলেই ভারতে তার পাল্টা একাধিক জাতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকুল পরিবেশ গড়ে উঠলো।
এই হিন্দুত্বের জাতিকল্পনাই এক মারাত্মক দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার জন্ম দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম আর জাতি যদি অভিন্ন হয় তাহলে নেপাল বলে তো কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকতে পারেনা। নেপাল, যা হিন্দুপ্রধান একটা দেশ যা ভারত নয় সে তো কোনভাবেই নিজেকে হিন্দু পরিচয় দেয়ার জন্য ভারতকে পিতৃভূমি আর হোলি ল্যান্ড ভাবতে পারেনা। ভারতের সাথে হিন্দু প্রধান নেপালের সমস্যার একটা ঐতিহাসিক সুত্র এখানেও থাকতে পারে। তবে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের সাথে মিলে রাষ্ট্র গঠন এই হিন্দুত্বের সংজ্ঞার জন্য মানসিকভাবে কার্যত খুব জটিল হয়ে যায়। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ভারত রাষ্ট্র একটা সম্ভাবনা হয়ে বিরাজ করতে থাকে।
হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মুল বক্তব্য ছিলো; পৃথিবীতে হিন্দু জাতি বলে বহু প্রাচীন গরিমায় দীপ্ত এক মহান স্বতন্ত্র জাতি আছে। হিন্দু জাতির ধর্ম স্বতন্ত্র, ভাষাও স্বতন্ত্র। হিন্দু জাতি সম্পর্কিত এই ভাবনাই হিন্দুত্বের জন্ম দেয়, যার পলিটিক্যাল এক্সপ্রেশন ছিলো দ্বিজাতি তত্ত্ব, আর সেটাই হয়ে দাড়ায় ভারতভাগের কারণ। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাকবোন।
এদিকে আমরা যদি দেখি মুসলমানদের আলীগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ এমনকি ১৮৮৩ সালেও বলেছেন ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষে বসবাসরত সকলেই “একটি জাতি”। এমনকি এর অনেক পরেও ছিলো জিন্নার মুখে ঐক্যের সুর। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে এক সর্বদলীয় সন্মেলনে বলেন, We are all sons of this land. We have to live together…. Belive me, there is no progress for India until the Musolmans and Hindus are united. আমরা সকলেই এই মাটির সন্তান। আমাদের একসাথেই বাঁচতে হবে…। বিশ্বাস করুন ভারতের কোন অগ্রগতি হবেনা যদি হিন্দু আর মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ না হয়।
১৯৩৭ সালে আহমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার ১৯ তম অধিবেশনে সাভারকার বলেন, “There are two antagonistic nations living side by side in India”, India cannot be assumed today to be a unitarian and homogenous nation. On the contrary, there are two nations in the main: the Hindus and the Muslims, in India…. several infantile politicians commit the serious mistake in supposing that India is already welded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so”
“দুটি পরস্পরবিরোধী জাতি ভারতে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, ভারতকে কখনোই একশিলা সমসত্ব জাতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা। বরং উল্টোভাবে ভারতে প্রধানত দুইটি জাতি; হিন্দু এবং মুসলমান…। কিছু বালকসুলভ রাজনীতিবিদেরা এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা পোষন করে যে, ভারত এরমধ্যেই একটি সুসমসত্ব একটি জাতি হিসেবে তৈরি হয়েছে বা তৈরি করা যেতে পারে।”
এই সভার প্রায় সতেরো বছের আগেই এসেন্সিয়ালস অফ হিন্দুত্ব নামে সাভারকারের একটা পুস্তকে দ্বিজাতি তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। এবং হিন্দুদেরকে একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এই সভার তিন বছর পরে লাহোর অধিবেশনে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সভার জিন্নাহও সাভারকার উত্থাপিত হিন্দু মহাসভার দ্বিজাতি তত্ত্ব গ্রহণ করে।
ঘটনার পরম্পরা বিবেচনা করলে পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে দ্বিতীয় অবদান ভারতীয় মুসলমানদের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দেন সাভারকার তার হিন্দু জাতির তত্ত্ব দিয়ে।
নেহেরু তার অটোবায়োগ্রাফিতেও লিখেছেন “Socially speaking, the revival of Indian Nationalism in 1907 was definitely reactionary” সামাজিকভাবে বলতে গেলে ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল ছিলো।
হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্বের চর্চাই মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার যিনি কোনভাবেই মুসলমান প্রেমী ছিলেন না, তিনিও স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম বইয়ে লিখেছেন, The outburst of Hindu Mohasova served to strengthen the power and influence of Muslim League. “হিন্দু মহসভার বিস্ফোরণই মুসলিম লীগের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলো।”
দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক জিন্নাহ নয়; হিন্দুত্ববাদী সাভারকার। অথচ কি আশ্চর্য ভারত এবং বাংলাদেশের স্যেকুলারেরা এই দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম দেয়ার জন্য জিন্নাহ আর মুসলিম লীগকেই তুলোধোনা করে সবসময়।
Read MoreAuthor: Pinaki Bhattacharya
Historical Hindu 12-September-2022 by east is risingযে পরিকাঠামোটাই বোঝেনা তার কাছে মজবুত পরিকাঠামো আশা করা ভুল।
১। প্রথমে একটা শক্তিশালী সংসার থাকতে হবে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠিকঠাক হতে থাকবে।
২। তারপরে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারার মতো একটা বাহিনী দরকার।
৩। তারপরে এলাকা বৃদ্ধি করার জন্য সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা ও বাহিনী দরকার।
৪। তারপরে নিজেদের দখলে থাকা অঞ্চলে নিজেদের মতো করে ব্যবসা করার বুনিয়াদ বানানো দরকার।
৫। তারপরে অন্য কোন নিরপেক্ষ অঞ্চলে গিয়ে দরকষাকষি করে ব্যবসা করার পরিকাঠামো দরকার।
৬। সব শেষে শক্তিশালী সংস্কৃতি থাকা দরকার যা অন্য জাতিগুলোর কাছে উক্ত জাতি সম্পর্কে ভয়কে ভক্তিতে পরিণত করবে।
বাঙালি মুসলমান সহ বহু তৃতীয় বিশ্বের জাতি আধুনিক যুগে এখনো পর্যন্ত কেবল মাত্র দ্বিতীয় স্তর অবধি যেতে পেরেছে।
একমাত্র মার্কিন জাতিই ষষ্ট স্তরে আছে। হলিউড থেকে শুরু করে গণতন্ত্র, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে অভিবাসী হওয়ার হাতছানিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভক্তিভাব পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষের মধ্যেই আছে।
চীন রাশিয়া পঞ্চম স্তরে আছে আর চীনের পঞ্চম স্তরের বুনিয়াদ রাশিয়ার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই চীন আস্তে আস্তে ষষ্ট স্তরে উন্নীত হচ্ছে। চীনের দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বল্প মূল্যের উন্নত মানের পণ্য, সস্তা ঋণ, দ্রুত প্রযুক্তির উন্নয়ন, উন্নত পরিকাঠামো এবং বিশাল বাজার ক্রমেই চীন সম্পর্কেও বিশ্বের মানুষের মনে ভক্তিভাব জাগাচ্ছে।
ইউরোপ ব্রিটেন ও জাপান চতুর্থ স্তর অবধি যেতে পেরেছে আর পঞ্চম স্তরে যেতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বা রাশিয়ার সাথে বা চীনের সাথে স্বাধীনভাবে দরকষাকষি করার ক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি মার্কিন ও চীন রাশীয়ার বৈরিতার সুযোগ নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই।
লাতিন আমেরিকার দেশগুলো, ইরান, উত্তর কোরিয়া অধিকাংশ আরব দুনিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও চতুর্থ স্তরে আছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মার্কিন ও চীন রাশীয়ার বৈরিতার সুযোগ ভাল মতো নিচ্ছে আর কেউ নিতে পারছেনা।
তুর্কিয়ে চতুর্থ স্তর থেকে পঞ্চম স্তরে উন্নীত হচ্ছে আস্তে আস্তে।
ভারতের নিয়ন্ত্রক জাতিগুলোও (হিন্দি ও গুজারাতি) চতুর্থ স্তরে আছে। তামিল তেলেগু ও শিখরা রয়েছে দ্বিতীয় স্তরে।
বাঙালি হিন্দুদের দ্বিতীয় স্তরটাই নেই। মানে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারার মতো বাহিনীই নেই। অথচ ষষ্ট স্তরের সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে এরা অধিকাংশ সময়টা অতিবাহিত করে। এরা বুঝতেই পারেনা যে এদের সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক কাজের কোন ফলই এরা পাবেনা। কারণ সংস্কৃতি ও গবেষণাকে ক্ষমতায় রূপান্তর করতে গেলে একটা জাতির দরকার যুদ্ধ করার ও ব্যবসা করার পরিকাঠমো ও মানসিকতা। বাঙালি হিন্দুদের যুদ্ধ করার ও ব্যবসা করার পরিকাঠমো ও মানসিকতা কোনটাই নেই। উপরন্তু সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে যুদ্ধ করাকে খারাপ বলে চিহ্নিত করে। ফলে এরা যোদ্ধা পুরুষের পুজো করেনা। নারীর হাতে অস্ত্র দিয়ে, নারীর পায়ে পুরুষকে রেখে তারা যোদ্ধা পুরুষকে ব্যঙ্গ করে। যুদ্ধ করতে পারেনা বলে ব্যবসা করতেও ব্যর্থ হয় আবার বিপদে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনা।
এমনকি প্রথম স্তরেও অর্থাৎ সংসার এবং জন্মহারেও বাঙালি মুসলমান ও হিন্দিদের সাথে বাঙালি হিন্দুরা পাল্লা দিতে পারছেনা। তবে এই সঙ্কট প্রায় সমস্ত জাতির জীবনেই ঘনিয়ে এসেছে আর তাই আলাদা করে এই স্তর নিয়ে এখানে বলা হলনা।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Theoretical Hindu 09-September-2022 by east is risingগত পর্বে পরিলক্ষিত হয়েছিল যে বাঙালী হিন্দু আদতে একটি গোলাম জাতি। এই পর্বে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করব।
বাঙালী হিন্দুর অফিসিয়াল ইতিহাস শুরু হয় ঊনবিংশ শতকে। এটি বাঙালী নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ঊনবিংশ শতকের কতগুলো অতিসাধারণ ব্যাক্তিকে নিয়ে বাঙালী হিন্দু রীতিমত ধর্মীয় কাল্ট বানিয়ে ফেলেছে এবং তাদের নিয়ে কিছু শুনলেই একদম খড়গহস্ত হয়ে ওঠে (যদিও প্রকৃত শত্রু দেখিলে আবার গর্তে ঢোকে)। এই সময়েই নাকী ‘নবজাগরণ’ ও বাঙালী হিন্দুর গব্বের সময়। যদিও 1870 পর্যন্ত কিছু বাঙালী পুঁজিপতির বিকাশ হয়েছিল তবে তা 1870 এরপরে থেকে পিছু হঠতে শুরু করে। আর সব থেকে বড় কথা এইসময়ে বাঙালী হিন্দু ছিল ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন। নিতান্ত আহাম্মক জাতি না হলে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার সময়কে ভালো বলে কোন মুখ্খে। অথচ বাঙালী হিন্দুর ন্যারেটিভটাই হল এমন, আগে আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিলনা, শুধু সতীদাহ আর বাল্যবিবাহ হত, নারীরা খুব অত্যাচারিত হত, আমরা পড়াশুনা করতে জানতামনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের উদ্ধার করে দিয়েছেন। আদতে ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার জন্যে প্রচুর বাবু-কেরানীর দরকার ছিল। সেটি তৈরী করতেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যাবস্থা প্রচার করা হয়েছিল। আর মোগলদের হাতে বাংলার সার্বভৌমত্ব চলে যাবার পরে অনেক অবক্ষয় ঘটেছিল বাংলার, তাই সেগুলির প্রভাব ব্রিটিশ আগমনের সময়েও ছিল। সতীদাহরোধ ও বিধবাবিবাহ চালুর খুব সহজ কারণ দিয়ে দেওয়া যেত জন্মহার বাড়িয়ে ডেমোগ্রাফি শক্তিশালী করার। কিন্তু সেটা না করে হল উল্টো, যেহেতু বাঙালীর মস্তিষ্কে যুক্তিবুদ্ধির বিকাশ হয়নি এবং মূলত আবেগে চলেতাই তার নারী পুজাই শেষ কথা বলল। এবং সে তার নারী পুজাকেই তত্ব বানিয়ে নারীবাদী হয়ে উঠল যার প্রভাবে ধীরে ধীরে ডেমোগ্রাফিকালি দূর্বল হতে শুরু করল। এছাড়াও যেহেতু ঊনবিংশ শতক থেকেই বাঙালীর ভূমিকা ছিল মূলত বাধ্য চাকর হিসাবে, ফলে গোলামিও বাঙালীর মজ্জাতে ঢুকে গেল। এছাডাও বাঙালী স্বভাবতই নিশ্চিত জীবন চায় এবং স্থিতাবস্থা চায়। ফলত পরাধীনতায় সুরক্ষিত থাকাকেই তারা বেছে নিল। এইভাবে বাঙালী ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড খুইয়ে নতমস্তক ক্রীতদাসে পরিণতহল। সমসাময়িক বাঙালীর তথাকথিত আইকনদের রচনাতেও বাঙালীর গোলাম হওয়াকেই মোক্ষ বলেছেন। ‘সুবোধবালক’ হওয়া থেকে ‘ভারতের মহামিলনের তীর্থে’ বিলীন হওয়ার মাধ্যমে বাঙালী হিন্দু একটি আপাদমস্তক গোলাম জাতি তৈরী হল। বাংলা সাহিত্যে ও বিজাতীয়দের নায়ক ও বাঙালী শাসকদের খলনায়ক বানিয়ে হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেওয়া হল।
অথচ বাঙালী হিন্দু যখন রাজনৈতিক ধাক্কা খেল, দেশভাগে বিপর্যস্ত হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিহার সবেতেই কচুকাটা হল তখন কিন্তু এই কবিতা, গদ্য, সাহিত্যের ঝুড়ি ঝুড়ি জ্ঞান তাদের বাঁচাতে আসেনি। বাঙালী হিন্দু যে শশাঙ্ক, দেবপালদের বিস্মৃত করে দিয়েছিল তার মাসুল দিতে হল।
বর্তমানেও বাঙালী হিন্দু একটি গোলাম গোষ্ঠী এবং এটাই আশা করে যে রাষ্ট্র তাদের ঢেলে ঢেলে চাকরি দেবে এবং স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নিশ্চিন্তে মধ্যবিত্তের জীবন কাটাবে। এর ফলে ভৃত্য হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
বাঙালী হিন্দুর নেতা ও সেই হয় যে আরামে নিরাপদে বসে ফাঁকায় বুলি ঝাড়বে এবং অন্যদের বিনামূল্যে গাড্ডাতে ফেলবে। বিপদ আসলে সেই নেতাই চম্পট দেয়।
এর কারণ বাঙালি হিন্দু মেরুদণ্ডযুক্ত পুরুষকে সহ্য করতে পারেনা। ফলে ভেড়ুয়া ও ধান্দাবাজরাই দখল নেবে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যাক্তিস্বার্থ গোছাবে।
ভারতের সকল জাতিই ইতিহাস সচেতন কেবল বাঙালী বাদে। এর ফলে বাঙালী অন্য জাতির কাছে ভ্যালিডেশন খোজে ও তাদের সাথে একাত্ম হতে চায়। কিন্তু ছিন্নমূল চাকরদেরকে পাত্তা দেবে।
যে নিজেকে সম্মান করে না, যার মেরুদণ্ড সোজা নয়, যে টিকে থাকার জন্যে পরনির্ভর, যে সর্বদাই অপরকে তুষ্ট করাকে মোক্ষ ভাবে তার কপালে তো ভোগান্তি আছেই।
Read MoreAuthor: Purandhar Khilji
Historical Hindu 19-August-2022 by east is risingআম্রপালী ছিলেন এমন একজন অনিন্দ্য সুন্দরী ; প্রায় ২,৫০০ বছর আগে রাষ্ট্র যাকে বানিয়েছিল নগরবধূ বা পতিতা-
স্বাদের দিক থেকে অনেকের কাছেই 'আম্রপালী' আম খুবই প্রিয় । আকারে ছোট কিন্তু মিষ্টির দিক থেকে যেন সকল আমকে পিছনে ফেলে দিয়েছে 'আম্রপালী' । কিন্তু এই আমটার নামকরণ কোথা থেকে হল জানেন ?
আম্রপালী জন্মেছিলেন আজ থেকে ২,৫০০ বছর আগে ভারতে । তিনি ছিলেন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং নর্তকী । তার রুপে পাগল ছিল পুরো পৃথিবী আর এই রুপই তার জন্য কাল হয়ে ওঠে । যার কারণে তিনি ছিলেন ইতিহাসের এমন একজন নারী, যাকে রাষ্ট্রীয় আদেশে পতিতা বানানো হয়েছিল !
আম্রপালী বাস করতেন বৈশালী শহরে । বৈশালী ছিল প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক একটি শহর, যেটি বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যের অর্ন্তগত ।
মাহানামন নামে এক ব্যক্তি শিশুকালে আম্রপালীকে আম গাছের নিচে খুঁজে পান । তার আসল বাবা-মা কে ইতিহাস ঘেঁটেও তা জানা যায়নি । যেহেতু তাকে আম গাছের নিচে পাওয়া যায় তাই তার নাম রাখা হয় আম্রপালী । সংস্কৃতে আম্র মানে আম এবং পল্লব হল পাতা । অর্থাৎ, আমগাছের নবীন পাতা ।
কিন্তু শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিতেই আম্রপালীকে নিয়ে হইচই পড়ে যায় । তার রুপে চারপাশের সব মানুষ পাগল হয়ে যান । দেশ-বিদেশের রাজপুত্রসহ রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে যান । নানা জায়গায় থেকে তাকে নিয়ে দ্বন্দ, ঝগড়া আর বিবাদের খবরও আসতে থাকে । সবাই তাকে একনজর দেখতে চান, বিয়ে করতে চান । এ নিয়ে আম্রপালীর মা-বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন । তারা তখন বৈশালীতে সকল গণমান্য ব্যক্তিকে এর একটি সমাধান করার জন্য বলেন । কারণ, সবাই আম্রপালীকে বিয়ে করতে চান । তখন বৈশালীর সকল ক্ষমতাবান ও ধনবান ব্যক্তি মিলে বৈঠকে বসে নানা আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত নেন তা হল, আম্রপালীকে কেউ বিয়ে করতে পারবেন না । কারণ তার রুপ । সে একা কারো হতে পারে না । আম্রপালী হবে সবার । সে হবে একজন নগরবধু, মানে সোজা বাংলায় পতিতা ।
এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত । ইতিহাসে এভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে কাউকে পতিতা বানানো হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত খুবই বিরল ! আম্রপালী সে সভায় পাঁচটি শর্ত রাখেন-
(১) নগরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় তার ঘর হবে ।
(২) তার মুল্য হবে প্রতি রাত্রির জন্য পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা ।
(৩) একবারে মাত্র একজন তার গৃহে প্রবেশ করতে পারবেন ।
(৪ ) শক্র বা কোন অপরাধীর সন্ধানে প্রয়োজনে সপ্তাহে সর্বোচ্চ একবার তার গৃহে প্রবেশ করা যাবে ।
(৫) তার গৃহে কে এলেন আর কে গেলেন- এ নিয়ে কোন অনুসন্ধান করা যাবে না ।
সবাই তার এসব শর্ত মেনে নেন । এভাবে দিনে দিনে আম্রপালী বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন । তার রুপের কথাও দেশ-বিদেশে আরও বেশী করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ।
প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিম্বিসার । শোনা যায়, তার স্ত্রীর সংখ্যা নাকি ৫০০ ছিল ! নর্তকীদের নাচের এক অনুষ্ঠানে তিনি এক নর্তকীর নাচ দেখে বলেছিলেন, এ নর্তকী বিশ্বসেরা ।
তখন তার একজন সভাসদ বলেন- মহারাজ, এই নর্তকী আম্রপালীর নখের যোগ্য নয় !
বিম্বিসারের এই কথাটি নজর এড়ায়নি । তিনি তার সেই সভাসদের থেকে আম্রপালী সম্পর্কে বিস্তারিত শুনে তাকে কাছে পাবার বাসনা করেন ।
কিন্তু তার সভাসদ বলেন, সেটা সম্ভব নয় । কারণ, তাহলে আমাদের যুদ্ধ করে বৈশালী রাজ্য জয় করতে হবে আর আম্রপালীর দেখা পাওয়াও এত সহজ নয় । দেশ-বিদেশের বহু রাজাসহ রাজপুত্ররা আম্রপালীর প্রাসাদের সামনে তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন । কিন্তু মন না চাইলে তিনি কাউকে দেখা দেন না ।
এত কথা শুনে বিম্বিসারের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল । তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ছদ্মবেশে বৈশালী রাজ্যে গিয়ে আম্রপালীকে দেখে আসবেন । কি এমন আছে সেই নারীর মাঝে, যার জন্য পুরো পৃথিবী পাগল হয়ে আছে !
তারপর বহু চড়াই উৎরাই শেষে তার আম্রপালীর সাথে দেখা করার সুযোগ আসে । আম্রপালীর প্রাসাদ আম্রকুঞ্জে । কিন্তু দেখা করতে গিয়ে রাজা চমকে উঠেন, এত কোন নারী নয় ; যেন সাক্ষাৎ পরী ! এ কোনভাবেই মানুষ হতে পারেন না । এত রুপ মানুষের কিভাবে হতে পারে !
কিন্তু অবাক রাজার জন্য আরও অবাক কিছু অপেক্ষা করছিল । কারণ, আম্রপালী প্রথম দেখাতেই তাকে মগধ রাজ্যের রাজা বলে চিনে ফেলেন এবং জানান- তিনি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন বহু আগে থেকেই ।
এই কথা শুনে রাজার বিস্ময়ের সীমা থাকে না ।
রাজা সাথে সাথে তাকে তার রাজ্যের রাজরাণী বানানোর প্রস্তাব দেন । কিন্তু আম্রপালী জানান, তার রাজ্যের মানুষ এটা কখনোই মেনে নেবেন না । উল্টো বহু মানুষের জীবন যাবে । রক্তপাত হবে । তাই রাজাকে দ্রুত এখান থেকে চলে যেতে বলেন ।
কিন্তু বিম্বিসার বৈশালী আক্রমন করে আম্রপালীকে পেতে চান । ওদিকে আম্রপালী তার নিজের রাজ্যের কোন ক্ষতি চান না । তাই তিনি রাজাকে তার নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠান এবং বৈশালীতে কোন আক্রমণ হলে তিনি তা মেনে নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন ।
এদিকে বিম্বিসারের সন্তান অজাতশত্রুও আম্রপালীর প্রেমে মগ্ন ছিলেন । তিনি বিম্বিসারকে আটক করে নিজে সিংহাসন দখল করে বসেন এবং আম্রপালীকে পাওয়ার জন্য বৈশালী রাজ্য আক্রমণ করে বসেন । কিন্তু দখল করতে সক্ষম হননি এবং খুব বাজেভাবে আহত হন । পরবর্তীতে আম্রপালীর সেবায় সুস্থ হয়ে গোপনে তার নিজের রাজ্যে ফেরত যান । সেদিনও আম্রপালী অজাতশত্রুর বিয়ের প্রস্তাব সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন ।
এত নাটকীয়তার পর শেষের দিকে এসে কি হল ? গৌতম বুদ্ধর সময়কাল তখন । গৌতম বুদ্ধ তার কয়েকশ সঙ্গী নিয়ে বৈশালী রাজ্যে এলেন । একদিন বৈশালী রাজ্যের রাবান্দা থেকে এক বৌদ্ধ তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে আম্রপালীর মনে ধরে গেল । তিনি ভাবলেন, দেশ-বিদেশের রাজারা আমার পায়ের কাছে এসে বসে থাকেন আর এত সামান্য একজন মানুষ । তিনি সেই সন্ন্যাসীকে চার মাস তার কাছে রাখার জন্য গৌতম বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন । সবাই ভাবলেন, বুদ্ধ কখনই রাজি হবেন না । কারণ, একজন সন্ন্যাসী এমন একজন পতিতার কাছে থাকবেন ; এটা হতেই পারে না । কিন্তু গৌতম বুদ্ধ তাকে রাখতে রাজি হলেন এবং এটাও বললেন, আমি শ্রমণের (তরুণ সে সন্ন্যাসীর নাম ছিল) চোখে কোন কামনা-বাসনা দেখছি না । সে চার মাস থাকলেও নিষ্পাপ হয়েই ফিরে আসবে- এটা আমি নিশ্চিত !
চার মাস শেষ হল । গৌতম বুদ্ধ তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে যাবেন । তরুণ শ্রমণের কোন খবর নেই । তবে কি আম্রপালীর রুপের কাছেই হেরে গেলেন শ্রমণ ? সেদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে তরুণ শ্রমণ ফিরে আসেন । তার পিছনে পিছনে আসেন একজন নারী । সেই নারীই ছিলেন আম্রপালী । আম্রপালী তখন বুদ্ধকে বলেন, তরুণ শ্রমণকে প্রলুব্ধ করতে কোনও চেষ্টা বাকি রাখেননি তিনি । কিন্তু এই প্রথম কোন পুরুষকে বশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বৈশালীর নগরবধূ আম্রপালী । তাই আজ সর্বস্ব ত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় চান তিনি ।
পরে সব কিছু দান করে বাকী জীবন গৌতম বুদ্ধের চরণেই কাটিয়ে দেন ইতিহাস বিখ্যাত সেই রমণী আম্রপালী আর এই আম্রপালী নামেই ১৯৭৮ সালে ভারতের আম গবেষকরা 'দশোহরি' ও 'নিলাম'- এই দু'টি আমের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে এক নতুন জাতের আম উদ্ভাবন করেন এবং নাম রাখেন 'আম্রপালী' ।
Collected From Facebook by Anonymous Writer
Author: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 17-August-2022 by east is risingবাঙালী হিন্দুর সঠিক বিকাশ হয়নি সে নিয়ে গত পর্বেই আলোচনা করছি।এই পর্বে আরো গভীরে যাব এবং দেখব কীভাবে বাঙালী হিন্দুর কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে।
বাঙালী হিন্দু হল কূপমণ্ডুক গোষ্ঠী। ছোট্ট সংসার, পাড়া, অফিস-কাছাড়ি এই নিয়েই তার জীবন।তার ফলে এর বাহিরে সে দুনিয়া দেখতে পারেনা। এছাড়া সে সর্বদাই তার এই ক্ষুদ্রজগতে কূপমণ্ডুকের ন্যায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং একেই দুনিয়া হিসাবে মানে। এই ক্ষুদ্র জগতের বাইরে সম্পর্ক গড়তেও সে অনিচ্ছুক। তাই বৃহৎ জগত কেউ ওয়াকিবহল থাকেনা।ফলত তার জীবনের কোন পরিবর্তন হয়না। কূপমণ্ডুক হবার কারণে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও আত্মকেন্দ্রিকও হয়, ফলত এরা নিজেদের দল বাড়াতে তো পারেইনা উল্টে খেয়োখেয়ি করে আরো ছোট হয়।যদি যে কোন বাঙালী সংগঠনকে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তারা ক্রমাগত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট দল তৈরী হচ্ছে।বাঙালী হিন্দু জুড়ে বড় হতে পারেনা, ভেঙ্গে ছোট হতে জানে। এর কারণ হিসাবে বাঙালী হিন্দুর উত্তরাধিকার ব্যাবস্থাও দায়ী, পৈতৃক সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে ক্রমাগত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে হতে শেষে কিছুই থাকেনা।যেহেতু তারা কূপমণ্ডুক ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাই এগুলিকে অবলীলায় স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেয়।
যেহেতু তারা কুয়োর জগতে পড়ে থাকে তাই নিজেদের বর্তমান অবস্থা কী, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, কীভাবে অবস্থার উন্নতি করে যায়, দুনিয়াটা কি সেই বিষয়ে কোন বোধই গড়ে ওঠেনা।
এছাড়াও কূপমণ্ডুকতার কারণে তারা কূটনৈতিক, রাজনৈতিক জোট বা মিত্রতা গড়তে পারেনা। কে শত্রু ও কে বন্ধু এই বোধ আসেনা। কার সঙ্গে লড়া উচিত কার সঙ্গে নয়, এই বোধ না থাকার কারণে দিনের শেষে বাঙালী হিন্দু একা হয়ে যায়। আবেগে ভেসে অনেকে অগ্নিযুগের বিপ্লবী থেকে নক্সাল হতে যায় এবং দিনের শেষে তার পরিণাম আরো ভয়ঙ্কর হয়।
বাঙালী হিন্দু সংগঠিতই হতে পারেনা, তো একা লড়ে কিছু আদায় করা তো দূর, ভোগান্তি ছাড়া কিছু আসেনা।এরা কারুর সাথে সখ্যতা তৈরী না করে সবার সাথেই বৈরীতা তৈরী করে ফেলে এবং সকলের চক্ষুশূল হয়।বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে এটাই বোঝা যায় যে বাঙালী হিন্দুর কোন মিত্রই নেই এবং যেই সুযোগ পায় সে এসে অবলীলায় সর্বনাশ করে যায়।
আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাঙালী হিন্দুর পরিচয়হীনতা। কোন বাঙালী হিন্দুই জানেনা সে নিজে কে? কেউ বলবে আমি বিশ্বমানব, কেউ আগে মানবতাবাদী, কেউ হয় ভারতীয়, কেউ বিশ্বহিন্দু, কেউ রাবীন্দ্রীক বাঙালী, ইত্যাদি।অর্থাৎ বাঙালী হিন্দু নিজেই জানেনা তার পরিচয়। অথচ শত্রুর কাছে সে বাঙালী বা বাঙালী হিন্দু হিসেবেই চিহ্নিত হয় ও আক্রমণের শিকার হয়। পরিচয় না গড়ে ওঠারও মূল কারণ হল কূপমণ্ডুকতা এবং ঐতিহাসিক বিকাশ না হওয়া।ফলত নিজের ক্ষুদ্র জীবনের নাগপাশেই আবদ্ধ হয়ে থাকে ও বৃহৎ দৃশ্যটি দেখতে অক্ষম।
নানা ভাবে ও রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী উলু বনে শেয়াল রাজা হয়ে উঠেছে।এই শ্রেণীর সহযোগীতাতে বাকী বাঙালী বিশেষত পুঁজিপতি, উৎপাদক, সংগঠক শ্রেণীদের শেষ করে দেওয়া হয়েছে।বাঙালী গরীবদেরকেও তুষ্ট করে তাদের উচ্চাকাঙ্খাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।তাছাড়া বাঙালী হিন্দুর অন্তর্নিহিত ঈর্ষা ও উলু বনে শেয়াল রাজা থাকার বাসনা সমস্ত সম্ভাবনাময় বাঙালীকে ধ্বংস করে দিয়েছে।ফলে আপৎকালে বাঙালীর রক্ষাকর্তার কোন উদয় হয়নি। যেহেতু এরা কূপমণ্ডুক ও তাই অকারণেই হাম্বড়া। এরা মধ্যবিত্ত জীবনটাকেই স্বর্গসুখ ভাবে।
আবার এই চাকরীজীবী শ্রেণী তো সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর। ফলে এরা টিকে থাকার জন্যে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর।ফলত এরা রাষ্ট্রের বাধ্য ক্রীতদাস।ভারত রাষ্ট্র বাঙালীর নয় সেই বোধটাও বিকাশ হয়নি কারণ ইহাদের কাছে সরকারী চাকুরে বা আইটি কুলি হওয়ার মতো মোক্ষ আর নেই।ফলত বাঙালী হিন্দুই ভারত রাষ্ট্রের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য দেখায় যদিও ভারত রাষ্ট্র প্রথম থেকেই বাঙালী হিন্দুর পেছনে আছোলা বাঁশ দিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে তা নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা আছে। ভারতের বাকী জাতিরা রাষ্ট্রের সাথে দরকষাকষি করে নিজেদেরটা বাগিয়ে নেয় কিন্তু বাঙালী হিন্দুর সেই মুরোদ নেই। এতেও বাঙালী হিন্দুর পশ্চাদপদতা বোঝা যায়।
জয়ন্ত ভাণ্ডারী বা প্রবীণ সাহনি ভারতের শাসক জাতিরই ব্যাক্তি। একজন পশ্চিম ভারতীয় জৈন ও অপরজন পাঞ্জাবী হিন্দু। কিন্তু তা সত্বেও এরা ভারতকে তুলোধোনা করতে পিছপা হয়না।অথচ বাঙালী হিন্দু রাষ্ট্রের থেকে কিছু পায় তো নিই বরঞ্চ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।তাতেও বাঙালী হিন্দুই ভারত রাষ্ট্রের প্রতি শর্তহীনভাবে সিজদা করে চলেছে এবং আজকেও কোন বাঙালী জয়ন্ত ভাণ্ডারীর হদিশ পেলামনা।
উপসংহার হিসেবে এটাই বলতে হয় যে মোটের উপর বাঙালী হিন্দু একটি পশ্চাৎপদ গোলাম জাতি এবং আদৌ স্বশাসনের যোগ্যতা যে নেই তাও বলা যায়।এই অবস্থার দ্রুত বদল হতে হবে নয় বাঙালী হিন্দুর ঠাঁই যাদুঘরেও হবেনা।অথচ মরণকালেও বোধোদয় হয়নি এবং মুষ্টিমেয় কিছু দূরদর্শী বাঙালী হিন্দু যারাই অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে তারাই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে স্বজাতির থেকে। তা সত্বেও তাদের শুভকামনা জানিয়ে আমার লেখা শেষ করলাম।
Read MoreAuthor: Purandhar Khilji
Historical Hindu 17-August-2022 by east is rising"বাঙ্গালীদের শারীরিক গঠন মেয়েলি ও ভঙ্গুর বলা চলে। এরা বাষ্পস্নানে অভ্যস্থ। নির্জনতা প্রিয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অশক্ত, চলাফেরা নিস্তেজ ও নির্জীব। যুগের পর যুগ তারা বিদেশী শাসকদের দ্বারা পদদলিত হয়েছে। ক্ষীণ দেহ বলে এরা সাহস রাখে না, স্বাতন্ত্র্যবোধ এদের নেই এবং এরা কখনো সত্যবাদী হয় না। এদের মন ও দেহ অভিন্ন। এরা পুরুষোচিত প্রতিরোধে অপারগ, দুর্বল দেহের জন্য অসহায়বোধ করে। কিন্তু এদের নমনীয়তা ও চাতুর্য প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই প্রাপ্য। বস্তুত ভিন্ন জলবায়ুর লোকেরা এদের যেমন ভক্তি করে, তেমনি ঘৃণা করে। একটা দূর্বল জাতির আত্মরক্ষার্থে যেসব কৌশল প্রয়োজনে অবলম্বন করতে হয় তার সবগুলি এদের জানা আছে। জুভেনালের সময় আওনীয়দের কিংবা মধ্যযুগে ইহুদিদেরও এত কৌশল জানা ছিলো না। মহিষের কাছে সিং-এর যে মূল্য, বাঘের কাছে থাবার যে গুরুত্ব, মৌমাছির যেমন হুল, পুরনো গ্রীক কবিতা অনুসারে নারীর জন্য সৌন্দর্য যা, বাঙালির কাছে প্রতারনা সেরকম মূল্যবান। এরা লম্বা- লম্বা প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার সুন্দর অজুহাত দেখায়, প্রতারনা, মিথ্যা হলফ, জালিয়াতি এসব তারা আত্মরক্ষার্থে কিংবা অন্যের ক্ষতি করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। গাঙ্গেয় নিম্নাঞ্চলের লোকদের স্বভাবই এরকম। বঙ্গে কয়েক মিলিয়ন বাঙালি বাস করে। অথচ এদের একজনও কোম্পানির সেনা বিভাগে নাম লেখায়নি। কিন্তু সুদের ব্যবসা, পোদ্দারি এবং মোক্তারিতে প্রতিযোগিতায় কোন জাতি এদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আবার বাঙ্গালীরা নমনীয় চরিত্রের হলেও এদের মতো নির্দয় ও অদম্য শত্রু অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এরা মানুষের প্রতি করুণাশীল হতে জানে না। স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে লেগে থাকতে জানে এবং বিপদের আশঙ্কা দেখা না দিলে ক্ষান্ত হয় না।"
এরকম আরও গুন বচন পড়তে চাইলে আগ্রহীরা দেখতে পারেন-
Memories of the life of Warren Hastings, first Governor-General of Bengal By Lord Macle, London: 1841.
লেখক মনে করে মেকলে সাহেব ঠিকই বলেছেন মূলত বাঙালি হিন্দু সম্পর্কে। বাঙালি মুসলমানদের ধরলে চরিত্র অনেকটাই আলাদা হবে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মিলেও যাবে। কিন্তু লেখক মনে করে বাঙালি হিন্দুদের যে ভাল গুণগুলো মেকলে তুলে ধরেছে যেমন ব্যবসা করার ক্ষমতা বা কোন বিষয় বিপদ না থাকলে লেগে থাকার ক্ষমতা তা উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের বাঙালি হিন্দুদের জন্যেই প্রযোজ্য। উনবিংশ শতকের শেষভাগের, বিংশ শতাব্দীর, এবং বিশেষ করে বর্তমান সময়ের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ব্যবসা করার ক্ষমতা বা কোন বিষয় লেগে থাকার ক্ষমতা একেবারেই নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং গায়ের জোড় ও সাহসের কমতি চাতুর্য দিয়ে ও ধৈর্য দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করত।
লেখক মনে করে বঙ্কিম চন্দ্রের লেখনীর সময় থেকে মানে ১৮৬৬ সাল থেকে বাঙালি হিন্দু নিজেদের দুর্বলতাকে রাজপুত ও মারাঠা সাহসিকতার গল্প (অধিকাংশেই যা ছিল মিথ্যা) দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেছে। এভাবেই বাঙালি হিন্দু রাজপুত ও মারাঠাদের (যারা অতীতে বাঙালি হিন্দুদের লুট করতে আসত এবং শত্রু বলে অভিহিত হত) নিজেদের আরাধ্য বানিয়েছে এবং হিন্দু জাতিয়তা ও ভারতীয় জাতিয়তার দিকে গাঁ ভাসিয়েছে। গিতা পড়ে বম্ব বেঁধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে লড়াই করতে গেছে। আসলে মনে মনে নিজেকে হীন মনে করে সেই হীনতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে গেছে। সাম্রাজ্যের সাথে লড়ে স্বাধীন রাষ্ট্র বানাবার অর্থ কি তা বাঙালি হিন্দু বোঝেনি আর তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন শেষ হল বাঙালি হিন্দুরা তখন উদ্বাস্তু হল আর হিন্দিভাষীদের গোলামে পরিণত হল।
Author: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 06-August-2022 by east is risingবাঙালী হিন্দু অধুনাযুগে তিন বার বড় ধাক্কা খায়- 1870, 1910-1920 ও 1945-47 এ। সে সব নিয়ে আগের পর্বেই কথা হয়েছে। এইপর্বে 1947 পরবর্তীকাল বিশ্লেষণ করা হবে।
1870 থেকেই বাংলার বিভিন্ন অংশকে কেটে ছেঁটে অন্যপ্রদেশে দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। দেশভাগ হবার পরেও তাবলবৎ থাকে। 1956 এর ভাষিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময়ে শুধুমাত্র মানভূমভাষা আন্দোলনের কারণে পুরুলিয়া পায়, বাকি অংশটি বিহারেই থাকে। সেই সব অঞ্চলে ধীরে বাংলা নিশ্চিহ্ন হয়।আসামের বরাকে ভাষা আন্দোলের মাধ্যমে বাংলা থাকলেও গোয়ালপাড়া অঞ্চল থেকে পুরোপুরি বাংলা নিশ্চিহ্ন হয়। তাছাডা আসামে বঙ্গাল খেদা, মেঘালয়ে, ত্রিপুরাতে বাঙালী গণহত্যা, বিহারে, উড়িষ্যাতে বাঙালী বিরোধী আন্দোলন হয়।ফলে পশ্চিম বঙ্গের বাইরে ভূমিপূত্র বাঙালী কোনঠাসা হয় ও ভারতীয় বাঙালী বিশাল এলাকা হারায়।খোদ পশ্চিম বঙ্গেই নেপালের সাথে উন্মুক্ত সীমান্তের দরুণ দার্জিলিং পর্বতে বাঙালীর এথনিক ক্লিনজিং হয় এবং বর্তমানে সেই ধারা অব্যাহত।এছাড়া উত্তর বঙ্গ থেকে রাঢ় বাংলা থেকে ত্রিপুরা সকল জায়গতাতেই বাঙালী বহিরাগত ও উপজাতি ভূমিপুত্রের জিগির তুলে ক্রমাগত বাঙালী উপরে নির্যাতন হয়।
দেশভাগের ফলে নিঃস্ব বাঙালী উদ্বাস্তু বৈষম্যের শিকার হয়।পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বৈষম্যমূলক নীতি নেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ ভারতে এসে ফুলেফেঁপে ওঠে।কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী উদ্বাস্তুদের (অবাঙালীদের ক্ষেত্রে উল্টো নীতি নিয়েছিল) বহিরাগত দাগিয়ে জাতিগত বৈষম্য, হিংসার স্বীকার হয়।
উপরন্তু খোদ পশ্চিম বঙ্গেই বাঙালীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানানো হয়। আদতেই এই আধা রুটির টুকরোর মত ভিক্ষা দেওয়ার জন্যই কোন বাঙালী হিন্দু হোমল্যাণ্ড হিসেবে তৈরী হয়নি। এটি মূলত মারোয়ারীদের স্বার্থেই বানানো হয়েছে। ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া বেনামী সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে মারোয়ারীরা দখল করে।এছাড়া রাষ্ট্রীয় মদতেই বাঙালী পুঁজি ধ্বংস হয়। নক্সাল দমনের নামে তরুণ বাঙালীদের হত্যা করে শেষ মেরুদণ্ডটিও ভাঙে।এরপর বামেদের হাত ধরে মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্রমালিক এই দুটি দালাল বাঙালী শ্রেণীর হাত ধরে সম্পূর্ণ রূপে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতে। সকল রাজ্য তাহার নিজের জাতির জন্যেই সুরক্ষিত কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ হয় মুক্তঞ্চল।ফলে চুড়ান্তভাবে একপাক্ষিক সম্পর্কে আটকা পড়ে বাঙালী।
এইভাবে ধীরে ধীরে বাঙালী হিন্দুর অন্তরায় ঘনিয়ে আসে।
এত কিছুর পরেও বাঙালী হিন্দু কিচ্ছু করতে পারলনা কেন? দক্ষিণীদের মতো নিজেদের আখের গোছালোনা কেন? উত্তর জানতে পরের পর্বের অপেক্ষা করতে হবে।সেখানে বাঙালী হিন্দুর সম্পূর্ণ পোস্টমর্টেম হবে এবং কীভাবে বাঙালী মুসলমান এই সংকট আটকালো সেটাও তারপরের পর্বে বিশ্লেষণ হবে।
Read MoreAuthor: Purandhar Khilji
Historical Hindu 14-June-2022 by east is risingবাঙালী হিন্দু বিশ্বের সব থেকে পশ্চাৎপদ জাতগুলির মধ্যে পড়ে। বাঙালী হিন্দুর বিবর্তন তাম্রযুগ অবধি।subsistence farming , ঘরোয়া সংসারকেন্দ্রিক জীবন, পাড়া গাঁই জগৎ এইভাবেই বাঙালী হিন্দু গড়ে উঠেছে। ফলেনগর সভ্যতা, কৌমচেতনা, সমষ্টিগঠন, বাণিজ্য, শিল্প, রাষ্ট্রচেতনা এসবের বিকাশ হয়নি।এছাড়াও নারী পুজারী হবার কারণে পৌরুষের বিকাশ ঘটেনি। ফলেসাহস, সততা, শক্তি, বিজয়, সম্প্রসারণ, প্রাচুর্য, মূল্যবোধ, সামাজিককাঠামো, ন্যায়বোধ এসব পুরো ভিনজগতের ধারণা।এগুলি সমস্ত ভারতীয়দের জন্যে প্রযোজ্য হলেও বাঙালী হিন্দু আরো পেছনের সারিতে কারণ এরা দল বানাতেই পারেনা। বাকী ভারতীয়দের মতো দল বানিয়ে রাষ্ট্রের থেকে কিছু আদায় করতে পারেনা, পয়সা কড়ি করতে জানেনা বরং যেটা করে তা হল নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি, হিংসা হিংসি।যদু বংশকে শেষ করতে বহিঃশত্রু লাগেনা।
বাঙালী হিন্দুই বোধহয় একমাত্র জাতি যেখানে মধ্যবিত্তকে এলিট বলে দেওয়া হয়।কারণ এদের কাছে ওটাই বিশাল পাওনা। তাছাড়া ঈর্ষাতে তাহার জুড়ি মেলা ভার।এই জাতির পুরুষদের চরিত্রও পুরো নারীদের মতো (ইহা যদিও সকল ভারতীয়র জন্যেই প্রযোজ্য, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর ক্ষেত্রে তা অন্যমাত্রা ধারণ করে)। এর জন্যে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে কোন আকাঙ্খাই নেই। খাদ্য, বাসস্থান, সংসার হলেই তার যথেষ্ট এবং মূলত একটা ঘোরের জগতে দিবাসপ্ন দেখে বাকিটা কাটায়।তার ফলে ক্রমাগত তার পশ্চাৎদেশে একটার পর একটা আছোলা বাঁশ ঢুকলেও সে কোনরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুজলেই যথেষ্ট মনে করে। ফলে ক্ষমতা, অর্থ, শক্তি, সুখ সব কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত।আর নিজেদের মধ্যেই মারামারি করা এদের জন্মজাত। ফলে এদের বিনাশ আটকানো সম্ভব হয়নি।
একটা বাজারি কথা খুব প্রচলিত যে কলকাতার এলিটরা না কী জেলাকে বঞ্চনা করছে!!!! এই বোকাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই এলিট কারা তখন তারা অঙ্গুলি দেখাবে শহরতলিতে থাকা মধ্যবিত্তের দিকে।অথচ কলকাতার এলিট আদতে তো গুজরাটী, মারোয়ারীরা। বাঙালী কে কীভাবে এলিট বলবো?এটা যাদের চোখে পড়েনা তারা বোকা ছাড়া আর কি? কলকাতাতে এসে দুনিয়ার লোক ফুলেফেঁপে ওঠে অথচ এই জেলা থেকে আসা বাঙালিরা বঞ্চিতহয়। কলকাতা তো দুরহস্ত, এখন হুগলী শিল্পাঞ্চল, হাওড়া, শিলিগুড়ি, খড়গপুর, আসানশোল, দূর্গাপূর সব বাঙালীর হাতছাড়া। অর্থাৎ এরা শহরাঞ্চল দখলে রাখতে অপটু কারণ নগর সভ্যতাতে এরা পৌঁছয়নি।উল্টে পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি সব মায়ের ভোগে পাঠিয়েছে। পারিবারিক বিবাদ, পড়শীর বিবাদ, শরীকী বিবাদ করে সব সম্পত্তি খুইয়েছে, পৈত্রিক সম্পত্তি বেচে খেয়ে উড়িয়েছে।
এই একটা উদাহরণ দিয়েই বোঝা যায় যে এদের বিকাশ কতটা নিম্নে যে এরা কিছুই ধরে রাখতে অপারগ।
আবার পেছনে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপকরা, পেছনে লাগা, কাঠি করার মতো অসভ্য জংলীপনা ও এদের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।
এবার দেখা যাক এদের নারীপূজার উন্মাদনা। বাঙালী হিন্দু নারী নামেই পাগল, দিগ্বিদিকশূণ্য।হতদরিদ্র জাতি হয়েও এরা মেয়েদের জন্য টাঁকশাল উন্মুক্ত করে দেবে। ফলে ছেলেগুলোকে ছোটবেলা থেকে গবাদীপশু বানাতে লাগে।বাল্যকাল থেকেই এরা মেয়েদের শিক্ষা দেয় যে তুমি আলালের ঘরের দুলালী, তাই আজীবন মাগনাতে অন্যের অর্থে ফুটানী করবে। আর ছেলেদের শিক্ষা দেয় যে একদম মেরুদণ্ডহীন ক্লীবলিঙ্গ হয়ে অন্যের খ্যাঁটনের যোগান দেবে, তোমার মানুষ হিসাবে কোন জীবন থাকবেনা এবং এর জন্যে তোমাকে সারা জীবন ইঁদুরদৌড় করে যেতে হবে।ফলে এদের মেয়েগুলিকে একদিকে সাপের পাঁচপা দেখে আর ছেলেগুলির জীবন বলেই কিছু থাকেনা, পুরোপুরী নারীসুলভ, স্তাবক, ভীরু, অসামাজিক, কাঠিবাজ, হিংসুটে, কুচুটেপ্রকৃতির। এর ফলে এরা কোন সমষ্টিই বানাতে পারেনা।
এদের বৃদ্ধগুলি আরেক বিষ। এদের মানসিকতা হল এদের পরবর্তী প্রজন্মহল এদের বৃদ্ধবয়সের পেনসন, সন্তানদের মুখ্য ফাংশন ইহল তাদের অপদার্থ অবসর জীবন কাটানোর যোগান দেওয়া।ফলে এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যূপকাষ্ঠে বলি দেয় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।
তবে এই জনগোষ্ঠীর সকলেই নিজেকে বিশাল কিছু মনে করে।
উপরিউক্ত সমস্ত কিছুই মাত্র একটি সারাংশ। পুরো বলতে গেলে শতগিলগামেশের চেয়েও বড় উপাখ্যান হবে।
তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, এই জনগোষ্ঠীর পক্ষে কিছু করা তো দুর হস্ত, টিকে থাকাও দুষ্কর।কারণ বাকি সবকিছুর মতো এরা ডেমোগ্রাফিও হারিয়ে ফেলেছে। তবে এই অর্বাচীনদের মতে জনসংখ্যাও বোঝা।
তবে নে, এবার ঠেলা বোঝ।
Author: Purandhar Khilji
Historical Hindu 14-June-2022 by east is risingবাঙালি হিন্দু ১৮৭০ থেকে ইলবারট বিলকে কেন্দ্র করে ক্রমেই ব্রিটিশদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। চীন ও বাংলা অষ্টাদশ শতকে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিল্পোন্নত অঞ্চল এবং সবচেয়ে বড় বাজার। কিন্তু ১৮৪০ এর পরে ব্রিটেন ও পশ্চীম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠতে শুরু করে সবচেয়ে বেশি শিল্পোন্নত অঞ্চল এবং সবচেয়ে বড় বাজার। ফলে পূর্ব দিকের কোলকাতার থেকে পশ্চীম দিকের মুম্বাই-এর গুরুত্ত্ব বাড়তে শুরু করে। কারণ চীন ও বাংলার সাথে যখন প্রধান বাণিজ্য তখন কোলকাতাই গুরুত্বপূর্ণ আর পশ্চীমের সাথে যখন প্রধান বাণিজ্য তখন মুম্বাই সুরাট ইত্যাদির গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ১৮৭০ থেকে এটাই হচ্ছিল আর তাই বাঙালি হিন্দুর ব্রিটিশদের প্রধান বন্ধু হিসেবে থাকাটা অসম্ভব হচ্ছিল। তাই বাঙালি হিন্দু ও ব্রিটিশ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।
প্রথমে দ্বন্দ্বের জন্য বাঙালি হিন্দু বাংলা জাতিয়বাদের দিকে যায়। ১৮৮০-এর আদম সুমারী থেকে বোঝা যেতে থাকে যে বাংলা আস্তে আস্তে মুসলমান প্রধান অঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশরা ১৮৫৭ শিপাই বিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নেয় যে মোঘল ও ব্রাক্ষণ জোট ভাঙতে হবে কারণ ব্রিটিশ শিপাইদের ব্রাক্ষণ অংশ বিদ্রোহ করে কিন্তু রাজপুত অংশ ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকে। তাই হিন্দি অঞ্চলে রাজপুতদের ক্ষমতা বাড়াতে ও হিন্দু-মুসলমান দূরত্ব বাড়াতে হিন্দিকে উর্দুর থেকে পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ব্রিটিশরা ১৮৬৭ সালে আর সেন্ট্রাল প্রভিন্স (বর্তমান ইউপি) হিন্দিকে সরকারী ভাষা বানায় ১৮৮১ সালে। এইভাবে একটা বিশাল অঞ্চলকে হিন্দিভাষি বানিয়ে ফেলল ব্রিটিশরা।
ব্রিটিশরা বাঙালি হিন্দুদের বাঙালি জাতিয়তাবাদকে ভাঙতে হিন্দি ভাষা ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুতোকেই ব্যবহার করে। ১৯০৫-এ রিসলে সাহেব বলেন, "United Bengal is a power, once divided it will fall into different ways"। অর্থাৎ বাঙালি জাতিয়তাবাদকে ভাঙো। কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করতে চাইল এমনভাবে জাতে পূর্ব দিকে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে আর পশ্চীমে হিন্দিভাষিরা সংখ্যাগুরু হয়। এভাবে বাঙালি হিন্দুকে শক্তিহীন করে ফেলা সম্ভব। এই চাপের মুখে বাঙালি হিন্দু বলল বাঙালিকে এক রাখতে হবে। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু মুখে বলল যে তারা বাঙালি মুসলমানকে বেশি আপন মনে করে। কিন্তু কাজে এই মিলনের পক্ষে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলনা। শশঙ্ক ও ইলিয়াস শাহ-কে এক সূত্রে গাঁথতে হত। সিস্তানী, তুর্কি, পাঠানদের বিদেশি বলে যে তকমা বঙ্কিম চন্দ্ররা দিয়েছিল তা ভাঙতে হত। কিন্তু বাঙালি হিন্দু সেরকম কিছুই করতে পারলনা। উলটে এক দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার মুসলমানদের সাথে কোন আদর্শগত জোট না করে স্রেফ রাজনৈতিক জোট চালাতে লাগলেন আর রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহামানবের সাগরতীর প্রচার শুরু করলেন।
বাঙালি হিন্দু এটা মেনে নিতে পারছিলনা যে বাংলাতে মুসলমান সংখ্যা ৫০%-এর ওপরে আর তাই বাংলা কখনোই আর উনবিংশ শতকের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা বাঙালি হিন্দু। তাই সে ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় জাতিয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরছিল। কিন্তু ভারতকে হাতে রাখতে সে বাঙালি মুসলমানকে বাঙ্গালিত্বের মোড়কে সাঝাতে চাইছিল। এদিকে ১৯৩০-এর দশকে ফজলুল হকের সময় থেকেই কৃষক প্রজা পার্টি বানিয়ে বাঙালি মুসলমান দেখিয়ে দেয় স্বাধীন বাংলাতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাদের বেশি পছন্দের। এর মানে হল বাঙালি হিন্দু চাইছিল বাঙালি মুসলমান যেন তার সংখ্যা দিয়ে ভারতে বাঙালির সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়ায় আর বাঙালি মুসলমান চাইছিল স্বাধীন বাংলায় সংখ্যাগুরু হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং বাঙালি হিন্দু যেন সেই কাজে বাঙালি মুসলমানকে বাঙ্গালিত্বের নামে সমর্থন করে। বাঙালি হিন্দু যা করতে পারত তা হল খুব শক্তিশালী সংখ্যালঘু হিসেবে স্বাধীন বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে নিজেদের দাবিদাওয়া দরকষাকষির মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা। সেটা না করে বাঙালি মুসলমানদের ওপর নিজেদের তৈরি উনবিংশ শতকের বাঙ্গালিত্ব চাপাতে গেল আর ভেবে গেল বাঙালি মুসলমানের সমর্থন নিয়ে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
এরকম ভুল ভাবনা সফল হয়নি স্বাভাবিকভাবেই। বাঙালি হিন্দু পশ্চীম বঙ্গ নামে ভারতের মধ্যে ৮% জনসংখ্যার দুর্বল একটা রাজ্য তৈরি করল। ৪৭%-এর হিন্দিভাষি বা ৫২%-এর হিন্দি-গুজারাতি জোটের সামনে এই ৮% খুবই দুর্বল। এই ৮% বাঙ্গালির মধ্যে আবার ৩০% বাঙালি মুসলমান, ৩ঁঁ% উর্দুভাষি মুসলমান, ৮% হিন্দিভাষি ও ২% নেপালী। বাঙালি হিন্দু ৫৭%-এর বেশি নয় পশ্চীম বঙ্গে। আসাম, ত্রিপুরা ও ঝারখণ্ডে বসবাসরত বাঙালির মধ্যে সেরকম কোন উদ্দীপনা তৈরি করতে পারেনি। ১৯৪৭-এর ধাক্কা বাঙালিকে ভেঙেচুড়ে দিয়েছে। শুধু পাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশ নামে একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে পেরেছে বাঙালি মুসলমানেরা। বাকিটা একদম এলোমেলো হয়ে আছে। ইতিহাস এই এলোমেলো অয়ে যাওয়া জাতিকে খুব শিঘ্র একটা সুযোগ দিতে চলেছে। দেখা যাক.........।
Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya
Historical Hindu 11-June-2022 by east is risingযদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ’। (‘মহাভারত’, ১/৫৬/৩৩)
অর্থাৎ যা ‘মহাভারত’-এ আছে তা ভারতে আছে, আর যা ‘মহাভারত’-এ নেই তা ভারতেও নেই। এই একটি উ‘ক্তিই ভারতভূমির সাথে গ্রন্থটির নিবিড় ও অকৃত্রিম আত্মীয়তাকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে। বিষয়ের গুরুত্বে ও আয়তনে মহান ‘মহাভারত’ ভারতবর্ষের পৌরাণিক চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল দলিল। একে ‘কাব্য’,‘মহাকাব্য’,‘ইতিহাস’, ‘আখ্যান’, ‘উপাখ্যান’, ‘ধর্মশাস্ত্র’, ‘মোক্ষশাস্ত্র’ ইত্যাদি যাই বলা হোক না কেন, গ্রন্থটি আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারা ও মানসিকতাকে ব্যক্ত করছে। যেকোনো সাহিত্যগত উপাদানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যই বোধ করি তাই। আসলে সাহিত্যিক উপাদানগুলি বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজ ও সামাজিক মানসিকতাকে পরোক্ষে লিপিবদ্ধ করে রাখে। সময়ে সময়ে গবেষকগণ সেই সূত্র ধরে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ইতিহাসকে আরও পুষ্ট করেন। ‘মহাভারত’-ও তেমনই এক মূল্যবান উপাদান যা বহু বিচিত্র তথ্য তালাশের জাদুকাঠি।
আলোচনার শুরুতে ‘মহাভারত’ গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। লোকবিশ্বাস অনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা এবং বর্ণিত কাহিনির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তবে ১৮টি পর্ব ও লক্ষাধিক শ্লোকসমন্বিত যে ‘মহাভারত’ বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মূল শ্লোকসংখ্যা বিষয়ে মতান্তর আছে। কখনও একে ‘অষ্টৌ শ্লোকশতানি অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি’ অর্থাৎ ৮,৮০০ শ্লোকের বলা হয়েছে। কখনও ‘চতুর্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা’ অর্থাৎ ২৪,০০০ শ্লোকসমন্বিত বলা হয়েছে। আবার কখনও মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ‘শতসাহস্রী সংহিতা’ অর্থাৎ ১,০০০০০। এই তথ্যের ভিত্তিতে বহু গবেষক মহাভারত রচনাক্রমকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। আবার ‘আদি পর্ব’-এর সাক্ষ্য অনুসারে ‘মহাভারত’-এর কাহিনি তিন বার তিন জন পৃথক ব্যক্তির দ্বারা বিবৃত হয়েছে। তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে সহজ করে সাজিয়ে নিয়ে বলতে পারি—
১) প্রথম স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ৮,৮০০। বক্তা ব্যাস আর শ্রোতা ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন। এটি ‘জয়’ নামে খ্যাত।
২) দ্বিতীয় স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০। বক্তা বৈশম্পায়ন, শ্রোতা জনমেজয়। ‘ভারত’ নামে খ্যাত।
৩) তৃতীয় স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ১,০০০০০। বক্তা সৌতি, শ্রোতা শৌনকাদি ঋষিগণ। এটিই আসলে লোকবিশ্রুত ‘মহাভারত’।
প্রবন্ধের মূল বিষয়ের আলোচনার স্বার্থে ‘মহাভারত’-এর রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের যেকোনো ব্যক্তি বা দলিলের কালনির্ণয় কঠিনতম অংশ। তথ্যের অভাবে তুলনাত্মক জটিল অঙ্কের সিঁড়ি বেয়ে আনুমানিক সময়ে পৌঁছোতে হয়। ‘মহাভারত’-ও ব্যতিক্রম নয়। আশ্বলায়নের ‘গৃহ্যসূত্র’ সম্ভবত প্রাচীনতম দলিল যেখানে ‘মহাভারত’-এর উল্লেখ পাই এবং এর সময় আনুমানিক ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অপরদিকে ৪৪৫ খ্রিস্টাব্দের গুপ্তযুগীয় অভিলেখ সম্ভবত প্রথম দলিল যাতে লক্ষশ্লোকযুক্ত ‘মহাভারত’-এর উল্লেখ রয়েছে। অধিক জটিল আলোচনায় প্রবেশ না করে বলতে পারি, ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ সময় ধরে এই কালজয়ী গ্রন্থ একটু একটু করে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের বহু কবিপ্রতিভার স্পর্শে ধন্য ‘মহাভারত’ নামক সিন্ধুর বুকে লুক্কায়িত রয়েছে মূল্যবান বহু অপ্রিয় সত্য।
ভারতে ‘মহাভারত’-এর একাধিক সংস্করণ প্রচলিত আছে। তাদের পর্ব ও শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন। আবার বাংলা ভাষার বিখ্যাত সংস্করণগুলির মধ্যেও পাঠান্তর ও ব্যতিক্রম প্রচুর। শুধু তাই নয়, সংস্করণগুলির মধ্যে পর্বাধ্যায়সংখ্যা, তাদের বিন্যাস বা শ্লোক সংখ্যাগত পার্থক্যও অনেক। এই সকল পাঠান্তর ও ব্যত্যয় গবেষণার বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এসব জটিলতা আলোচ্য বিষয়ের জন্য জরুরি নয়। অত্যন্ত পরিচিত ও প্রচলিত কাহিনিনির্ভর এই আলোচনা।
এইবার আসা যাক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণ’ দ্রোণাচার্য চরিত্রের বিশ্লেষণে। দ্রোণের অন্যান্য পরিচয় ছেড়ে সচেতনভাবে তাঁকে ‘ব্রাহ্মণ’ বিশেষণে বিশেষায়িত করা কেন? কারণ দ্রোণ চরিত্রের যত বিড়ম্বনা ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয়। কীভাবে? তা ক্রমশ প্রকাশ্য। ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ প্রথমে পিতার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন।তারপর মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শী হন। পিতার আদেশে কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। অশ্বত্থামা নামে তাঁদের এক অতি তেজস্বী পুত্র সন্তান জন্মায়।পিতার মৃত্যুর পর দ্রোণ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ পরশুরামের কাছে বহু বিচিত্র ও অসাধারণ অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রত্যাহার শিক্ষা করে হয়ে উঠলেন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।এই পর্যন্ত দ্রোণের জীবন নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন ছিলনা। প্রশ্ন থাকার কথাও নয়। কারণ এক সাধারণ ব্রাহ্মণ সন্তান আর পাঁচটা সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মতোই জীবন অতিবাহিত করছেন।পিতার নির্দেশে অল্পকেশী সাধারণ কন্যাকে বিয়ে, সন্তান। আর ব্রাহ্মণের যা কাজ, মানে এই গুরু ওই গুরুর কাছে নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণ করে বেড়ানো।কিন্তু দ্রোণ তো অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন? তাতে কী! তিনি তো শিখছিলেন, তার প্রয়োগ তো করেননি। তাই এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল।বিড়ম্বনা শুরু হল দ্রোণ যখন দ্রোণাচার্য হলেন অর্থাৎ রাজার বেতন ভোগী অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক হলেন। ব্রাহ্মণ হয়ে অস্ত্রজীবী! সমালোচনা ক্রমশ অসম হতে লাগল। বনে-জঙ্গলে যৎসামান্য ছাউনির তলায় বসে, ক্ষুধাকে অস্বীকার করে, ইহলোক ও পরলোকের গূঢ়তত্ত্ব চর্বিত চর্বণ না করে এই ব্রাহ্মণ কী না রাজগৃহে থেকে, ভালো ভোজন করে, রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার সাহস দেখায়! অনিবার্য সমালোচনা; ব্রাহ্মণ মানেই ক্ষমতালোভী ও সুযোগ সন্ধানী। একলব্যের প্রসঙ্গ এলে তো আর কথাই নেই। সকলে সমস্বরে দ্রোণাচার্যের মুণ্ডচ্ছেদনে ব্রতী হন। এত নিষ্ঠুরতা ও জাতিবিদ্বেষ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর মধ্যেই নেই। দ্রোণাচার্য গুরুকুলের কলঙ্ক— এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেউ বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করেন না। তাছাড়া অন্যায় যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বে যেভাবে নির্বিচারে অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছে তাতে দ্রোণাচার্য চরিত্রের নির্মম পাশবিকরূপ স্পষ্ট। এইরকম শত শত অভিযোগ ও সমালোচনার শরে দ্রোণাচার্য আহত ও পীড়িত। নিঃসন্দেহে কিছু ঘটনার আকস্মিকতা হৃদয়কে সহস্রছিন্ন করে। কিন্তু সমালোচনা তো ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, কোমলতা-কাঠিন্য উভয়ের সামঞ্জস্যতার অপেক্ষা রাখে। চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যে কোনো পরম প্রিয়ের আঘাত বীজ হিসেবে লুকিয়ে রয়েছে কি না তার অনুসন্ধানই বিশ্লেষণকে নিটোল করে। প্রবন্ধটি এইধরনের কিছু প্রবণতা অন্বেষণের একটি প্রয়াস।
মনে রাখতে হবে, যে সুদীর্ঘ সময়কে আমরা ‘মহাভারত’ সংকলনের সময় হিসেবে নির্দেশ করেছি সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থাপনায় ‘কৌটিলীয়-অর্থশাস্ত্র’ ও ‘মনুস্মৃতি’ এই দুই গ্রন্থের প্রভাব ছিল বিস্তর। এই দুই গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার ভিত্তি ছিল ‘বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা’। এদের মধ্যে ‘বর্ণ-ব্যবস্থা’-র ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। চার ‘বর্ণ’ হল—‘ব্রাহ্মণ’, ‘ক্ষত্রিয়’, ‘বৈশ্য’ ও ‘শূদ্র’। এদের কাজও নির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণের কাজ— অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হল সমাজের সুশিক্ষিত অংশ। ক্ষত্রিয়ের কাজ— অধ্যয়ন, যজন, দান ও অস্ত্রজীবী হওয়া বা প্রজাপালন করা। সহজ কথায় ক্ষত্রিয়রা হল সমাজের ক্ষমতাবান অংশ। বৈশ্যদের কাজ— অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ঋণদান। অর্থাৎ বৈশ্যরা হল সমাজের বিত্তবান অংশ। শূদ্রদের কাজ— বাকি তিন বর্ণের সেবা করা। সহজ করে বললে যুদ্ধ, কৃষি, পশুপালন, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিপুল পেশিশক্তি প্রয়োজন তার যোগান দেয় শূদ্ররা। অর্থাৎ শূদ্ররা হল সমাজের শ্রমজীবী অংশ। এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পরিবর্তে যথাক্রমে শিক্ষিত, ক্ষমতাবান, বিত্তবান ও শ্রমজীবী/পেশিশক্তি শব্দগুলি সচেতনভাবে বার বার ব্যবহৃত হবে। যাইহোক, এই বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যেই পরস্পরকে লড়িয়ে দেওয়ার যথেষ্ট উপাদান ছিল। পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যারা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত অংশ তাদের সামান্য জীবিকাটুকু নির্দিষ্ট হল না। শিক্ষিতদের হাতে না থাকল উপার্জনের ক্ষমতা, না থাকল প্রশাসনিক ক্ষমতা। অপর দিকে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যাদের হাতে শাসনক্ষমতা তাদের হাতে অর্থকরী ক্ষেত্রগুলির (কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি) সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা শিক্ষিতদের মতো সামাজিক খ্যাতি কোনোটাই রইল না। আবার বৈশ্যরা অর্থাৎ যাদের হাতে বিপুল অর্থ তাদের কাছে প্রশাসনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাও নেই এবং শিক্ষিতের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নেই। শূদ্ররা অর্থাৎ যাদের পেশির ওপর নির্ভর করে ক্ষমতাবানরা বছরের পর বছর ক্ষমতায় থাকছে, যাদের শ্রম ও দক্ষতার ওপর ভর করে বিত্তবানরা তাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করে আরও বিত্তশালী হচ্ছে তাদের হাতে প্রায় কিছুই নেই। শিক্ষার অধিকার নেই, জমির অধিকার নেই, আর্থিক, সামাজিক বা প্রশাসনিক নিরাপত্তাও নেই। ফলে এই চার বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে কী সুচারু ও সুচতুর কৌশলে এই প্রতিযোগিতাকে করে তোলা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক। তাই লড়াইটা হয়ে উঠল শুধু ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের। অথচ এই দুই ‘বর্ণ’-ই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা এমনভাবে হতে লাগল যেন ব্রাহ্মণই কেবল শূদ্রকে অস্পৃশ্য মনে করে কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের গৃহে তাদের অবাধ বিচরণ। কিছু আজব নিয়ম-কানুনকে হাতিয়ার করে শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা দারিদ্র আর জীবিকাহীনতার হতাশা শূদ্র-অত্যাচারের মাধ্যমে চরিতার্থ করতে লাগল। অপরদিকে, বিত্তবান বা ক্ষমতাবান কোনো প্রভুর অধীনস্ত শূদ্ররা মনিবের অত্যাচার জীবিকার খাতিরে মানতে বাধ্য হলেও হতদরিদ্র, অশৌখিন ব্রাহ্মণদের অযথা লাঞ্ছনা সহ্য করতে বা পারিশ্রমিকহীন সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিল না। অগত্যা নিজেদের সমস্যা ও বঞ্চনার প্রতিকারের পরিবর্তে এই দুই বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা বাড়তে লাগল। সমাজের ক্ষমতাবান বা বিত্তশালীরা এই দ্বন্দ্বের অখণ্ড ফল ভোগ করে গেল।‘বর্ণ-ব্যবস্থা’-য় চার ‘বর্ণ’-এর উল্লেখের ক্রমের মধ্যেও যেন এই ষড়যন্ত্রের আভাস আছে। লক্ষ্য করুন, এই ক্রমে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার পরের পরের ‘বর্ণ’-এর সঙ্গে যোগাযোগ ও হৃদ্যতা ক্রমশ কমছে। ব্রাহ্মণের সাথে (অবশ্যই মুষ্টিমেয় কিছু ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয়ের যে সম্পর্ক, বৈশ্যের সাথে তা অনেকটাই দুর্বল। আবার বৈশ্যের সাথে ব্রাহ্মণের যে দুর্বল যোগাযোগ তা শূদ্রের কাছে গিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কায়দা করে শিক্ষিতদের অর্থবল ও লোকবল থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। সমাজের এই সবকটি মানসিকতা ক্ষমতা ও অর্থের অলিন্দে থাকা একটা শ্রেণির গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল। আর দ্রোণাচার্য তার একটি শিকার।
দ্রোণের প্রথম অপরাধ তিনি ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তির পরিবর্তে ক্ষাত্রধর্মকে বৃত্তি করেছেন। অনিবার্যভাবে দ্রোণাচার্যের সাথে শাস্ত্রঅবমাননাকারী, ক্ষমতালোভী ইত্যাদি বিশেষণ সেঁটে দেওয়া হল। আমি আর একটু তলিয়ে ভাবতে চাই। দ্রোণাচার্য যে শুধু মহান অস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাই নয় বেদ, বেদাঙ্গ, মনুর নীতিশাস্ত্রাদিতেও দ্রোণ নিষ্ণাত। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যেকোনো দেশের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! পূর্বে দ্রোণ ছিলেন পাঞ্চালদেশের অধিবাসী। একদিন তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা ধনিপুত্রদের দুধ খেতে দেখে বাবা দ্রোণের কাছে এসে কাঁদতে লাগল। বালককে দুধ খাওয়ানোর আশায় উচ্চশিক্ষিত দ্রোণ ধর্মসঙ্গত উপায়ে পয়স্বিনী গাভী সংগ্রহের চেষ্টা করলেন এবং ব্যর্থ হলেন। দান যদি ব্রাহ্মণের উপার্জনের সাধন হয় তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে দান অপরের ইচ্ছাধীন। যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেই বস্তুই লোকে দান করবে এমন কাকতালীয় ঘটনা তো আর বার বার ঘটবে না। ইতিমধ্যে ধনিপুত্ররা শিক্ষিত অথচ উপার্জনহীন ব্রাহ্মণ দ্রোণের পুত্রের সাথে আর একটু তামাশা করল। অশ্বত্থামাকে তারা পিটুলি (চাল বাটা) গোলা জল খেতে দিল। তা খেয়েই দ্রোণের পুত্র আহ্লাদে আটখানা। অর্থাৎ বালক অশ্বত্থামা শিশু বয়সেও কোনোদিন দুধের আস্বাদ পায়নি। সেই কারণে বালক অশ্বত্থামা পিটুলি গোলা জলকেই দুধ বলে পান করে আনন্দ পাচ্ছে। ধিক সেই যোগ্যতাকে যে যোগ্যতায় একজন পিতা তার সন্তানের জন্য একটু দুধ জোটাতে পারে না। ধিক সেই সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে যে ব্যবস্থাপনায় দরিদ্রদের সামান্য সামাজিক সম্মান ও অধিকারটুকু নিশ্চিত হয় না। অগাধ যোগ্যতাসম্পন্ন দ্রোণের জীবনে এর থেকে বেশি হতাশাজনক এবং অপমানের আর কী হতে পারে?একদিকে শিক্ষিত দ্রোণের দারিদ্রের হৃদয়বিদারক ছবি; উল্টোদিকে ব্রাহ্মণের দারিদ্রে বিত্তবানদের বিদ্রুপ— বহু প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত কথা বলছে। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। বিত্তবানেদের লাঞ্ছনায় পীড়িত পিতা দ্রোণের এবার এক ক্ষমাতাবানের কথা মাথায় এল। তিনি দ্রোণের বাল্যসখা, সহপাঠী এবং অধুনা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ।প্রতিকারের আশায় ছুটলেন দ্রুপদের কাছে। কিন্তু কেবলমাত্র বন্ধু সম্বোধনের অপরাধে ক্ষমতাবান দ্রুপদ দরিদ্র দ্রোণকে অকথ্য অপমান করলেন এবং কেবলমাত্র এক রাত্রির উপযুক্ত ভোজন দিতে ইচ্ছা করলেন। যে প্রশাসন দ্রোণের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপার্জনের উপায় করতে পারেনা সে প্রশাসন কী জনকল্যাণ করবে? আদৌ সে প্রশাসকের ক্ষমতায় থাকা উচিত? না কি শিক্ষিতরা দিন গুজরানের জন্য ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালীদের দোরে দোরে ঘুরবে— এটাই অভিপ্রায়? ঠিক এখানেই দ্রোণ ষড়যন্ত্রীদের একহাত নিয়েছেন। শিক্ষিত মানেই মেধা আর ক্ষুধাকে একসাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—সমাজের এই অযৌক্তিক আবদারের বিরুদ্ধে দ্রোণ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন হস্তিনাপুরে যোগ্যপদে চাকরি নিয়ে। মেধাকে তিনি ক্ষুধা নিবারণের হাতিয়ার করতে শেখালেন।
এইবার কেউ কেউ ঝাঁঝিয়ে প্রশ্ন করবেন দ্রোণের জীবনে এইটুকুই না হয় কষ্ট। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তো প্রশ্নাতীত ক্ষমতা ভোগ করেছেন? আমি আবারও উল্টো কথা বলব। হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রোণাচার্য কেবলমাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপযুক্ত সম্মান পেতেন যা তাঁর যোগ্যতাবলে পাওয়া। কিন্তু প্রশ্নাতীত ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কারণ তিনি রাজা নন। রাজা তো রাজাই। ‘মনুসংহিতা’ বলছে— ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের— এই সকল দেবতার সারভূত অংশ নিয়ে পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন (৭/৪)। সিদ্ধান্ত এই— ‘বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ/ মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি//’ (৭/৮) অর্থাৎ রাজা নাবালক হলেও (বলা ভালো রাজপদের অনুপযুক্ত হলেও) তাঁকে সাধারণ মানুষ ভেবে অবজ্ঞা কোরো না; আসলে রাজা হলেন প্রকৃতপক্ষে একজন দেবতা যিনি মানুষের রূপে এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন। অতএব রাজাই ঈশ্বর, রাজকর্মচারীরা নন। আবার মন্ত্রীদের সাথে পর্যালোচনা করলেও তাদের সিদ্ধান্তই যে রাজাকে মেনে চলতে হবে তাও নয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত রাজাই নিতেন। এক্ষেত্রে ‘মনুসংহিতা’-র সাক্ষ্য— ‘সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ হিতমাত্মনঃ’ (৭/৫৭)। অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে বা মিলিত ভাবে মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে রাজা নিজে যেটি হিতকর বলে মনে করবেন সেইরকম করবেন। অতএব যারা এই ধারণা পোষণ করেন যে শাসনযন্ত্রে ব্রাহ্মণরাই সর্বোচ্চ স্থানে থাকতেন এবং ব্রাহ্মণদের কথা মতো রাজারা চলতেন, তাদের বলি হিসেবটা এক আর একে দুইয়ের মতো অতটা সহজ ছিল না। যদি তাই হত তাহলে দ্রোণ, কৃপদের পরামর্শ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা যুবরাজ দুর্যোধন মেনে নিতেন আর কুরক্ষেত্রের যুদ্ধই হত না। পদে পদে এঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিক্ষিতদের উপদেশ মোটেই ক্ষমতাশালীদের অভিপ্রেত ছিল না। ভেবে দেখুন, শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁদেরই শাস্ত্রীয় পরামর্শে ক্ষত্রিয়রা সমাজের শাসন পরিকাঠামোর সর্বেসর্বা। ব্রাহ্মণের পরামর্শ ক্ষত্রিয় শুনতেও পারে আবার নাও পারে। নিজেদের রাজা করবার এমন সুযোগ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা কেন হাতছাড়া করলেন? তাহলে কি মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষকে নিমিত্ত করে সমাজের ক্ষমতালোভীরা নিজেদের অভিসন্ধিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে? কোনো রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুমোদন ছাড়া কি কোনো নীতিশাস্ত্র রচিত বা অনুমোদিত হতে পারে? প্রশ্ন থাকছেই।
এবার আসি দ্রোণ-একলব্যের প্রসঙ্গে।দ্রোণ একলব্যের কাহিনিকে বিশ্লেষণ করে ব্রাহ্মণের জাতিবিদ্বেষ বা গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ককে কলুষিত করবার তত্ত্ব যেমন খাড়া করা যায় তেমনি এগুলির অতিরিক্ত কিছু সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়। ভেবে দেখুন, দ্রোণাচার্য একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিয়ে কার স্বার্থ রক্ষা করলেন? এক ক্ষমতাশালী পরিবারের ও এক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বালক অর্জুনের। দ্রোণাচার্য নিজে কী পেলেন? কলঙ্ক আর সমালোচনা। আবার একলব্যের নীচুজাতির কারণে সমাজের তৈরি করা নিয়মের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে দ্রোণ তাঁকে সরাসরি শিক্ষাদানেও আপত্তি করলেন। ব্রাহ্মণের জাতিবিদ্বেষ তত্ত্ব আরও সুদৃঢ় হল। কিন্তু একলব্যের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যেসব ধারণা প্রচলিত রয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আশ্চর্য হতে হয়। ‘হরিবংশ’ (মহাভারতের ১৮টি পর্বের অতিরিক্ত অংশ) অনুসারে এই নীচুজাতির একলব্য জরাসন্ধের হয়ে যুদ্ধ করেছেন যখন কংশবধের প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। ‘ভাগবত পুরাণ’ (মথুরা সংস্করণ) অনুসারে জরাসন্ধের বাহিনীর যোদ্ধা একলব্যকে কৃষ্ণ হত্যা করেন কারণ তিনি জানতেন একলব্যের মতো যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়ের পথে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেন। আবার এমন কাহিনিও প্রচলিত আছে যে, রাজপুত্র দুর্যোধন একলব্যকে হস্তিনাপুরের সমস্ত বনের রাজা ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ একলব্য কেবলমাত্র নীচজাতি হওয়ার কারণে যে সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে তাঁকে তাঁর ছাত্ররূপে গ্রহণ করতে দিল না, সেই সমাজের ক্ষমতাবানরা কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে তাঁর যুদ্ধের প্রতিভাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে গেল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিনাপ্রশ্নে এই ষড়যন্ত্রকে মেনেও নিল! তখন তাদের জাত-কুল-মান সব হয়ে গেল গৌণ! না; একলব্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কর্ণের ক্ষেত্রেও সে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সূতপুত্র হওয়ার অপরাধে দ্রোণ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও হস্তিনাপুরের শাসকরা সময় মতো তাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। লক্ষ্যণীয়, এতে দ্রোণাচার্যের মতো ব্রাহ্মণদের সাথেই কেবল একলব্য বা কর্ণদের মতো নীচুতলার মানুষগুলোর দূরত্ব বাড়ে। আর ক্ষমতাবানেদের প্রতি বাড়ে আনুগত্য। অথচ কোন জাদুবলে জানি না, ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাঁকেই হত্যা করবার ইচ্ছায় তাঁরই তত্ত্বাবধানে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠানো হল আর তিনি তাকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না! ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষমতাশালীর পুত্র বলেই কি দ্রোণ জানতে জানতে বিষ পান করলেন? উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও দ্রোণ যদি এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন তবে সমাজের বাকি শিক্ষিতদের দশা কীরূপ ছিল? সমস্ত সম্ভাবনারই পক্ষপাতহীন অনুসন্ধান প্রয়োজন।
এবার আসা যাক অভিমন্যুবধ প্রসঙ্গে। যারা দ্রোণের সেনাপতিত্বে অন্যায় যুদ্ধের তত্ত্ব কপচে বেড়ান তাদের বলি মহাভারতে অন্যায় যুদ্ধের বর্ণনা সঠিক ভাবে করলে একটি উপন্যাস হয়ে যাবে। শুধু দ্রোণকে দোষ দিলে আপনার পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতাই স্পষ্ট হয়। আর একটি বাস্তব কথা ভাবুন, আপনি যুদ্ধের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা আশা করেন কী করে? সমস্ত নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখনই তো যুদ্ধের মতো নৃশংসতা নেমে আসে। অতএব নিয়ম মাফিক যুদ্ধের আশা করা মূঢ়তার নামান্তর। তবে অভিমন্যুবধের আগের কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে ক্ষমতালোভীদের যেকোনো কিছুর বিনিময়ে ক্ষমতা প্রাপ্তির এক জঘন্য প্রচেষ্টা ধরা পড়ে। ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই দুর্যোধন সেনাপতি দ্রোণকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কারণ কৌরবদের পরিকল্পনা অনুসারে এখনও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করতে সমর্থ হননি। দ্রোণের প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও দুর্যোধনের ক্রুর বাক্যবাণে মর্মাহত দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে আজকের যুদ্ধে পাণ্ডবদের একজন ‘মহারথ’-কে (যিনি বহু রথীর অধিনায়ক) হত্যা করবেন। একেবারে একজন বীর যোদ্ধাসুলভ দ্রোণের এই আচরণ। পরিকল্পনা হল আজ দ্রোণ এমন এক ব্যূহ রচনা করবেন যা কয়েকজন মাত্র ভেদ করতে পারেন। কিছু যোদ্ধা অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে ব্যূহ থেকে দূরে রাখবে। হলও তাই। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন এবং যথা স্থানে উপযুক্ত যোদ্ধাদের স্থাপন করলেন। সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখলেন। বেগতিক দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন এই বুঝি গুরু দ্রোণাচার্য তাঁকে বন্দি করলেন। ধরা পড়ার ভয়ে আকুল হয়ে তিনি অভিমন্যুকে আদেশ করলেন চক্রব্যূহ ভেদ করতে। অভিমন্যু ভীষণ স্পষ্ট করে জানালেন তিনি চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতি তাঁর জানা নেই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বন্দি হতে নারাজ। বন্দি হলে যুদ্ধও শেষ হবে। রাজ্য জয়ের সকল আশা ব্যর্থ হবে। তা তিনি হতে দিতে পারেন না। অতএব যে ব্যূহ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, যে ব্যূহ মহাযোদ্ধা দ্রোণ রচনা করেছেন, সেই ব্যূহে তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবলীলায় নিক্ষেপ করলেন। যিনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারেন না তাঁর পরামর্শ মতো স্থির হল অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে রাস্তা করে দেবেন আর বাকি যোদ্ধারা সেই পথে ব্যূহে প্রবেশ করে অভিমন্যুকে রক্ষা করবেন। দ্রোণের মতো যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করা কী এতই সহজ! কৃষ্ণের বুদ্ধিতে আর ভাইয়েদের শক্তিতে বলীয়ান যুধিষ্ঠিরের কী এমন যুদ্ধশাস্ত্রগত মেধা আছে যে দ্রোণাচার্যের তৈরি ব্যূহ ভেদ করবেন? যা ফল হওয়ার তাই হল। অভিমন্যুর তৈরি করা পথে পাণ্ডব যোদ্ধারা প্রবেশ করতে পারলেন না আর অভিমন্যুও প্রাণ থাকতে ব্যূহের বাইরে বেরোতে পারলেন না। কেউ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আগুনকে দগ্ধ করার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন কি? কিন্তু হ্যাঁ এই অভিমন্যুর জ্যেষ্ঠতাত কয়েকদিন পরেই রাজা হয়েছিলেন। আর দ্রোণ আজও কলঙ্কের ভাগিদার।
দ্রোণাচার্যের জীবনের বিভিন্ন ছোটো ছোটো ঘটনা বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষিতদের স্থান ক্ষমতাবানদের পদতলে। সমাজের ক্ষমতাশালীরা তাদের স্বার্থে যেমন খুশি তাদের মেধা বা স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করতে পারে। কারণ শিক্ষিতরা দিনের শেষে বেতনভোগী কর্মচারী। রাজশেখর বসুর ‘মহাভারত’-এর সারানুবাদ থেকে জানা যায় কৌরবগণ কপট উপায়ে জয় করা ইন্দ্রপ্রস্থের দায়িত্ব দ্রোণকে দিয়েছিল। বিষয়টি তলিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। পঞ্চপাণ্ডবের সুযোগ্য নেতৃত্বে ইন্দ্রপ্রস্থ স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সুখ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ রাজ্যের প্রজারা ভালোই ছিল। এমন সময় হঠাৎ করে তাদের রাজার সাথে কপটতা করে তাদের বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাদের রাজরাণীর অপমানের কথাও তারা নিশ্চয়ই জানত। এমন অবস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজাবিপ্লব বা প্রজাবিক্ষোভ কি খুব স্বাভাবিক নয়? এমতাবস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থে দরকার ছিল এক সুদক্ষ প্রশাসকের। রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজে অন্ধ। তিনি নিজে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। অতএব তার দ্বারা এই দায়িত্ব পালন কোনো উপায়েই সম্ভব ছিল না। দুর্যোধন নামেই নিজের মস্তক ধারণ করেন। মামা শকুনি আর বন্ধু কর্ণের বুদ্ধি ছাড়া তিনি এক পা চলতে পারেন না। অতএব এই দুর্যোগ ঠেকানো তাঁর কর্ম নয়। সুতরাং বিকল্পের সন্ধান। দ্রোণ সেক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ। কারণ তিনি বুদ্ধিমান এবং বীর। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি আলোচনা ও যুদ্ধ দুই বিষয়েই সমান পারদর্শী। তাছাড়া তিনি শিক্ষিত তাই সমাজে তাঁর একটা বিশেষ ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। অগত্যা প্রভুদের পাপের বোঝা বেতনভোগী কর্মচারীকেই নিতে হল। অনেকেই বলতে পারেন এই যুক্তি কল্পনা মাত্র।তাদের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা; ঠিক কী কারণে এত কুমন্ত্রণা ও কপটতার পর প্রাপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্যোধন ভোগ করলেন না? কুটিল তর্কের খাতিরেও কেউ নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে ত্যাগী, বিষয়ে নির্লিপ্ত বা ভোগে উদাসীন বলবেন না!
দ্রোণ আজীবন তাঁর আশ্রয়দাতাদের হিতার্থে কাজ করে গেলেন। তাঁর সমস্ত শিক্ষা উজাড় করে দিয়েছেন রাজপুত্রদের। শ্রেষ্ঠ ছাত্র অর্জুনের প্রতি তাঁর স্নেহ কখনও কখনও পুত্র অশ্বত্থামাকেও অতিক্রম করে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে প্রতিটি অন্যায়ের পূর্বে সাধ্যমতো সতর্ক করবার সমস্ত প্রয়াস করেছেন। অন্যায় যুদ্ধ জেনেও কেবলমাত্র প্রভুদের প্রতি আনুগত্যবশত প্রাণপ্রিয় পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সপুত্র যুদ্ধ করেছেন ও প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু এই আনুগত্য ক্ষমতাবান আশ্রয়দাতারা স্বীকার করল কোথায়?‘উদ্যোগপর্ব’-এ দৌত্য কর্ম শেষে সঞ্জয় যখন কৌরব সভায় পাণ্ডবদের মনোভাব স্পষ্ট করছেন তখন আসন্ন জয় পরাজয়ের চিন্তায় দোদুল্যমান রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে হয়েছে দ্রোণ তাঁর দেওয়া দানের প্রতিদান হিসেবে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও জয়লাভ করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যেহেতু দ্রোণ স্থবির ও অর্জুনের গুরু।ভাইয়ের ভাগ্য বিড়ম্বনাকে হাতিয়ার করে নিজের প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে সিংহাসন আঁকড়ে থাকা ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অবদান কী? তিনি কোন যোগ্যতাবলে দ্রোণাচার্যের মূল্যায়ন করেন? অন্নদাতা বলেই কি তাঁর এই দম্ভ? অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৮ দিনের মধ্যে ৫ দিন (১১-১৫ নং দিন দ্রোণের মৃত্যু পর্যন্ত) এই বৃদ্ধের নেতৃত্বেই কৌরবরা যুদ্ধ করেছে। কৌরবদের জন্যই এই বৃদ্ধ প্রাণ দিয়েছেন। আর দুর্যোধনের কথা নাই বা বললাম। একদা অস্ত্রগুরু যে বর্তমানে তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী তা তিনি পদে পদে দ্রোণকে বুঝিয়েছেন। দ্রোণের জীবদ্দশায় কোনো অস্ত্রের আঘাত হয়তো তাঁকে এতটা আঘাত করেনি যতটা আঘাত করেছে দুর্যোধনের বাক্যবাণ। শিক্ষিত কর্মচারীর মনিব যদি বুদ্ধিহীন ও ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয় তবে সেই কর্মচারীর অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভালো।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কেউ ধর্মযুদ্ধ হিসেবে দেখেন তো কেউ দেখেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র হিসেবে। আমার ধারণা খানিক ভিন্ন। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিল কারা? পাণ্ডবপক্ষে এক ব্রাহ্মণ দ্রোণের শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন। কৌরবপক্ষে ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য ভীষ্ম (১-১০ দিন), ব্রাহ্মণ দ্রোণ (১১-১৫ দিন), ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য কর্ণ (১৬-১৭ দিন), শল্যের পর আরও এক ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা (১৮ নং দিন দুর্যোধনের পরাজয়ের পর)। যুদ্ধে ধ্বংস হল কারা? ব্রাহ্মণগুরুদের অসামান্য যোদ্ধা শিষ্যরা এবং সেনাবাহিনীতে চাকরিরত সহস্র সহস্র সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এই যুদ্ধ সমাজকে কতটা আঘাত করল? মানুষ দেখল যুদ্ধের নামে বিপুল আর্থিক সম্পদ, মানবসম্পদ, পশুসম্পদের অপচয়। সমাজ বুঝল ক্ষমতাশালী হতে গেলে স্নেহ, মায়া, মমতার বা শ্রদ্ধার সকল সম্পর্ককে প্রথমে হত্যা করতে হয়। স্বজন হারানো, বন্ধু হারানো, গুরু হারানো, শিষ্য হারানো, পিতা হারানো, পুত্র হারানো এই যুদ্ধ থেকে লাভবান হল কারা? কেবলমাত্র ক্ষমতাশালীরা। একদল ক্ষমতাবান যুদ্ধে পরাজিত হলেও তাদের যুদ্ধ করবার বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হল। আর এক দল এই যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করল। যে শিক্ষিত ও শ্রমজীবীরা প্রাণ দিল তারা কী পেল? আবার এক নতুন প্রভু? এত প্রাণ নিজেদের জন্য দিতে পারলে তো নতুন প্রভুর বদলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত! তাহলে শুধুমাত্র প্রভু পরিবর্তনের খেলায় কেন এত আত্মাহূতি? এই মানসিকতা সত্যিই অবাক করে।
যদি ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দকে মহাভারতের মূল কাহিনির সময় কাল ধরে নিই তাহলে দ্রোণ আসলে সেই সময় থেকেই বিকশিত হতে চাওয়া এক প্রবণতার বীজ। দ্রোণ তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দ্রোণ মেধাকে ক্ষুধা জয়ের অস্ত্র করেছেন। শিক্ষিত হলেই বিত্তশালী আর ক্ষমতাশালীদের পারিশ্রমিকহীন শিক্ষা প্রদান করতে হবে— সমাজের এই প্রচলিত ধারণার মূলে দ্রোণাচার্য আঘাত করেছেন। আপন যোগ্যতার বলে বলীয়ান হয়ে ক্ষমতাবানেদের থেকে রাজকীয় সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছেন। দ্রুপদের মতো ক্ষমতাবানকে পদানত করে শিক্ষিতদের বার্তা দিয়েছেন। এরপরেও বলতে হয় কোথাও যেন প্রতিবাদের ভাষা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। প্রশ্ন থেকে গেল অনেক। যে দ্রুপদকে বৃদ্ধ দ্রোণ কুরুক্ষেত্রের মাঠে পরাজিত করতে পারেন সেই দ্রোণের যৌবনে তাঁকে হারাতে কেন ক্ষমতাবান পরিবার থেকে আসা শিষ্যদের প্রয়োজন হল? পাঞ্চাল জয় করেও কেন দ্রুপদকে অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন? কেন একলব্য বা কর্ণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে মেধাশক্তি ও পেশিশক্তির মধ্যে কৃত্রিম দূরত্ব তৈরির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারলেন না? যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন দ্রোণ বেতনভোগী কর্মচারীর ভাবমূর্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন না? এইরকম বহু প্রশ্ন আসলে এক অনুচ্চারিত, অনালোচিত রহস্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। তবে দ্রোণ যে সমাজের ক্ষমতাশালীদের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাইতো যুধিষ্ঠিরকে হাতজোড় করে দ্রোণের কাছে তারই মৃত্যুর উপায় জানতে হয়। ধর্মযুদ্ধের নামে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে হয়। চুলের মুঠি ধরে মুণ্ডু কেটে ক্ষমতাবানেদের দ্রোণের মৃত্যুতে উল্লাস বুঝিয়ে দেয় এই শিক্ষিত লোকটি তাদের কতটা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়দের বাহুবলে দ্রোণকে জয় করা অসম্ভব ছিল। রাজশেখর বসুর অনুবাদ অনুসারে (দ্রোণপর্ব, দ্রোণবধপর্বাধ্যায়) পঞ্চদশদিনের যুদ্ধে ভীমের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে প্ররোচিত না হয়ে দ্রোণ যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছেন তখন বিশ্বামিত্র, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রমুখ মহর্ষিগণ দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন (সূক্ষ্মদেহে) এবং জানালেন যে দ্রোণ যেহেতু অধর্মযুদ্ধ করছেন তাই তাঁর মৃত্যু আসন্ন। এইধরনের নেতিবাচক প্ররোচনা একজন যোদ্ধার মানসিক দুর্বলতার জন্য যথেষ্ট। মজার বিষয় হল, এইভাবে দ্রোণের উৎসাহহানি করছেন কিছু ব্রাহ্মণ! তবে কি বিপ্লব করতে চাওয়া শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শিক্ষিতদের লড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতাশালীদের ক্ষমতায় টিকে থাকার গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য?যাইহোক না কেন দ্রোণকে যদি এই বিপ্লবের বীজ ধরি তবে অবশ্যই পুষ্যমিত্র সুঙ্গ তার প্রথম পরিণতি এবং পরবর্তী সময়ে কাণ্ব, সাতবাহনরা সেই পরিণতির প্রবহমান ধারা। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এমনই এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মৌর্য বংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথকে ক্ষমতাচ্যুত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। কিংবদন্তির যদি কিছুমাত্রও সত্যি হয় তবে কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণের মেধাশক্তিতে ভর করে নীচুতলার প্রতিনিধি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার পুষ্যমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে ক্ষমতাবান মৌর্যরা পদানত হল। আসলে শিক্ষিত নেতা আর প্রচুর পেশিশক্তির মিলনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যুগান্তকারী বিপ্লবের আগুন। সেই আগুন যেকোনো বিত্তশালীর অর্থের শক্তি বা যেকোনো ক্ষমতাশালীর প্রতিরোধ শক্তিকে নিমেষে গ্রাস করতে পারে। তাই ষড়যন্ত্রীরা যুগ যুগ ধরে কখনও মেধার পক্ষ নিয়ে আবার কখনও পেশির পক্ষ নিয়ে মেধা আর পেশিকে পরস্পরের শত্রু করে রেখেছে। তাই কখনও পেশিশক্তি একত্রিত হলেও নেতার শিক্ষার অভাবে আন্দোলন উদ্দেশ্য হারায়। আবার কখনও নেতা শিক্ষিত হলেও পেশিশক্তি তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। পক্ষপাতহীন সামগ্রিক প্রচেষ্টাই এর সমাধান করতে পারে। নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, আমাদের এই সঙ্কীর্ণ মানসিকতা কাদের সুবিধা করছে?
*****
Read MoreAuthor: Sovon Lal Misra
Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্রোণাচার 16-August-2021 by east is risingসমসাময়িক কালে ‘মনুবাদ’ শব্দটি প্রায়শই বিতর্কেরকেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ছে। একদল ‘মনুবাদ’-এর ‘সব ভালো’ গোছের যুক্তিজাল বিস্তারে সদা সচেষ্ট। আর অপর দলটি স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে ‘সব খারাপে’র রোজনামচা আওড়াতে আওড়াতে গাজোয়ারি করেই চলেছেন। একবিংশশতকের যুক্তি ও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনায় অতিপক্ষপাত বা বিকট বিরোধিতার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। ‘মনুবাদ’ হল প্রকৃতপক্ষে মনুর সমাজদর্শন বা মনু প্রণীত জীবন ও সমাজনীতি। মজার বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন নীতিপ্রণেতার নাম খুঁজে পাওয়া বোধ করি সবচেয়ে কঠিনতম কাজ হবে যাঁর প্রণীত নীতি একশ শতাংশ সমাদৃত হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের পক্ষে হিতকর ‘সুনীতি’ আজও সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক। অতএব, ‘মনুবাদ’ বা মনুর নীতিরও কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক দিক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এটাও কাম্য যে, যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই ভালো-মন্দ মিলিয়ে তার পুরোটা সমালোচিত হবে। কেবলমাত্র ধর্মীয়, দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে এর ওপর শুধুই নেতি বা শুধুই ইতির বিজ্ঞাপন সেঁটে দেওয়া একেবারেই কাম্য নয়।
‘মনুবাদ’ বুঝতে গেলে মনুর সাথে পরিচিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্রকার মনু একটি সর্বপণ্ডিতগ্রাহ্য ও সমাদৃত নাম। তবে মনু ভারতীয় পরম্পরার বহু প্রাচীন ব্যক্তিত্ব। বৈদিকসাহিত্যে মনুর বারংবার স্বপ্রতিভ উপস্থিতি তাঁর প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য ও জনপ্রিয়তাকে সুনির্দিষ্ট করে।বেদে মনু হলেন ‘আদি মানব’ (ঋগ্বেদ ৩/৩৪/৪, ৩/৫৭/৪) অতএব তিনিই ‘আদি পিতা’ (ঋগ্বেদ ১/৮০/২৬, ১/৯৬/২) অর্থাৎ প্রজাবান মনুর লোকবল ছিল সুপ্রচুর। কখনও কখনও তিনি যজ্ঞকর্তা (ঋগ্বেদ ১/৩৬/১০, ৮/৩০/২, ১০/৩৬/১০, ১০/৬৫/১৪ ইত্যাদি) অর্থাৎ মনুর আর্থিক প্রাচুর্যও ছিল অতুলনীয় কারণ যজ্ঞকর্ম ছিল একটি অত্যন্ত ব্যয়বহূল অনুষ্ঠান। আবার ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণী অনুসারে মনু পাঁচটি সূক্তের ঋষি। সুতরাং মনু শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতদের একজন। এখন যার কাছে লোকবল, অর্থ এবং বুদ্ধি থাকবে সেই প্রতিপক্ষহীন একাধিপতি হওয়ার প্রয়াস করবে। অগত্যা ঋগ্বেদে (৫/৪৫/৬) মনুই শত্রুবিজেতা যোদ্ধা এবং কৃতযুগের রাজা। এইরূপ শত্রুদলন, বলশালী এবং শিক্ষিত রাজার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকাটাই বিধেয়। তাই তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মনুর বচন কে ঔষধের ন্যায় কল্যাণকর বলা হয়েছে। এইভাবে বৈদিকসাহিত্যে উল্লিখিত মনুর গুণাবলিকে বাস্তবিক ভঙ্গিমায় সাজিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি মনুর মধ্যে শাশ্বত মানবদর্শনের এক সুস্পষ্ট ও সরল চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ কোন মনু কর্তৃক প্রণীত তা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়। ‘মনুসংহিতা’-য় (১/৬১-৬৩) সাত জন মনুর উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন- স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। যদিও শাস্ত্রপরম্পরা আরও সাত জন মনুর কথা বলে। এই সাত জন হলেন- সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মনুর সময়কালকে ‘মন্বন্তর’বলে। অতএব মোট চোদ্দো জন মনুর মধ্যে কোন মনুর সময়ে এই মহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করা খুব কঠিন। এই চোদ্দো জন ছাড়াও ‘যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা’-র টীকাকার অপরার্ক ও বিজ্ঞানেশ্বর ‘বৃদ্ধমনু’ এবং ‘বৃহন্মনু’ কর্তৃক রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবার ‘মনুসংহিতা’-র ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার গোবিন্দরাজ মনুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, মনু এমন একজন পুরুষ যিনি বিভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়ন ও জ্ঞান করেছিলেন, বেদবিহিত সকল কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। যদিও একদল পণ্ডিত শাস্ত্রীয় কয়েকটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে স্বায়ম্ভুব মনুকেই প্রাচীনতম মনু ও ‘মনুসংহিতা’-র রচয়িতা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই সিদ্ধান্তের বেশিরভাগই অনুমান নির্ভর। বৈদিক মনুকেও এর রচয়িতা মেনে নেওয়া কঠিন যেহেতু এই দুই সাহিত্যের কালের ব্যবধান বিস্তর। এককথায়, মনু কোনো ব্যক্তি নাম না গোত্র নাম তা নির্ণয় যেমন কঠিন ‘মনুসংহিতা’-র গ্রন্থ কর্তৃত্ব নির্ণয়ও ততটাই কষ্টসাধ্য।
বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ নামক যে গ্রন্থটির ওপর ভিত্তি করে মনু বা তাঁর নীতি সমালোচিত হয়, সেটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ২৬৮৫ শ্লোক সমন্বিত।তবে গ্রন্থটির উৎস বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। ‘মহাভারত’ অনুসারে (শান্তিপর্ব, ৩৩৬/৩৮-৪৬) পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান লোকহিতার্থে ধর্মবিষয়ক এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেন যা মনু কর্তৃক প্রজাগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। উশনা ও বৃহস্পতি মনুর নিকটে ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান করেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ‘নারদস্মৃতি’আবার বলছেন, মানবসমাজের কল্যাণার্থে মনু ২৪টি প্রকরণে এক লক্ষ শ্লোকে এক সুবৃহৎ ধর্মশাস্ত্র রচনা করে নারদকে দান করেন। নারদ বারো হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে মার্কণ্ডেয়কে শিক্ষা দেন। মার্কণ্ডেয় আবার আট হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে ভৃগুপুত্র সুমতিকে শিক্ষা দেন। সুমতি সেই শাস্ত্রকে মাত্র চার হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করে উপস্থাপিত করেন। বর্ণিত এই কাহিনিগুলির সত্যাসত্য এখানে বিচার্য নয়। লক্ষ্যণীয় হল, পরম্পরাক্রমে বিষয়সংক্ষেপের মারাত্মক প্রবণতা। আর সংক্ষেপের মানসিকতায় কোনো শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হলে মূল বক্তব্যবিষয় থেকে বা মূলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বিচ্যূতি যে কতটা স্বাভাবিক তা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আরও একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য, ‘মনুসংহিতা’-তেই বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ধর্মবিষয়ক এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে মনুকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। অধিগতশাস্ত্র মনু মরীচি প্রমুখ মুনিগণকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে ভৃগুকে মনু মহর্ষিগণের সমীপে এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যানের নির্দেশ দেন। মনু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভৃগু যা উপস্থাপিত করেন তাই হল ‘মনুসংহিতা’। অর্থাৎ আমাদের হাতে যে ‘মনুসংহিতা’ রয়েছে তা স্বয়ং মনুর দ্বারা উচ্চারিত, কথিত বা লিখিত নয়। আর একজনের মতামত যখন অপর একজনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তখন মূল বক্তার বক্তব্য বিকৃতঅথবাসুগঠিতহতেই পারে। আবার ব্যাখ্যাতার নিজের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দ্বারাও তা প্রভাবিত হতে পারে। এককথায়, মূল বক্তার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে সমালোচকগণের বিচারভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। অতএব, ভৃগু প্রোক্ত এই ‘মনুসংহিতা’-র নিরিখে যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই উক্ত অতিবাস্তব বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে।
আলোচ্য ‘মনুসংহিতা’-য় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তও নেহাত কম নয়। যেমন- ৩/১২-১৩ শ্লোকে ‘অনুলোম বিবাহ’-কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নীচবর্ণের কন্যার বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। কিন্তু এর ঠিক পরেই ৩/১৪-১৫ শ্লোকে পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলা হল যে ইতিহাস বিপৎকালেও দ্বিজাতি কর্তৃক নীচবর্ণের স্ত্রী গ্রহণের উপদেশ দেয় না। ‘অনুলোম বিবাহ’-এর ফলে দ্বিজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বা বংশগৌরব হারিয়ে ফেলে। এখন প্রথম সিদ্ধান্তটিকে হাতিয়ার করে একদল মনুকে আধুনিক ও উদার প্রমাণে ব্যস্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে প্রাধান্য দিয়ে আরেক দল মনুর কট্টর বিরোধিতা করছেন। দুটোই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা আবারও বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নরেখে গেল। বর্তমান ‘মনুসংহিতা’ কি আদৌ পুরোটা মনুর মতামত বা সেটি কি আদৌ আদ্যোপান্ত ভৃগু প্রোক্ত? না কীসময়ে সময়ে সুযোগসন্ধানী সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থ মতো মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনের মাধ্যমে আজকের চেহারা দিয়েছে? না কী মনু তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তের দ্বারা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েও কোনো বিশেষ শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন? এই সবই গভীর ও গম্ভীর গবেষণার বিষয়। তাই সমালোচকগণের উচিত রাগদ্বেষাদিবর্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ‘মনুসংহিতা’ নামক গ্রন্থটির বা ‘মনুবাদ’ নামক নীতিটির বিচার বিমর্শ করা। তা না হলে গ্রন্থটির বা নীতিটির সঠিক তত্ত্বনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।
ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো রচনা, ঘটনা বা ব্যক্তির সময় নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ কারণ আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাসের প্রতি অনীহা এবং আত্মশ্লাঘাদোষদুষ্ট হওয়ার অযথা ভীতি। ‘মনুসংহিতা’-ও তার ব্যতিক্রম নয়। অগত্যা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত মনু ও ‘মনুসংহিতা’ বিষয়ক তথ্যগুলির পৌর্বাপর্য বিচার করে এবং এই গ্রন্থে পরিবেষিত (মনুসংহিতা, ১০/৪৪) পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ- এই জাতিগুলির ইতিহাস বিচার করে পণ্ডিতগণ ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ এই সুদীর্ঘ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক গবেষকগণ অবশ্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে গ্রন্থটিকে আরও আধুনিক রচনা বলে সিদ্ধান্ত করে ০-২০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন।
এখন নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে ‘মনুসংহিতা’-তে উপদিষ্ট নির্দেশিকাগুলির তুল্যমূল্য আলোচনা করা যাক। মনু সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়ে চলেছেন যে দুটি নীতির জন্য তাদের মধ্যে একটি হল ব্রাহ্মণতোষণ। ব্রাহ্মণ্যস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার নির্লজ্জ প্রয়াস ‘মনুসংহিতা’-তে সুপ্রচুর। মনু গুণ ও কর্মের নিরিখে যেকোনো বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বর কথা বললেও ব্রাহ্মণকে জন্ম মাত্রই শ্রেষ্ঠ বলেছেন (মনুসংহিতা, ১/৯৯)। ব্রাহ্মণ যদি অপরের অর্থ গ্রহণ করেন, অন্যের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধানও করেন তাতেও তাঁর কোনো অন্যায় হয় না যেহেতু এই জগতে যত ধনসম্পত্তি আছে তা সবই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য (মনুসংহিতা, ১/১০০-১০১)। আসলে যারা লোভী ও পরশ্রীকাতর ব্রাহ্মণ তাদের স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান সুরক্ষিত করা হল।
২/১৩৫ শ্লোকে বলা হয়েছে, একশবছর বয়স্ক একজন ক্ষত্রিয় দশবছর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণের প্রতিও পিতার মতো আচরণ করবে। অতএব বাকি বৈশ্য ও শূদ্রের কথা বলাই বাহুল্য। এতে করে ব্রাহ্মণের প্রতি বাকি তিন বর্ণের আনুগত্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হল তেমনি শাসনযন্ত্রের যারা নিয়ন্ত্রক সেই ক্ষত্রিয়দের বদান্যতাও আদায় করা গেল।
রাজতান্ত্রিক শাসন পরিকাঠামোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং তৎসম্পর্কিত বিচার পরামর্শ ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সঠিক মন্ত্রণার দ্বারা স্থিরিকৃত যুদ্ধ বা সন্ধিনীতির ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তার। এক্ষেত্রেও মনু ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। সন্ধি-বিগ্রহাদির বিষয়ে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীগণের অভিপ্রায় জানার পর সবশেষে বিশিষ্ট ধার্মিক বিদ্বান ব্রাহ্মণের সঙ্গেই তিনি গোপনে মন্ত্রণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন (মনুসংহিতা, ৭/৫৭-৫৯)। বিচার ব্যবস্থাতেও ব্রাহ্মণের প্রায় একই রকম প্রাধান্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা ঘুরপথে কিছু ব্রাহ্মণের করায়ত্ত ছিল।
ব্রাহ্মণ কোনো গুপ্তধন লাভ করলে পুরোটাই তার নিজের হত। কিন্তু রাজাও যদি গুপ্তধন পান তবে তার অর্ধেক ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি ছিল (মনুসংহিতা, ৮/৩৭-৩৮)। ব্রাহ্মণের আর্থিক স্বাধীনতার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।
শাস্তির ক্ষেত্রেও আজব বৈষম্য। মনু ব্রাহ্মণের জন্য যতটা সম্ভব লঘু দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধান নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি। আর সমাজের শিক্ষিতরাই পথপ্রদর্শক হন। উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মতাদর্শ ও জীবনদর্শন সমাজের একটি বৃহত্তর অংশে প্রভাব ফেলে। যেকোনো সময়ের জন্য একথা প্রাসঙ্গিক। অথচ মনু এই শ্রেণিটির জন্যই পাইয়ে দেওয়ার নীতি প্রণয়ন করেছেন। একজন সামাজিক নীতিনির্ধারকের কাছে এইরকম বিশেষ একটি শ্রেণির তোষণ ও পোষণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। অতএব ‘মনুবাদ’-এর সমালোচনা কাঙ্ক্ষিত। এই প্রসঙ্গে অধিককথন নিষ্প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে ‘মনুবাদ’ আর ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর উৎকট বিরোধিতার দৌলতে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অল্পবিস্তর অবহিত আছেন।
এবার আসি মুদ্রার অন্য পিঠের গল্পে। আচ্ছা কোনো একজন তথাকথিত ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’ বিরোধী বলতে পারেন, ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যেও ব্রাহ্মণরাই কেন দরিদ্র আর লোভী হয়? গল্পে গোরুও গাছে উঠতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাব কখনও ঘোঁচে না। চাল কলার প্রত্যাশা তার থেকেই যায়। এর কারণ হল ব্রাহ্মণের বৃত্তির অভাব। মনু ব্রাহ্মণের কাজ নির্দেশ করেছেন- অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (মনুসংহিতা, ১/৮৮)। ‘মনুসংহিতা’-রও কমপক্ষে ২০০ বছর আগে কৌটিল্যও ব্রাহ্মণদের প্রায় একই কাজ নির্দেশ করেছেন(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১/৩/১)। অর্থাৎ সভ্যতার সূচনালগ্নের কিছুটা পর থেকেই ব্রাহ্মণদের আয়ের উৎস হল অধ্যাপনা ও যাজন। তবে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করবার মতো বিদ্বান হতেন না। ফলে রাজার পুত্রদের পড়ানোর মতো লোভনীয় পদ ব্রাহ্মণ মাত্রই পেতেন না। আবার রাজপরিবার বা শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক প্রণীত নিয়মের বেড়াজালে পড়ে শূদ্ররা অর্থাৎ সমাজের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এরফলে ছাত্র সংখ্যাও ছিল সীমিত। অতএব অধ্যাপনা সকল ব্রাহ্মণের বৃত্তি হতে পারেনি। আরও মজার ব্যাপার হল, যে অধ্যাপক বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করতেন তিনি নিন্দিত ও নিকৃষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫৬)। হাতে রইল যাজন। প্রাসঙ্গিক কারণেই যজ্ঞপদ্ধতি ও আড়ম্বর বাড়তে থাকে এবং ছলে-বলে-কৌশলে সকল স্তরের মানুষের ওপর যজ্ঞ করবার বিধান চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু এতেও সমাজের সকল ব্রাহ্মণের জীবিকা সুনিশ্চিত হয়নি। কারণ পৌরোহিত্য করবার মতো শাস্ত্রজ্ঞান বা গ্রহণযোগ্যতা সকল ব্রাহ্মণের ছিলনা। অগত্যা বিকল্প বৃত্তির সন্ধান। পড়ে রয়েছে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অন্যে দান করলে তার গ্রহণ। কিন্তু দান মানুষের ইচ্ছাধীন। আবার শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবিকার অন্য পথও আর নেই। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণকে দান যে কতটা পুণ্যের তার প্রচার শুরু হল। সুনির্দিষ্ট জীবিকার অভাবে আপামর ব্রাহ্মণের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করবার এই সকল অন্যায় আবদারে নাজেহাল সমাজের কাছে ব্রাহ্মণমাত্রেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে।
অথচ বাকি তিন বর্ণের সুনির্দিষ্ট জীবিকা ছিল। ক্ষত্রিয়গণের হাতে ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য। বৈশ্যগণের কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ছিল ভীষণ অর্থকরী জীবিকা।‘মনুসংহিতা’ রচনার সময়ে কৃষিই ছিল আর্থ-সামাজিক ভিত্তি। আবার ঐ সময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ মনুর ব্যবস্থিত বৃত্তির সুবাদে বৈশ্যরা ছিল স্বচ্ছল। শূদ্রদের প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বিতর্কিত। তাহলেও তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাপনাতে মনু কোনো কার্পণ্য করেননি। দ্বিজাতি সেবার পাশাপাশি শূদ্রদের কারুকর্ম ও শিল্পকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মনুসংহিতা, ১০/১০০)। সমসাময়িক ইতিহাস বহুপ্রকার নতুন নতুন শিল্পকর্মের কথা বলে। যেমন- ‘বসকার’ (বাঁশের কারিগর), ‘কোনাচিক’ (কঞ্চির কারিগর), ‘মালাকার’ (মালা গাঁথা ও বাগানের পরিচর্যা করা), ‘সোবাসক’ বা ‘গধিক’ (সুগন্ধী প্রস্তুতকারক), ‘দন্তকার’ (গজদন্তশিল্পী), ‘সুবর্ণকার’ (স্বর্ণশিল্পী), ‘মণিকার’ (মূল্যবান পাথর দিয়ে অলংকার প্রস্তুতকারক), ‘রঙ্গকার’ (কাপড় রঙ করবার কারিগর) ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সময়ে শূদ্রদেরও বহু জীবিকা ছিল। শুধু তাই নয়, ভৃত্যরূপ শূদ্রের ভালোভাবে দিনযাপনের জন্য তার কর্মনৈপুণ্য ও পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে বেতন ব্যবস্থার কথাও মনু বলেছেন (মনুসংহিতা, ১০/১২৪)।
কিন্তু অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় মনু স্পষ্ট করেননি। বৃত্তির অভাবে সিংহভাগ ব্রাহ্মণ বর্ণব্যবস্থার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁদের ক্ষুন্নিবারণের প্রচেষ্টাও সমালোচিত হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার বিপরীতে গিয়ে যাঁরা অন্যান্য কাজকে জীবিকা করেছেন মনু তাঁদের সরাসরি নিন্দা করে তাঁদেরকে নিকৃষ্ট শ্রেণির বলেছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫০-১৬৬)। যেমন- ‘স্তেন’ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ চোর। তাহলে জীবিকার তাড়নায় ব্রাহ্মণেরা চৌর্যবৃত্তিও গ্রহণ করেছিল। ‘নাস্তিকবৃত্তি’- পরলোক ইত্যাদি আস্তিক সিদ্ধান্ত মানতেন না এমন ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ ধর্মান্ধ বা গোঁড়া ছিলেননা। ‘অনধীয়ান’- যিনি বেদাধ্যয়ন করেননি বা অধ্যয়ন করলেও তা আয়ত্ত করতে পারেননি। তাহলে সব ব্রাহ্মণ বেদ পড়তেন এ ধারণা ভুল। কারণ বেদ পড়লেই অধ্যাপনার মতো যোগ্যতা অর্জন সবার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। যে ব্রাহ্মণ বহুলোকের হয়ে যাজন করে সেও নিন্দিত। যে যাজন বেশকিছু ব্রাহ্মণের অন্নের ব্যবস্থা করছিল তাতেও বাধা পড়ল। অর্থাৎ অনেকের পৌরোহিত্য করে বেশি উপার্জনের পথও সম্ভবত বন্ধ ছিল। ‘চিকিৎসক’- যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা ওষুধবিক্রয়কারী। চিকিৎসা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হলেও, সমাজের তাতে উপকার হলেও যেহেতু একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপার্জনের চেষ্টা করছে কেবল সেই কারণেই তারা শাস্ত্রকার কর্তৃক সমালোচিত। ‘মাংসবিক্রয়ী’- যে ব্রাহ্মণেরা মাংস বিক্রয় করেন। সহজেই অনুমেয় সেই ব্রাহ্মণেরা সমাজে কিরকম বিদ্রুপের সম্মুখীন হতেন। ‘বিপণন’- যে ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ পণ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্থাৎ জীবিকার অভাব অনেক ব্রাহ্মণকেই গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করত।‘পশুপাল’- যে ব্রাহ্মণ জীবিকার কারণে বিভিন্ন পশুপালন করতেন। ‘গণাভ্যন্তর’- যে ব্রাহ্মণ মঠাদিতে প্রদত্ত জনসাধারণের অর্থে জীবনধারণ করে। তাহলে কি মন্দিরে দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থের অধিকারও সাধারণ ব্রাহ্মণগণের ছিলনা? যদি তা সত্যি হয় তাহলে ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর নামে গুটিকয়েক ক্ষমতাভোগকারী ব্রাহ্মণের জন্য জীবনসংগ্রামে লড়াই করে যাওয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ভাবমূর্তির অপব্যাখ্যা হচ্ছে।‘কুশীলব’- অভিনয়ের মাধ্যমে উপার্জন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই জীবিকা সমাজে সমালোচিত হত। অতএব সেই সময়ের ব্রাহ্মণগণ কী পরিমাণ নিরুপায় ছিলেন তা বুঝতে অধিক বেগ পেতে হয় না। ‘বৃষলীপতি’- যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীকে বিবাহ করেছেন। ব্রাহ্মণবিরোধীরা যতই অস্পৃশ্যতার গল্প শোনান না কেন, উল্টো ছবিও যে ছিল তা অস্বীকার করতে পারবেন না। সাধারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রা বিবাহের উদারতা ও সাহস ছিল। ‘শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব’- যিনি শূদ্রের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং শূদ্রকে অধ্যয়ন করান। বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক। তাহলে শূদ্র মাত্রই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অনেকে অধ্যাপনার মতো ব্যুৎপত্তিও লাভ করতেন। আর সব শিক্ষিত ব্রাহ্মণই শূদ্রবিরোধী ছিলেন না। নতুবা শূদ্রকে অধ্যয়ন করাতেন না। তাহলে কি শূদ্র জাগরণের বীজ ব্রাহ্মণগণের হাতেই বপিত হয়েছে? ‘সোমবিক্রয়ী’- ঔষধের জন্য বা যাগের জন্য যে ব্রাহ্মণ সোমলতা বিক্রয় করেন। তাহলে শুধু শূদ্র কেন, ক্ষমতা বা অর্থহীন ব্রাহ্মণেরও সোমপানের অধিকার ছিলনা। ‘তৈলিক”- তেলি। আসলে নির্দিষ্ট সুনিশ্চিত উপার্জনের উপায়ের অভাবে ব্রাহ্মণরা যুগে যুগে জর্জরিত। বিচিত্র জীবিকাতেও যথেষ্ট আয়ের অভাবেই ব্রাহ্মণ দরিদ্র। আর চাওয়া পাওয়ার সাংসারিক জালে আবদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বাভাবিক নিয়মেই লোভী। সেই লোভ পূরণের বাসনায় ব্রাহ্মণ কখনও ধূর্ত আবার কখনও কপট।
‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর বিরোধীগণ বলবেন এগুলি কয়েকটি ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে যা প্রমাণের চেষ্টা চলছে তা নিরেট মিথ্যা। এঁনাদের এঁদের পরিচিত ভাষাতেই উত্তর দিতে চাইছি। বর্তমানে গণতন্ত্রের সুবাদে এবং সুসংবদ্ধ সংবিধানের আশীর্বাদে সকল জাতির স্বার্থ বেশ সুরক্ষিত। তবুও মাঝেমধ্যেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া কোনো জাতির মানুষের ওপর যে কারণেই হিংসা করুক না কেন তা জাতিবিদ্বেষ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কখনোই সেটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিচার করা হয় না। দুর্বৃত্ত যে জাতিরই হোক না কেন অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্রাহ্মণ সমালোচিত হন। কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণ যখন অন্য জাতিতে বিবাহ করছেন, অন্য জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছেন, তাদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করছেন, অধ্যাপনা বা পৌরহিত্য ছাড়া অন্য কাজ করছেন তখন কেন তাঁরা প্রশংসিত হচ্ছেন না? অথচ আজকের সমাজে এটাই নিত্যদিন ঘটে চলেছে। আজকের ব্যতিক্রমী ঘটনার ওপর ভিত্তি করে যদি ব্রাহ্মণ সমালোচিত হতে পারেন তবেমনুরসময়েরঐ ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য তাঁদের প্রশংসাতে দোষ হবে কেন? বাস্তব চিত্র আরও কঠিন। যদি কোনো ব্রাহ্মণ অন্য জাতিতে বিবাহ করেন তবে কোন যাদুমন্ত্রে জানিনা অন্য জাতির লোকেরাই তাঁদের কোনো রকম পৌরোহিত্যকর্মে ঐ ব্রাহ্মণকে আর আমন্ত্রণ করেন না। তখনও কিন্তু কোনো বিরোধীই উচ্চবাচ্য করেন না। তাহলে কি কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্যই ব্রাহ্মণ বিরোধিতা চলছে? ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।
এতো গেল সামাজিক পরিস্থিতি ও মানসিকতার কথা। সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যবংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথকে ক্ষমতাচ্যূত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ হিসেবেই বর্ণিত। সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আয় সহায়ক বৃত্তির অভাবই ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রকে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিল কীনা সে প্রশ্ন আবারও রইল। যাই হোক না কেন, পূর্বে আলোচিত সিদ্ধান্ত অনুসারে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসনে আরোহণের সময়েই আসলে ‘মনুসংহিতা’ রচনা শুরু হয়েছিল। আবার পৌরাণিক সাক্ষ্য মেনে নিলে দশজন শুঙ্গ শাসক মোট একশ বারো বছর ক্ষমতায় ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শুঙ্গদের শাসন স্থায়ী ছিল। সুদীর্ঘ এই ব্রাহ্মণ বংশীয় শাসনের আবহের চিত কোনো সামাজিক নীতিনির্ধারক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের সামাজিক স্বার্থ বিশেষভাবে সুরক্ষিত হবে-
এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রাচীন ভারতের প্রায় কোনো রচনাই রাজশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি।
লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে, ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে কোনো বড় রাজশক্তি দীর্ঘকাল শাসন করতে পারেনি। এই সময়ে যে বিভিন্ন শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করছিল তাদের মধ্যে গ্রিক, শক, ইউয়ে-ঝি ইত্যাদির মতো মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত গোষ্ঠীগুলিও ছিল। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু বৈদেশিক শক্তি কেন, অন্যান্য শাসক শক্তিগুলির বেশির ভাগই তথাকথিত বৈদিক পরম্পরার প্রতি আকর্ষিত হননি বা সেসম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। হয়তো তাঁরা বৈদিক বিশ্বাসের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু রাজশক্তির আগ্রহের বিষয়না হওয়ায় তার প্রচারও প্রসার মন্দীভূত হতে থাকে। বৌদ্ধ বা জৈনরা যে ধরণের রাজানুকূল্য পেতে থাকেন, বেদপন্থীরা তা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। এরও আগে অর্থাৎ মৌর্যযুগেও বৈদিকেতর ধর্মই রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ফলে আলোচ্য যুগে হয়তো বৈদিক পরম্পরার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো দীর্ঘ মৌর্যযুগেও যার অস্তিত্ব বিরল সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো রাজনৈতিক গুরুত্বযুক্ত অথচ বৈদিক যজ্ঞের উল্লেখ শুঙ্গদের আমল থেকেই দেখতে পাই। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ যিনি অযোধ্যা অঞ্চলের শাসক সেই ধনদেব জানিয়েছেন যে পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী। বৈদিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে সমাজে আবার একবার প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা খুব সম্ভবত শুরু হয়েছিল। বোধকরি এইরকম আবহে এবং উদ্দেশ্যে ‘মনুসংহিতা’-র মতো স্মৃতি গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। ফলতসেখানেবর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ স্থান ভীষণ স্বাভাবিক।বৈদিকব্যবস্থাপনাকে অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যপালনীয় করবার প্রয়াস স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত নীতিগুলি ক্রমশ জটিল, সম্প্রদায়স্বার্থনির্ভর, পক্ষপাতদুষ্ট ও অমানবিক হয়েছে।
অপর যে কারণের জন্য মনু বারেবারে সমালোচিত হচ্ছেন সেটি হল নারী জাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে মনুর নারীদের জন্য গৃহীত নীতিগুলিতে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। নারীবাদীরা অবশ্য আলোচ্য বিষয়ে প্রায় প্রতিনিয়তই বিচার, বিমর্শ, তর্জমা করেই চলেছেন। তবুও কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত হবে।
মনুতাঁর ‘মনুসংহিতা’ গ্রন্থে সমাজের প্রত্যেকের অধিকার সুনিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব পালনে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ ও নারী- এই দুটিই সমাজের একমাত্র এবং অকৃত্রিম একক। অথচ নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সৃষ্ট সমাজের নীতি নির্ধারণে মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের কথা বললেন। ‘অস্বতন্ত্রাঃস্ত্রিয়ঃকার্যাঃ…’ (মনুসংহিতা, ৯/২) অর্থাৎ দিনে বা রাতে, ধর্মাচরণে বা আন্যান্য বিষয়ে নারীকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান পুরুষের অনুচিত। ‘…নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ (মনুসংহিতা, ৯/৩)–স্ত্রীরা স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করবে। ‘…নভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্’ (মনুসংহিতা, ৫/১৪৮) এখানেও নারীর স্বাধীনতা হরণেরই নির্দেশ। অথচ বিগত কয়েক শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যাবে, যে দেশের নারীশক্তির স্বার্থক অগ্রগতি যত বেশি সে দেশের বিকাশের হারও ততটাই উঁচুর দিকে। একজন নীতিপ্রণেতা কী করে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ বপন করতে পারেন! সমাজে শুধু পুরুষের উন্নতি হলে বা কেবলমাত্র পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকলে আদৌ সমাজ বা সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে তো! তাই মনুর এই ধরনের বক্তব্যগুলি বিস্ময়কর।
মনুর মতে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই নারীদের মূল কর্ম। বিবাহ ও গর্ভধারণের মধ্যেই নারীত্বের স্বার্থকতা। যেহেতু গর্ভধারণের জন্যই নারীর সৃষ্টি (মনুসংহিতা, ৯/৯৬)। কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য ‘নিয়োগপ্রথা’-র মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থাতেও মনুর সম্মতি লক্ষ্যণীয়। কোনো ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্রীয় কোনো পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে (মনুসংহিতা, ৯/১৯০)। উল্লেখ্য, শুধু সন্তান নয় বরং পুত্র সন্তান উৎপাদনেই বার বার জোর দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া মনু বাল্যবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছেন (মনুসংহিতা, ৯/৯৪)। নারী মাত্রই স্খলিত ও দূষিত চরিত্র তা প্রমাণে বহুবার প্রয়াস করেছেন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ মাত্রই আসক্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে পুরুষের বয়স বা রূপ কোনোটাই বিবেচ্য হয় না। নারীগণ ‘পুংশ্চলী’ অর্থাৎ দৃষ্টিপথে আগত যেকোনো পুরষের সাথে সম্ভোগের চিন্তায় এদের চিত্ত এতটাই চঞ্চল হয় যে স্বামীর প্রতিও বিরূপ হয়ে ওঠে (মনুসংহিতা, ৯/১৪-১৫)। এমনকি মা, বোন বা কন্যার সাথেও নির্জন গৃহে পুরুষকে বাস না করবার বিধান দেন (মনুসংহিতা, ২/২১৫)। নারীরা স্বভাবতই পুরুষের মনকে কামের দ্বারা কলুষিত করে (মনুসংহিতা, ২/২১৩)। নারীজাতির এহেন নীচ ভাবমূর্তি চিত্রণ একেবারেই কাম্য নয়। নারীর আবেদনে যে পুরুষেরা আকৃষ্ট হচ্ছে তারাও সমান দোষী। এক হাতে তালি আজ পর্যন্ত বাজেনি। অতএব মনুর কঠোরতম সমালোচনা ভবিতব্য।
কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে মনু নারীবিদ্বেষী। মনুপ্রণীত সকল নীতি নারীর স্বার্থবিরোধী ছিল না। এর বহু প্রমাণ রয়েছে যেগুলি সচেতন বা অচেতন ভাবেই অনালোচিত। যেমন- ৯/১৩০ শ্লোকে মনু পুত্র ও কন্যাকে সমান বলেছেন। পুত্র আর নিজের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর কন্যা পুত্রের সমান। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বীজ এখানেই লুকিয়ে রয়েছে।
মনু ব্যভিচার দোষদুষ্ট নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই শাস্তির বিধান দিয়েছেন। কোনো নারী পরপুরুষের সাথে মিলিত হলে তাকে বহুলোকের সামনে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলেছেন। আর যে পুরুষটির সাথে মিলিত হয়েছিল তাকে তপ্ত লোহার শয্যায় শুইয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কাঠ নিক্ষেপ করতে হবে যতক্ষণ না সে ভস্মিভূত হচ্ছে (মনুসংহিতা, ৮/৩৭১-৩৭২)। অতএব পুরুষরা কিন্তু শাস্তির বাইরে ছিল না।
এছাড়া মনু বহু উক্তিতে নারীর প্রতি সুউচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে যে বংশে নারী সমাদৃত হন সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন হন। যেখানে নারীর সমাদর নেই সেখানে সকল ধার্মিক ক্রিয়া নিস্ফল। গৃহের সকল নারীর সুখে শ্রীবৃদ্ধি, অন্যথা শ্রীহানি (মনুসংহিতা, ৩/৫৬-৫৭)। গৃহে শ্রী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই (মনুসংহিতা, ৯/২৬)। মা, দিদি বা বোন- প্রত্যেকের প্রতি মাতৃবৎ আচরণই বিধেয় (মনুসংহিতা, ২/১৩৩)। এসবই নারীজাতির প্রতি তাঁর অগাধ সম্মানের নিদর্শন।
মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের যে সকল বিধান দিয়েছেন তা সম্ভবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাবে ভাবিত হয়ে। কারণ ‘মনুসংহিতা’ যে সময়ের রচনা তখন সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। আর পরিবারগুলি ছিল যৌথ ও পিতৃতান্ত্রিক। যদিও দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘদিন সন্তানের নামকরণের সাথে মাতৃপরিচয় যুক্ত করার রীতি ছিল। সাতবাহন শাসকগণ এর সর্বজনবিদিত উদাহরণ। যাইহোক না কেন, পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজ কখনোই নারীস্বাধীনতা বা নারী অগ্রগতি চায়নি। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারানোর ভয় পুরুষজাতির মনে জাঁকিয়ে বসেছিল। মনুর নারী স্বাতন্ত্র্য খর্বের প্রয়াস পুরুষের সেই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।
মনুর বদনাম যে তিনি নারীদের কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। যদি সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে মনুর এই বদনামও বেশ কিছুটা লাঘব হতে পারে। ‘মনুসংহিতার’ রচনাকাল হিসেবে যে ৪০০ বছর কে নির্দেশ করা হয়েছে সে সময়ের আর্থ সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষি। এই সময়ে কৃষির উন্নতি ও প্রসার ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে কৃষি দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রধান বৃত্তি ছিল তা ক্রমশ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয়। নতুন নতুন কৃষি উপকরণ ব্যবহারের নিদর্শন সুস্পষ্ট। তক্ষশিলা থেকে লাঙল, কোদাল, দা, মাটি কোপানোর যন্ত্র, কুঠার, কুড়াল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি অধিকাংশই লৌহ নির্মিত। সাঁচী থেকে লাঙলের ফলা পাওয়া গেছে। ফলে কৃষিকর্ম অনেক উন্নত ও সহজ হচ্ছিল। পতিত জমিকে কর্ষণ করে নতুন চাষযোগ্য জমি তৈরির প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছিল। শুধু তাই নয় জমি ও জলবায়ুর বৈচিত্র অনুসারে ফসলেও বৈচিত্র দেখা যায়। যেমন- ‘শালি’, ‘কুমুদভণ্ডিকা’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ধান, আখ, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে উৎপন্ন তুলো, গোলমরিচ ইত্যাদি। কৃষির উন্নতির ফলে কৃষিজাত পণ্যের ওপর ভিত্তি করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও বাড়তে থাকে। তুলো থেকে তৈরি কাপড় (বিশেষ করে ‘মসলিন’), গোলমরিচ প্রভৃতির চাহিদা বিদেশের বাজারে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আরও বেশি জমি চাষের জন্য, পতিত জমিকে চাষযোগ্য করার জন্য, ভিন্ন রকম ফসল চাষের জন্য বা কৃষিজাত পণ্যগুলিকে সঠিক সময়ে বাজারে পৌঁছোনোর জন্য প্রচুর লোকবলের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরিবারগুলি সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীরাই সন্তানধারণ করতে পারেন, পুরুষরা নয়। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধিরূপ সভ্যতা ও যুগের চাহিদার বিপুল প্রত্যাশার চাপ নারীজাতির ওপর এসে পড়ে। আর পুত্রসন্তানের চাহিদা কেন? কারণ কৃষির বা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলি এতটাই শ্রমসাধ্য যে তা একজন পুরুষের পক্ষে যতটা সহজ একজন নারীর পক্ষে ততটা নয়। ফলত সন্তানধারণ, পতিসেবা ও গৃহকর্ম নারীর জন্য কর্তব্য। কারণ যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করা মনুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
সুতরাং সব শেষে আবারও উল্লেখ্য যে, দোষ-গুণ মিলিয়ে মনু বা ‘মনুবাদ’। মনু প্রণীত নীতির প্রতি ইতি বা নেতিবাচক একগুঁয়েমি অনভিপ্রেত। সমসাময়িক ইতিহাস, যুগের চাহিদা এবং সর্বোপরি মনু চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে ‘মনুবাদ’-কে বাদের খাতায় ফেলে দেওয়া মানে মূর্খের স্বর্গে বাস করা। মনুর নীতির মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র নীতিগত সফলতা না থাকত তাহলে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় তার কোনো প্রভাব থাকত না। বছর বছর ধরে বিভিন্ন রাজশক্তি ‘মনুসংহিতা’ প্রদর্শিত পথে শাসন পরিচালনা করে সফল হতেন না। আমরা আধুনিক। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীনের সার গ্রহণ ও অসার বর্জন করে বর্তমানকে আরও নির্ভুল ও নির্ভেজাল করতে হবে। এতেই আধুনিকতার মঙ্গল।
*****
Read More
Author: Sovon Lal Misra
Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 14-July-2021 by east is rising