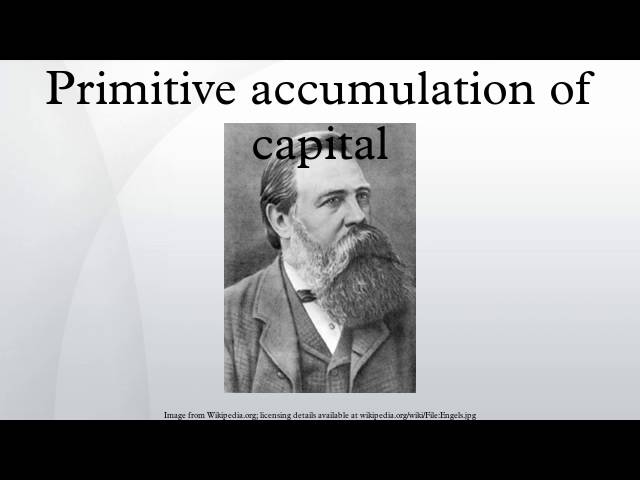


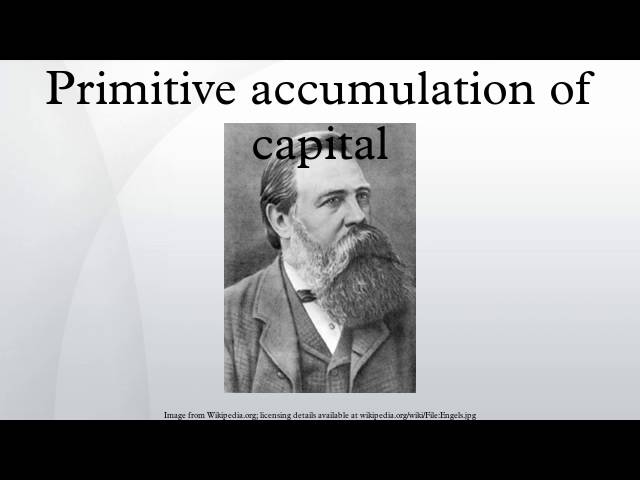
দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম পশ্চীম ইউরোপে কিভাবে একভাষি এক ধর্মের রাষ্ট্র গড়ে উঠল। তৃতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করব কিভাবে এবং কেন লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাতে কি ধরণের রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।
ফরাসী বিপ্লবের পরেই নেপোলিয়নের আঘাতে স্পেন ও পর্তুগাল-এর লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল হয়ে যায় আর সেই সুযোগে একের পর এক লাতিন আমেরিকার দেশ স্বাধীন হোতে শুরু করে। পরতুগীস ভাষি ও ক্যাথোলিক ধর্মের অংশটা একটা দেশ বানায় যাত নাম ব্রাজিল। স্প্যানিশ ভাষি ও ক্যাথোলিক ধর্মের অংশটা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লাতিন আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলো পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ, আধা শ্বেতাঙ্গ, বাদামী বর্ণের মানুষ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন দেশ হোলেও বর্ণগত বিভাজন বজায় থাকে, ভূমী সংস্কার হয়না, মূলত লাতিন আমেরিকার বিশাল খনিজ সম্পদের জোড়ে রাষ্ট্রগুলো বিদেশী মুদ্রা লাভ করতে থাকে কিন্তু বর্ণ বৈষম্য ও ভূমী সংস্কার না হওয়ায় বিদেশী মুদ্রা বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে উপনিবেশ হয়ে থাকা এশিয়া ও আফ্রিকার থেকে এগিয়ে গেলেও পশ্চীম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো। মূলত খনিজ সম্পদ ও আবহাওয়ার জন্য তৈরি হওয়া কৃষি সম্পদ জাত বিদেশী মুদ্রা লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোকে টিকিয়ে রাখে।
পূর্ব ইউরোপ জুড়ে তখন ছিল জার রাশিয়া ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য। বহুভাষি ও বহু ধর্মের এই সাম্রাজ্য দুটোও টিকে ছিল কারণ তাদের প্রকাণ্ড বড় আকারের জন্য তাদের হাতে ছিল অনেক জমি, জমির নীচের খনিজ সম্পদ। সেরকম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর না থাকায় এদের বাণিজ্যের বিকাশ হয়েছে ধীরে। পাশেই পশ্চীম ইউরোপের শিল্পায়ণ কর্মসূচীকে ত্বরাণ্বিত করত এদের খনিজ সম্পদ। এরা এই আয়কে ব্যবহার করত বিশাল সামরিক বাহিনী রাখতে আর নানা জাতির মানুষের বিদ্রোহকে দমণ করতে বা কিনে নিতে। ফলে এদের শিল্পায়ণ কর্মসূচী দুর্বল হয় এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চীম ইউরোপের তুলনায় জার রাশিয়া ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য এতোটাই পিছিয়ে পড়ে যে তাদের সামরিক বাহিনী প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পুরোপুরি পরাজিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই দুই সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য অনেক ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে কম জাতিগত বিভিন্নতার দেশ তৈরি হয় বা অনেক ক্ষেত্রে এক ভাষি এক ধর্মের দেশ তৈরি হয়। জার রাশিয়ার পতনের পরে সোভিয়েত সংবিধান সমস্ত জাতিকেই দেয় স্বাধীন হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। তাজিকদের মতো বহু জাতি তার ভাষার প্রজাতন্ত্র তৈরি করে সোভিয়েত সংবিধান মেনে। সোভিয়েত সরকার ভূমী সংস্কার করে সফলভাবে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিস্টরা পূর্ব ইউরোপ জুড়ে এই কর্মসূচী চালায় এবং দ্রুত শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে। শিল্পোন্নত হওয়ার পরেও ১৯৮০-এর দশকে এই সমস্ত দেশগুলো থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বিতারিত হওয়ার সাথে সাথেই কম বিভিন্নতার দেশগুলো এক জাতি এক ধর্মের দেশে পরিণত হয়। চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সাংবিধানিকভাবে প্রজাতন্ত্রগুলো আলাদা হয়ে যায়। যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক ভাষি এক ধর্মের দেশ তৈরি হয়।
অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হয়। তাদের অধিকাংশেরই ধর্ম সুন্নি এবং সাহিত্যের ভাষা আরবি। এই সব অঞ্চলে মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা আলাদাই রয়ে যায়। এদের মধ্যে একদিকে সাহিত্যের ভাষাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ আরব জাতি গঠনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে আর অন্যদিকে মুখের ভাষা ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছোট ছোট আরব জাতি তৈরির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। খনিজ তেল ও অজস্র আদর্শ আন্তর্জাতিক বন্দর থাকায় অধিকাংশ দেশেই দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ছোট ছোট আরব জাতি তত্ত্ব বৃহৎ আরব জাতি তত্ত্বকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।
মালেয়াশিয়া-সিঙ্গাপুর প্রথমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সিঙ্গাপুর তার আদর্শ বন্দর জাত বিদেশী মুদ্রার ভাগ বাকিদের দিতে অস্বীকার করে। সাংবিধানিকভাবেই এই তিন দেশ আলাদা হয়ে যায়। দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ ভারত আগে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তানে বিভক্ত হয় এবং পরে পাকিস্তান থেকেও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে একভাষি এক ধর্মের রাষ্ট্র স্থাপন করে। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে এখনো এরকম অনেক জাতি আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন চালচ্ছে।
সুতরাং ইতিহাস বলছে আদি পুঁজি সঞ্চয়ের স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রেই একটা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে একাধিক ভাষা ও ধর্মের মানুষ এক রাষ্ট্রের অধীনে শুরু করে বটে কিন্তু ক্রমেই আদি পুঁজির ভাগ অন্যদিকে দিতে না চেয়ে আবার দ্বিতীয়বার নিজস্ব আরও ছোট ও কম বিভিন্নতার রাষ্ট্র গড়ে তোলে। অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ একবারে নয়, বহুবারে হতে পারে পুঁজি সঞ্চয়ের ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে।
চীনের ক্ষেত্রে হান চীনারা মূলত পূর্ব উপকূলের বসবাসকারী এবং তাদের হাতে রয়েছে চীনের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো। হানদের সংখ্যাও চীনের জনসংখ্যার ৯০%। বাকি ১০% বহুভাগে বিভক্ত ছোট ছোট জাতি মূলত পশ্চীমের রুক্ষ অঞ্চলে বাস করে। এই অহানরা চীনে থাকতে চায় হানদের অর্থনৈতিক লাভের ভাগ পেতে। আর হানরা এই ভাগ দিতে রাজি থাকে তাদের পশ্চীমের সীমান্তকে বিপদমুক্ত রাখতে। কখনো যদি পশ্চীমের রুক্ষ অঞ্চলে বিশাল খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তাহলে অহানদের ওই বিশেষ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতা চাইতেই পারে। জিঞ্জিয়াং প্রদেশে কিছু তেল আবিস্কারের পরেই উইঘুরদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাময়ীকভাবে হলেও স্বাধোনতার তত্ত্ব ঢোকাতে সম্ভব হয়। তেমনই পূর্ব চীনই ওই তেলের ক্রেতা বলে মার্কিন সাহায্য পেয়েও বেশি দূর এগোতে ব্যর্থ হয় স্বাধীন জিঞ্জিয়াং-এর তত্ত্ব।
ভারতের ক্ষেত্রে উপকূলবর্তী অহিন্দিভাষিরা ক্রমেই মনে করছে তাদের লাভের বড্ড বেশি ভাগ দিতে হচ্ছে অন্তর্বর্তী হিন্দিভাষিদের। হিন্দিভাষিরা তাদের ৪৬% ভোট ব্যঙ্ক কাজে লাগিয়ে উপকূল রাজ্যগুলোর অহিন্দিভাষিদের শোষণ করছে। মনে রাখা দরকার সবচেয়ে বেশি বন্দর সমৃদ্ধ গুজারাতিদের অহিন্দিভাষিরা লটের ভাগ দিচ্ছে। এভাবেই ভারত হয়ে উঠেছে গুজারাতি-হিন্দিদের সাম্রাজ্য। একদিকে হিন্দিভাষিরা এক ভাষা এক ধর্মের শ্লোগান দিয়ে ভারতকে হিন্দু হিন্দি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। অন্যদিকে বহুত্ববাদের কথা বলে সংখ্যালঘু ধর্ম ও ভাষাগুলো টিকে থাকতে চাইছে। কংগ্রেসের নরম হিন্দু হিন্দির জায়গায় ক্রমেই বিজেপির শক্ত হিন্দুত্ব গেঁড়ে বসছে আর ততই অহিন্দিভাষি অহিন্দু ধর্মের মানুষেরা আতঙ্কিত হচ্ছে। দক্ষিণের উপকূলবর্তী জাতিগুলো স্বাধীন দ্রাবিড় রাষ্ট্রের কথা তুলছে হিন্দিভাষিদের ভোটব্যঙ্কের গুরুত্ব বাড়ায়। গুয়াজারাতি-হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের একটা অন্যতম স্তম্ভ হোল ভোটব্যঙ্ক সর্বস্ব গণতন্ত্র। ভোটব্যঙ্কের জোড়েই এই লুট টিকে আছে। তাই ভারত হিন্দি বনাম অহিন্দি দ্বন্দ্বে ভেঙ্গে পড়লে তা হবে ভোটব্যঙ্ক সরবস্ব রাজনীতির কাছে বড় একটা আঘাত। তা অবশ্যই গোটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে কাঁপিয়ে দেবে।
উনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর সময় এটা নয়। এখন সমস্ত দেশেই কৃষক প্রতি উৎপাদন অনেক বেড়েছে, নারী অনেক স্বাধীন হয়েছে, জন্মহার অনেক কমেছে, শিল্পোন্নত অঞ্চল বিশ্বে অনেক বেড়েছে আর এর ফলে খনিজ সম্পদ বিক্রেতা ও কৃষি সম্পদ বিক্রেতাদের দরকষাকষির ক্ষমতা ও আয়ও অনেক বেড়েছে। ফলে ভূমি সংস্কারের দাবী ও জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এখন ভোট ব্যঙ্ককে কেন্দ্র করে উৎপাদককে শোষণ করার এক নতুন ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্ম হয়েছে যারা তাদের শোষণকে সামাজিক ন্যায়ের নামে বৈধতা দিচ্ছে। তা ভারতের হিন্দি ভোটব্যঙ্ক হোক আর সামাজিক ন্যায়ের নামে নারী ভোটব্যঙ্ক। মেধা, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে এই ভোটব্যঙ্কের জোড়ে চলা সামাজিক ন্যায়ের নামে শোষণ।অন্যদিকে কমছে মেধা, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ, আগ্রহ ও উদ্যোগ। চীনের উত্থান হল এই ভোটব্যঙ্ক কেন্দ্রিক শোষণের বিরুদ্ধে যোগ্যতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উত্থান। পুরুষবাদী আন্দোলনও এই নারী ভোটব্যঙ্ক কেন্দ্রিক আইন ব্যবস্থা ও সমাজ চিন্তার বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব।
যোগ্যতা ভিত্তিক সমাজ বানাও, যোগ্যদের সম্মান দাও, কম যোগ্যদের যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ কর কিন্তু কম যোগ্যতাকে ঢাকতে ভোটব্যঙ্ক বানিয়ে যোগ্যদের শোষণ বন্ধ হোক। এটাই একবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব।
Author: Saikat Bhattacharya