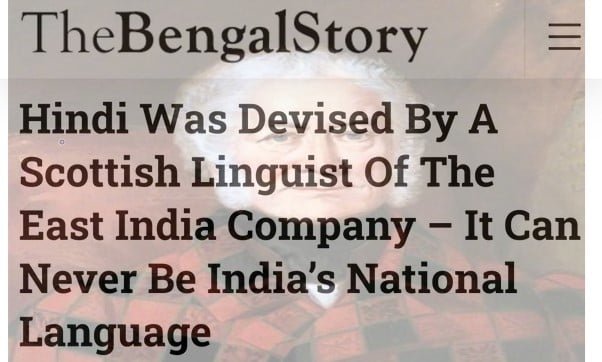


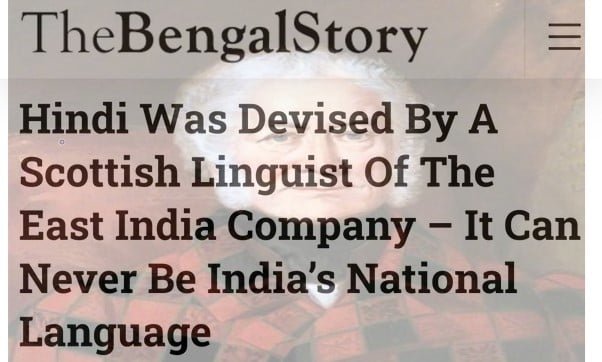
আধুনিক হিন্দী ভাষার বয়স ১৫০ বছরের কাছাকাছি। এই ভাষাকে স্থানীয় অনেক ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভারতে নেশন স্টেট বানানোর জন্য যে তিনটি মুল স্তম্ভকে বেছে নেয়া হয়।
তার একটি হিন্দু ধর্ম, একটি হিন্দি ভাষা , আরেকটি হিন্দুস্তান বলে একটি কাল্পনিক ভুখণ্ড। এই ভাষার উদ্ভব এবং বিকাশের সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু মহাসভার নাম।
দিল্লি এবং এর পাশের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে ভাষা ছিলো তাকে হিন্দি বলয়ের বাইরের মানুষেরা বলতো হিন্দবি বা হিন্ধি। আর নিজেরা এই ভাষাকে বলতো খড়ী বোলি বা চালু ভাষা।
দিল্লি ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে ব্রজভাষা, ডিঙ্গল, মেওয়ারি, আবধী, মাগহি, ভোজপুরি, মৈথিলি এই ভাষাগুলো ব্যবহৃত হতো। সবগুলোই খুব সমৃদ্ধ ভাষা ছিলো।
কবীরের বচন ছিলো ব্রজভাষায় রচিত, মীরার ভজন ডিঙ্গলে, আবধীর কবি ছিলেন বিখ্যাত তুলশি দাস, মৈথেলি ভাষায় বিদ্যাপতি আর গোবিন্দ। কিন্তু আপনি আজকে কোন ভাষাই আর খুঁজে পাবেন না। হিন্দি সব ভাষাকে সিস্টেমিকভাবে মুছে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে তাঁদের অমুল্য সাহিত্যের কথাও।
আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে হিন্দির আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব হয় কোলকাতাতেই আর আজকে এই কোলকাতাতেই হিন্দির দাপটে বাঙলার ত্রাহি ত্রাহি দশা। হিন্দি ভাষার প্রসার এবং তাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়া হয় হিন্দু মহাসভার মাধ্যমে।
উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজ কর্মচারিরা এখানকার চাপরাশি, সহিস, জমাদার এইধরনের ভৃত্যস্থানীয় কর্মচারিদের সাথে ও দোকানদার, ফেরিওয়ালা এদের সাথে কথা বলার জন্য যে ভাষার চর্চা করতো তা ছিল এই দিল্লির খড়ি বোলি, ইংরেজরা তাকে হিন্দি বলতো।
এই কথ্য ভাষাকে সংস্কার করে লিখিত ভাষার রূপ দেন জেমস গিলগ্রিস্ট নামের এক ইংরেজ। কলকাতা শহরেই প্রথম হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয় “উদন্ত মার্তণ্ড” নামে। তখনো পর্যন্ত হিন্দির জন্য বিশেষ কোন লিপি স্বীকৃত বা গৃহীত হয়নি।
ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন যখন তার নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারত ঘুরছিলেন তখন তিনি উপলব্ধি করেন সারা দেশের মানুষ নানা বিচিত্র ভাষায় কথা বলে, এক অঞ্চলের ভাষা আরেক অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারেন না।
তিনি আশ্রয় করেন হিন্দি ভাষার এবং “সুলভ সমাচার” পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দিতে তার মতবাদ সারা ভারতে প্রচার করতে শুরু করেন। এরপরে কোলকাতায় আসেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একটা বক্তৃতা দিতে। তিনি ছিলেন গুজরাটি কিন্তু শিক্ষিত সমাজের মাঝে বক্তৃতা দিতে হলে বক্তৃতা দিতেন সংস্কৃতে।
এসে দেখলেন এখানে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই হিন্দিকে সামাজিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এটা দেখে দয়ানন্দ সরস্বতী কোলকাতায় নিজের বক্তৃতাটা দেন হিন্দিতে। এরপরেই তিনি প্রস্তাব করেন হিন্দি নাগরি লিপিতে লেখা যেতে পারে। নাগরি লিপি হচ্ছে সেই লিপি যা দিয়ে গুজরাটি ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত চর্চা করতেন।
হিন্দির এই সর্বব্যাপী আগ্রাসনের ফলেই ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানের কাছে উর্দু হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের আত্মপরিচয়, আর পাকিস্তান রাষ্ট্রকল্প তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়ালো হিন্দির দাপট থেকে মননের মুক্তাঞ্চল।
Author: Pinaki Bhattacharya